- 16
- 0
প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

ফসল - কেন্দ্রিক লোকায়ত পৌষ পার্বনের ভাবনা
যে কোনও উৎসব মানুষ তখনই পালন করেন, যখন তার হাতে অর্থ বা সম্পদ আসে। তার মনে আনন্দ থাকে। সেই আনন্দেরই প্রকাশ ঘটে সামাজিক উৎসবে। দীর্ঘ ঐতিহ্যের উৎসবগুলি তাই কৃষির সঙ্গে, ফসলের সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলার শারদোৎসব, মহারাষ্ট্রের গণেশবন্দনা, আসামের বিহু, দক্ষিণ ভারতের ওনাম, পোঙ্গল, গুড়ি পরব, গুজরাতের গরবা, পাঞ্জাবের লোহরি --- সবই কোনও না কোনওভাবে ফসলের উৎসব। বাঙলায় এই দিন গঙ্গাসাগরের সঙ্গে অবশ্য ফসলের যোগ নেই, আছে ধর্মের যোগ। পৌষ মাসের শেষ দিনে, জ্যোতিষ মতে, সূর্য নিজের কক্ষপথে মকর রাশিতে প্রবেশ করে। তাই এর নাম মকর সংক্রান্তি। এলাহাবাদে, গঙ্গাসাগরে ও নানা নদনদীতে এদিন ধর্মপ্রাণ মানুষ মকরস্নান করেন। মকর সংক্রান্তি পালনের উল্লেখ আছে মহাভারতেও। গঙ্গাসাগরে যে মন্দিরকে ঘিরে লাখ লাখ মানুষের, যাঁদের বড় অংশই উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মানুষ ও সাধু, সেই মন্দিরও বাঙলার নয়। তার মালিক উত্তর প্রদেশ সরকারের কপিল মুণি ট্রাস্ট। এই আশ্রমে যে বিপুল টাকা ও ধনদৌলত আসে প্রণামী ও দানে, সবটাই উত্তর প্রদেশের। রাজ্যের দায়, সেই মেলার পরিকাঠামো থেকে নিরাপত্তার সব ব্যবস্থা নিজের খরচে করে দেওয়া। এটুকু বাদ দিলে বাঙলায় এদিনের সব উৎসবই ফসলের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতের নানা রাজ্যেও এই দিনের উৎসবে কৃষিপণ্যের যোগসূত্র আছে। এই সময়ে খেজুড় রস থেকে তৈরি সুগন্ধি গুড় পাওয়া যায়। খেজুড় গুড় দিয়েই বাঙলায় যেমন পৌষ পার্বনের আয়োজন, মহারাষ্ট্রে বা কর্নাটকেও তাই। মহারাষ্ট্রে এদিন তিল আর গুড় দিয়ে তৈরি নাড়ু বা লাড্ডু খাওয়ার উৎসব। উৎসবের নাম ‘তিলগুল’। কর্নাটকে একই উৎসবের নাম ইল্লু বিল্লা। বাঙলার পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ পার্বন তেমনই এক ফসলের উৎসব। ফসলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সংস্কৃতির বহমান ধারা। পৌষ সংক্রান্তিতে কেন্দুলিতে তাই আউল বাউলের আখড়াই এই দিনের মূল আকর্ষণ হয়ে যায়, অজয় নদে স্নান নেহাতই আনুষ্ঠানিকতা। প্রায় ৩৫০ আখড়ায় এদিন আউল, বাউল, খ্যাপা, ফকিররা আসর বসান। সারা রাত চলে আখড়ায় গানের আসর। হাজার হাজার মানুষ আউল বাউলের টানে পিপাসার্ত হৃদয়ে আসেন। তিনদিন ধরে চলে কেন্দুলি মেলা। এবার প্রশাসনের নির্দেশে শুধু অজয় নদে স্নান হবে, আখড়ার আসর আর মেলা বন্ধ।
বাঙলায় মুলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরের পৌষ সংক্রান্তিতে বিশেষ উৎসব। ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরের আলাদা কোনও ইতিহাস নেই। প্রিন্স দ্বারকানাথের ভাই পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের গোপীমোহনের কন্যা ব্রহ্মময়ীর নামে এই মন্দির। ব্রহ্মময়ী বিয়ের আগে তিনি গিয়েছিলেন গঙ্গায় স্নান করতে। স্নানের পর জল আনতে গিয়ে তিনি ডুবে যান। তার শবদেহ ভেসে ওঠে মুলাজোড়ে। গোপীমোহন ঠাকুর সেখানে কন্যার স্মৃতিতে কালীমন্দির বানান। মন্দিরের ভিতরে বসান তিনটি শিবলিঙ্গ - আনন্দশঙ্কর, গোপীশঙ্কর ও হরশঙ্কর। আর মন্দিরের পিছনে বানান কৃষ্ণমন্দির, মূর্তির নাম গোপীনাথ জিউ। গোটা পৌষ মাস জুড়েই ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরে বিশেষ পূজা হয়। তাকে ঘিরে মেলা বসে। শেষ দিনে হাজার হাজার মানুষ দেবীর উদ্দেশ্যে জোড়া মুলো অর্ঘ্য দিয়ে পূজা নিবেদন করেন। তারপর থেকে সেই বছর আর মুলো খান না। এই রীতির পিছনে ধর্মীয় কোনও কারণ পাওয়া যায় না। বাস্তব কারণ, মাঘ মাস থেকেই মূলো পেকে যেতে থাকে। শাল হয়ে যায়। তাই একটি উৎসবের আবহে মুলো খাওয়া বন্ধের আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু বাঙলায় এদিন লৌকিক উৎসবের অঙ্গ পিঠে, পায়েসের উৎসব। প্রবাদ আছে, শীতের পিঠা ভারি মিঠা। নতুন আমন ধান, খেজুড়ের সুগন্ধি গুড়, নারকেল কোড়া আর দুধ দিয়ে তৈরি কতরকম যে পিঠে আর মিষ্টান্ন এইদিনের সঙ্গে জড়িয়ে! সেই কবে পিঠা খাওয়া নিয়ে কৃষক ঘরের কথা লিখেছেন ঈষ্বরচন্দ্র গুপ্ত – আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর। গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার।। আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে। ঘেঁসে ঘঁসে বসে গিয়া আসনের কাছে।।
পৌষ সংক্রান্তির পিঠা খাওয়া নিয়ে বেগম সুফিয়া কামাল লিখেছিলেন, “পৌষ মাসের পিঠা খেতে বসে, খুশিতে বিষম খেয়ে আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে, মায়ের বকুনি পেয়ে।”
বাঙলার মায়েরা কত রকম পিঠা বানাতেন! তার কাছে কেক-পেস্ট্রি, পিজ্জা-পাস্তা, ধোসা, ধোকলা দ্শ বিশ গোল খায় আজও। ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা, পাকন পিঠা, পুলি পিঠা, মিঠা পিঠা, চিতই পিঠা, পাতা পিঠা, ঝাল পিঠা, নারকেল পিঠা নাম শুনলেই জিভে জল গড়ায়। কোনও কোনও মা ছিলেন নিপুন শিল্পী। তাঁরা বানাতেন নকশা পিঠা, ঝিনুক পিঠা, জামদানি পিঠা, সূর্যমুখী পিঠা, গোলাপ পিঠা ইত্যাদি। এছাড়া ক্ষীরপুলি, নারকেলপুলি, আনারকলি, দুধসাগর, দুধপুলি, রসপুলি, দুধরাজ সন্দেশ, আন্দশা, মালপোয়া, পাজোয়া নামধারী মিষ্টির কথা কি ভোলা যায়? তা হলে আজও আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়াবাসী বাঙালিরা এই দিনে পিঠা উৎসব করে কেন! ঝাড়খণ্ডে সিংভূম ও ধলভূম পরগণার পাশাপাশি বাঙলার বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায়; ঝাড়গ্রামে ও আসানসোলের আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের সমাজে পালিত হয় টুসু উৎসব। টুসু লৌকিক দেবী। মেয়েদের উৎসব। লক্ষণ ভাণ্ডারী লিখেছেন “দলে দলে কুমারীরা গায় টুসু গান”। তার কবিতায় আছে – মকরসংক্রান্তি আজি কর পূণ্যস্নান, অজয় নদীতে আজি টুসুর ভাসান। ভোর হলে সকলেই টুসু নিয়ে আসে, ফুলমালা নিয়ে টুসু নদী জলে ভাসে।
 টুসু গানের মূল উপজীব্য লৌকিক ও দেহজ প্রেম। গানে কল্পনা, দুঃখ, আনন্দ, মেয়েলি দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, অভীপ্সা, বিদ্বেষের পাশাপাশি সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সমকালীন রাজনীতি ছাপ পড়ে। বাঙলাকে বিহারের সঙ্গে সংযুক্তির বিরুদ্ধে পুরুলিয়াকে বাঙলার মধ্যে রাখার জন্য বিরাট আন্দোলনে টুসু সত্যাগ্রহ হয়েছিল। টুসু পরবে পুজোর পর মেয়েরা টুসুর দোলা নদীতে বা জলাশয়ে ভাসান দেয়। ‘টুসু’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তুষ থেকে। তুষ মৃত ধানের দেহ। সেই মৃতদেহকে ভাসান দিয়ে নতুন ফসলের আবাহনই টুসুর মূল বার্তা।
আরেকটি প্রাচীন কবিতা পড়ে নিই। ‘পৌষ পার্বণ” কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন,
“ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা।।
বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার।।
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া।।
'চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে
কহ দেখি কি হইবে নয় রেক চেলে?
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি।।
টুসু গানের মূল উপজীব্য লৌকিক ও দেহজ প্রেম। গানে কল্পনা, দুঃখ, আনন্দ, মেয়েলি দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, অভীপ্সা, বিদ্বেষের পাশাপাশি সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সমকালীন রাজনীতি ছাপ পড়ে। বাঙলাকে বিহারের সঙ্গে সংযুক্তির বিরুদ্ধে পুরুলিয়াকে বাঙলার মধ্যে রাখার জন্য বিরাট আন্দোলনে টুসু সত্যাগ্রহ হয়েছিল। টুসু পরবে পুজোর পর মেয়েরা টুসুর দোলা নদীতে বা জলাশয়ে ভাসান দেয়। ‘টুসু’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তুষ থেকে। তুষ মৃত ধানের দেহ। সেই মৃতদেহকে ভাসান দিয়ে নতুন ফসলের আবাহনই টুসুর মূল বার্তা।
আরেকটি প্রাচীন কবিতা পড়ে নিই। ‘পৌষ পার্বণ” কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন,
“ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা।।
বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার।।
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া।।
'চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে
কহ দেখি কি হইবে নয় রেক চেলে?
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি।।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার এই আউনি বাউনি হল পৌষ পার্বনের আরেক লৌকিক উৎসব। এর আগের নাম ‘আগলওয়া’। এই উতসবের কথা আছে গবেষক তারাপদ মাইতির ‘আউনি বাউনি’ এবং ড. দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত ‘বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ’ গ্রন্থে। আউনি বাউনি শস্যের উৎসব। অগ্রহায়ন মাস ছিল হিম ঋতুর প্রথম মাস। হেমন্তের পাকা আমন ধান ছিল বছরের প্রথম পাকা ফসল। আমনের কাহন কাহন ধান ঘরে উঠলে পর কৃষকের মনে আনন্দের হাসি ছড়াতো। বছরের প্রথম ফসলকে অতিপবিত্র ও সৌভাগ্যদায়ক মনে করে কৃষকরমনী তিনছড়া করে ধানের শিসের সঙ্গে মুলোর ফুল, সরষে ফুল, আমপাতার বিনুনি তৈরি করতেন। তারই নাম ‘আউনি বাউনি’। এই আউনি বাউনি বাঁধা হতো ধানের গোলায়, ঢেঁকিতে, বাক্সপেটরায়, আলমারীতে, ট্রাঙ্ক বা তোরঙ্গে আর চালের জালায়। ঘরের ও গোয়াল ঘরের খড়ের চালায় গুঁজে দেওয়া হয় আউনি বাউনি। নজর রাখা হতো, সারা বছর যেন সেটি সেখানে সমর্যাদায় থাকে। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। হারায় না ন্সেই সংস্কৃতি, যার শিকড় থাকে গ্রামে। গ্রামে গ্রামে আজও কৃষক রমনীরা আউনি বাউনি বাঁধেন। নানা রকমের পিঠা বানান পৌষ পার্বনে। কিন্তু সারা দেশের কৃষকের মাথায় আজ চেপে বসেছে সর্বনেশে তিন আইন। নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষকরা তো নানা রাজ্যে রাস্তার উপরে অবস্থান করছেন। এ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৫০ জনের বেশি কৃষক। কৃষকদের মনেই তো আজ আনন্দ নেই। কৃষক রমনীরা কি আউনি বাউনি বাঁধছেন? পৌষ পার্বন কি আর আগের মতো থাকবে?



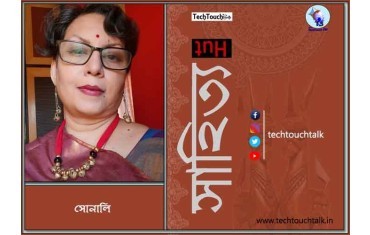
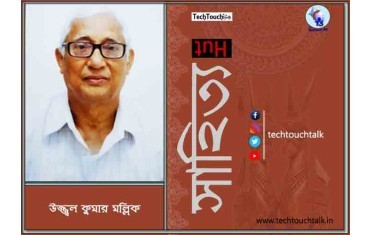
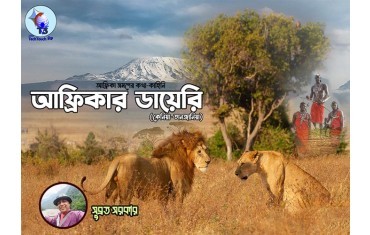
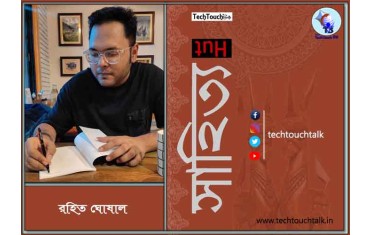
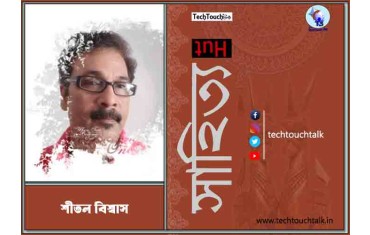
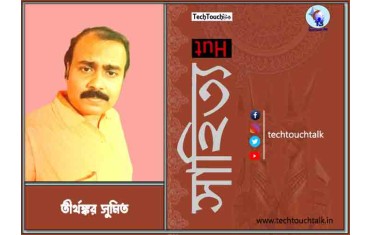

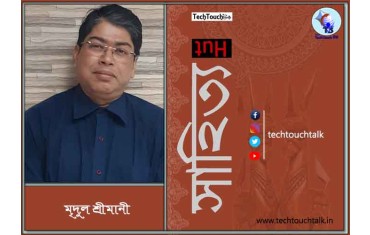
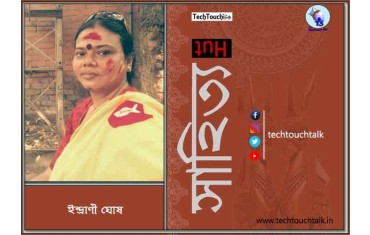
0 Comments.