- 11
- 0
ধারাবাহিক প্রবন্ধে তপশ্রী পাল (পর্ব - ৪৭)

আলাপ
এবার বলি অপর যে নৃত্য রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় এবং রবীন্দ্র নৃত্যে যার চলন ও মুদ্রা খুব বেশী ব্যবহার হয় সেই মণিপুরী নৃত্যের কথা! বললেই মনে পড়ে চিত্রাঙ্গদার কথা, তাই না? আদতেই এই নাচে কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা অর্থাৎ মার্শাল আর্টের ব্যবহার প্রচুর! মণিপুর রাজকন্যার মতোই সে নাচ কঠিনে কোমলে। একদিকে যেমন মার্শাল আর্টের ব্যবহার, অপরদিকে তেমনই লালিত্যময় অঙ্গভঙ্গী ও কৃষ্ণরাধা লীলা ফুটে ওঠে এই নাচে। এই নাচে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব যেমন আছে, তেমনই আছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাভা সুমাত্রা ইন্দোনেশিয়ার নাচের প্রভাব। মণিপুরী নাচের উৎসস্থল মণিপুর। বৈদিক পুরাণ অনুসারে স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় যে সব নর্তক নৃত্য প্রদর্শন করতেন তাঁদের বলা হত গন্ধর্ব। মণিপুরী লোকেরা মনে করে যে তাঁরা এই গন্ধর্বদেরই বংশধর। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক মন্দিরেই নৃত্যরত গন্ধর্বমূর্তি দেখা যায়। তাই মণিপুরকে গন্ধর্ব-দেশও বলা হয়। মণিপুরের রাজারা আদিতে শাক্ত এবং পরে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁরাই মূলতঃ এই নাচের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাই এতে বৈষ্ণব এবং শাক্ত বা শৈব দুইয়েরই প্রভাব আছে। বৈষ্ণবীয় রীতিতে মণিপুরী নাচে কৃষ্ণের রাসলীলা এবং কৃষ্ণ রাধার প্রেম ও বিরহ খুব সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়। এ ছাড়াও মণিপুরী উৎসব “লাই হারাওবা” উপলক্ষ্যে জঙ্গলের কাষ্ঠদেবতা উমঙ্গ লাই এর উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হয় এই নৃত্য। কৃষ্ণলীলা ছাড়াও রামায়ণ ও মহাভারতের নানা গল্পও মণিপুরী নাচের উপজীব্য হয়। কথিত আছে বারো বৎসর বনবাসের সময় তৃতীয় পান্ডব অর্জুন মণিপুরে গিয়ে পৌঁছন এবং সেখানে তিনি মণিপুরের সুন্দর ঢেউ খেলানো পর্বত উপত্যকায় মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রেমে পড়েন। মণিপুর রাজকন্যা তাঁর রূপে নয়, তাঁর সাহস ও গুণ দিয়েই অবশেষে জিতে নেন অর্জুনের মন। তাদেরই সন্তান বব্রুবাহন। সেই গল্পও মণিপুরী নৃত্যের উপজীব্য হয়। মণিপুরী আদিবাসীরা বৃক্ষ বা কাষ্ঠ দেবতা “উমঙ্গ লাই”য়ের উপাসক। তাঁরা নাচকে বলে “জাগোই”। “লাই হারোবা” উৎসবে তারা নটরাজ শিবের নানা ভঙ্গী ফুটিয়ে তোলে নৃত্যের মাধ্যমে। এ ছাড়া মণিপুরে পালিত হয় মৈরাং পরব। মণিপুরী উপকথা অনুসারে রাজা চিংখুবার কন্যা থৈবী এবং এক অনাথ বালক খাম্বার প্রেমের গল্প নিয়ে গড়ে উঠেছে এই উপকথা। একজন পুরুষ ও একজন মহিলার দ্বৈত নৃত্যে ফুটিয়ে তোলা হয় এই গল্প।
ঋক বেদ অনুসারে ভোরের দেবী ঊষা, যিনি সূর্যদেবতার ভগ্নী বা মতান্তরে কন্যা। মণিপুরে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী তিনিই মণিপুরী মহিলাদের নৃত্যশিক্ষার প্রথম গুরু। বলা হয়ে থাকে, তিনি মুখে মুখে এই নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন মণিপুরী মহিলাদের। এই বিশেষ ধরণের মণিপুরী নৃত্যের নাম “চিংখেইরোল মণিপুরী নৃত্য গুরুদের বলা হয় “গন্ধর্ব”। মণিপুরে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে এবং বিবাহের সময় নৃত্য প্রদর্শিত হয়।
খ্রীষ্টিয় পনেরোশো শতাব্দী থেকে মণিপুরের রাজারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। রাজা চারাই রংবা ১৭০৪ সালে প্রথম বৈষ্ণব হন। ১৭১৭ সালে মুসলিম রাজা গরীব নওয়াজ মণিপুর দখল করেন। এমনকি তিনিও শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাবিত হন। এর ফলে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ঘিরে গীত ও নৃত্যের প্রসার বাড়ে। এমনকি ১৭৩৪ সালে শ্রীরামের জীবন অবলম্বনে মণিপুরী নৃত্যনাট্য তৈরি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র, যাকে জয়সিং মহারাজাও বলা হয়, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মেইতেই উপজাতির রাজা নিংথাউ চিংথ্যাং খোরবা, যিনি গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন, তাঁর নির্দেশে প্রকৃত মণিপুরী নাচের প্রচলন হয়। মেইতেই উপজাতির এই রাজাকেই মণিপুরী নাচের প্রধাণ প্রবর্তক বলে ধরা হয়। তিনিই প্রথম মণিপুরী নাচের প্রকরণগুলি লেখেন এবং সঠিকভাবে সাজান। তিনি তিন ধরণের মণিপুরী রাসলীলা নৃত্যের প্রচলন করেন। সেগুলি হল “কুঞ্জ রাস”, “বসন্ত রাস” এবং “মহা রাস”। নৃত্যের মূল নিয়মগুলি ও প্রকরণ তিনি গোবিন্দ লীলা বিলাস বলে একটি গ্রন্থে গ্রথিত করেন। এ ছাড়া তিনি আরো অনেকগুলি নৃত্য, যেমন আচৌবা ভাঙ্গি পারেং ও খুম্বা ভাঙ্গি পারেং নাচ তৈরী করেন, কুমিল নাচের পোশাক স্থির করেন এবং বিভিন্ন মন্দিরে এই নাচের প্রচলন করেন। তিনি লোকমঞ্চে রাসলীলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।
এরপর ঊনবিংশ শতকে মহারাজা গম্ভীর সিং ও চন্দ্রকীর্তি সিং “নিত্য রাস” নৃত্যাঙ্গ তৈরী করেন। এ ছাড়া প্রথম জন “গোষ্ঠ বৃন্দাবন পারেং” ও “গোষ্ঠ ভাংগি পারেং” নামক দু ধরণের তান্ডব নৃত্যের প্রচলন করেন। দ্বিতীয় জন আবার “বৃন্দাবন ভাঙ্গি পারেং” ও “খ্রুম্ব ভাঙ্গি পারেং” নামে দুধরণের লাস্য নৃত্য নির্মাণ করেন। এই রাস নৃত্যগুলির পূর্বে চৌষট্টি পাং চোলম বা মণিপুরী পুরুষ-নর্তকদের ঢোল নিয়ে ঘুরে ঘুরে উদ্দাম নৃত্যের প্রচলনও এঁরাই করেন। এই বিশেষ নাচটি দেখার মত। ১৮৯১ সালে ব্রিটিশরা মণিপুর দখল করে এবং মণিপুর পরাধীন হয়। এর ফলে মন্দিরে ভারতীয় নৃত্যগুলির প্রদর্শণ নিষিদ্ধ হয়। তা সত্ত্বেও ইম্ফলের গোবিন্দ মন্দিরে এই নাচ হতো। কিন্তু ১৯১০ সালে আইন করে নাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর বিরূদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। ১৯২০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে এই নাচ আবার নতুন করে প্রচলন করার উদ্যোগ দেখা দেয়। এই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ এক প্রধাণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। গুরুদেব এই নাচের সঙ্গে জাভানিজ ও বালিনিজ ড্যান্সের অনেক মিল খুঁজে পান। তেমনই সৌন্দর্যমন্ডিত ও লালিত্যপূর্ণ নৃত্যাঙ্গনাদের পদচারণা! ১৯১৯ সালে সিলেট অর্থাৎ চট্টগ্রামে প্রথম মণিপুরী গোষ্ঠ লীলা দেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং এতো মুগ্ধ হয়ে যান, যে তিনি গুরু বুধিমন্ত্র সিংকে শান্তিনিকেতনে নৃত্য ভবনে মণিপুরী নৃত্য ও বিশেষতঃ রাস লীলা নৃত্য শিক্ষাদানের জন্য আহবান করেন। এরপর ১৯২৬ সালে গুরু নবকুমারও শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। ক্রমে অনেকগুলি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের কোরিওগ্রাফি করেন এই দুই গুরু এবং অন্যান্য বিখ্যাত গুরুরা যেমন আতোম্বা সিং, নীলেশ্বর মুখার্জী এবং সেনারিক সিং রাজকুমার।
বিভিন্ন ঋতু অনুসারে মণিপুরী নৃত্য নানারকম ভাবে পরিবেশিত হয়। এই নাচের ভাবভঙ্গিমা খুব কাব্যিক, লালিত্যপূর্ণ, ধীর এবং সুষমামন্ডিত। প্রধাণ দুই ধরণের চলনকে বলে ‘চারি’ এবং ‘চালি’। শরতে তিনবার মণিপুরী নৃত্য প্রদর্শন হয় এবং বসন্তে একবার। সর্বদাই পূর্ণিমা রাতে এই নাচ করা হয়। বাসন্তী রাস নৃত্য হয় হোলির সময়। এ ছাড়া শস্য ঘরে তোলার পর অথবা দিওয়ালীর সময়ও নৃত্যের আয়োজন করা হয়। এই নৃত্যের মূল উপজীব্য হল রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম ও সুদেবী, রঙ্গাদেবী, ললিতা, ইন্দুরেখা, তুঙ্গবিদ্যা, বিশাখা, চম্পকলতা এবং চিত্রা নাম্নী গোপীদের মাঝে তাঁদের নৃত্য। এক একটি নাচ এক এক গোপিনীর উদ্দেশ্যে এবং সবচেয়ে বড় এবং মূল নৃত্যটি কৃষ্ণ ও রাধাকে নিয়ে। নৃত্যনাট্যে হস্ত ও পদ মুদ্রা এবং মুখভঙ্গীমার প্রয়োগে ফুটিয়ে তোলা হয় নাটক। অন্য কয়েকটি মণিপুরী নৃত্যে আবার প্রবল তান্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে অত্যন্ত দ্রুত নৃত্যও প্রদর্শিত হয়। পোশাকঃ মণিপুরী নাচে পুরুষেরা কোমর থেকে নীচ পর্যন্ত রঙিন ধুতি ও ঊর্ধাঙ্গে চাদর পরেন। যিনি কৃষ্ণ সাজেন তাঁর মাথায় থাকে ময়ূর পালকের মুকুট! মহিলা নৃত্যশিল্পীদের পোশাক অপূর্ব সুন্দর, মণিপুরী বিয়ের কণের মতো এই পোশাক, যাকে বলা হয় ‘পাটলোই’। সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট পোশাক হল ‘কুমিল’ কস্টিউম। এতে কোমর থেকে পরা হয় শক্ত সিলিন্ডারের মত গঠনের একটি স্কার্ট। তাতে সোনা রূপোর জরির কাজ, আয়না ও নানা রঙবেরঙ এর পাথর বসানো থাকে। বর্ডারে থাকে সুন্দর পদ্মের ছাপ। এর ওপরে আবার পাতলা কাপড়ের একটি ছোট্ট স্কার্ট কোমরে তিনদিকে আটকানো, যেন ফুলের মতো ফুটে থাকে। দেহের ঊর্ধাঙ্গে ভেলভেটের ব্লাউস এবং মাথায় ওড়না ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের মত মণিপুরী নাচে নূপুর পরা হয় না। মাথায়, গলায়, হাতে থাকে সুন্দর ফুলের গয়না। পিছনে গাওয়া হয় ধর্মীয় গান ও ভজন। মনে হয় যেন অপ্সরাগণ ভেসে বেড়াচ্ছেন। পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা যারা ঢোল বাজিয়ে নাচেন, তাঁদের পরণে থাকে সাদা ধুতি এবং মাথায় সাদা পাগড়ি। ঊর্ধাঙ্গে চাদরটি বাঁ কাঁধে শক্ত করে আটকানো থাকে আর ডান কাঁধে থাকে ঢোলকের ফিতেটি। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রঃ এই নৃত্যের প্রধাণ বাদ্যযন্ত্র হল পাং, বা ব্যারেল গঠনের ড্রাম, সিম্বাল বা করতাল, হারমোনিয়াম, বাঁশী, পেনা এবং সেম্বং। বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও থাকেন অন্ততঃ একজন গায়ক। পং চোলম নাচে, যেটি রাসলীলার আগে নাচা হয়, তাতে ঢোল কাঁধে পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা অসাধারণ পদমুদ্রার ব্যবহার করেন, লাফিয়ে দ্রুতবেগে ঘোরাও এই নাচের অঙ্গ। তেমনই কর্তাল চোলম নাচে ঢোলের তালে তালে করতাল বাজিয়ে গোল হয়ে নাচেন নৃত্যশিল্পীরা। এই দুই নাচ পুরুষেরা করলেও মন্ডিলা চোলম নাচ করেন দলবদ্ধভাবে মহিলারা। করতাল বাজিয়ে এই নাচ করেন তাঁরা ঢোলের তালে তালে। করতাল গুলি চুলের ট্রাসেলের লম্বা দড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে। গানের ভাষা সংস্কৃত, ব্রজভাষা বা মৈথিলী হতে পারে। পদগুলি সাধারণতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দ, গোবিন্দদাস, চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির লেখা থেকে নেওয়া হয়।
মণিপুরী নৃত্যের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পী হলেন গুরু বিপিন সিং এবং তাঁর ছাত্রী দর্শনা জাভেরী এবং তাঁর বোনেরা নয়না, সুভর্ণা, রঞ্জনা, দেবযানী চালিহা এবং প্রীতি প্যাটেল। বলবো গুরু বিপিন সিং ও প্রীতি প্যাটেলের নাচ দেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে।


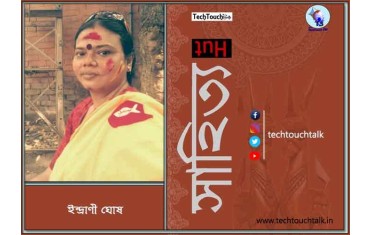
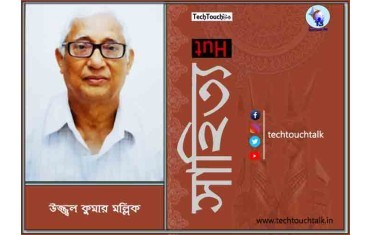


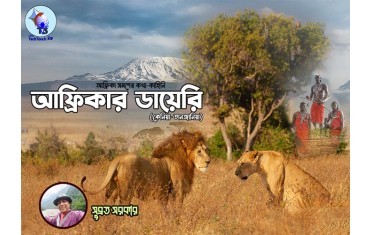
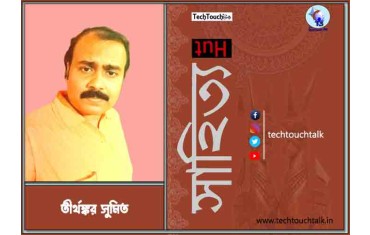
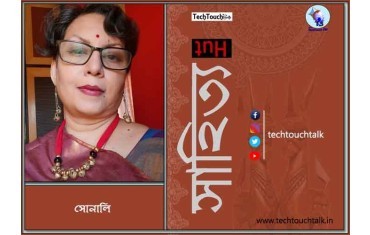
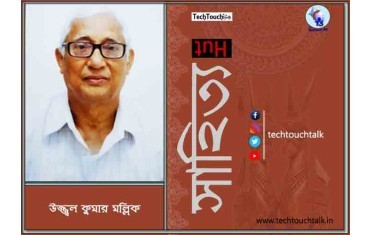
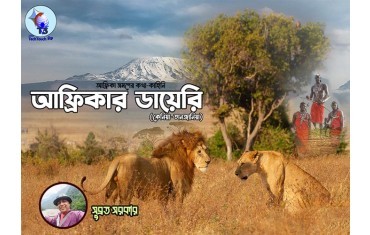
0 Comments.