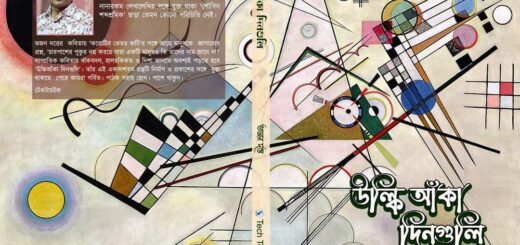রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প ১৮
৩ ওরা কাজ করে
মৃত্যুর কয়েকটি মাস আগে ১৯৪১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ( ১ ফাল্গুন ১৩৪৭) তারিখে শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন “ওরা কাজ করে” শীর্ষক কবিতাটি। সেখানে লিখেছেন “..রাজছত্র ভেঙে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;/ জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে;/ রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি/ শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।..”
১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়ায় গিয়ে তিনি ভেবেছিলেন:
“চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প’রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে–জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে– উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে রাশিয়ার সদর্থক ও ইতিবাচক দিকগুলি গভীর প্রভাব ফেলেছিল। সেই ভাল লাগার বোধ রাশিয়ার চিঠি ও অন্যত্র ধরা পড়েছে।
“পারস্যযাত্রী” গ্রন্থে ১৯৩২ সালে লিখেছেন: রুশীয় তুর্কিস্থানে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট অতি অল্প কালের মধ্যেই এশিয়ার মরুচর জাতির মধ্যে যে নূতন জীবন সঞ্চার করেছে তা আলোচনা করে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। এত দ্রুতবেগে এতটা সফলতা লাভের কারণ এই যে, এদের চিত্তোৎকর্ষ সাধন করতে, এদের আত্মশক্তিকে পূর্ণতা দিতে, সেখানে সরকারের পক্ষে অন্তত লোভের সুতরাং ঈর্ষার বাধা নেই।
মরুতলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত এই সব ছোটো ছোটো জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজন প্রভূত ও বিচিত্র। বহুজাতিসংকুল বৃহৎ সোভিয়েট সাম্রাজ্যে আজ কোথাও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মারামারি কাটাকাটি নেই। জারের সাম্রাজ্যিক শাসনে সেটা নিতান্তই ঘটত। মনের মধ্যে যে স্বাস্থ্য থাকলে মানবের আত্মীয়সম্বন্ধে বিকৃতি ঘটে না, সেই স্বাস্থ্য জাগে শিক্ষায় এবং স্বাধীনতায়।
(পারস্যযাত্রী, রচনাবলী ১২, পৃ ৪৫১)
রাশিয়ার চিঠির সমকালে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন, আমি যা বহুকাল ধ্যান করেচি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ হোল। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে। অল্প বয়সে জীবনের যা লক্ষ্য ছিল শ্রীনিকেতনে শান্তিনিকেতনে তা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হোক, সাধনার পথ অনেকখানি প্রশস্ত করেছি। নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেক কালের বেদনা রয়ে গেচে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না? (১৯৩০)
১৯৩০ সালের ৩০ অক্টোবর তারিখে রথীন্দ্রনাথকে কবি লিখেছিলেন, “আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেচে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।….
….যদি তুই রাশিয়ায় আসতিস এসম্বন্ধে অনেক তোর অভিজ্ঞতা হত।”
১৯৩৫ সালের ৭ মার্চ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, “সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। নানা ত্রুটি সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি।’ (চিঠিপত্র ১১, পৃ ১৪৫ – ৪৬)।
বত্রিশ বছর বয়সে, “চিত্রা” কাব্যগ্রন্থের “এবার ফিরাও মোরে” কবিতায় লিখেছিলেন:
“ওরে তুই ওঠ্ আজি ;
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন্ অন্ধকারামাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া ; বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার ; ”
আরো লিখেছিলেন:
“এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা — এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা — ডাকিয়া বলিতে হবে —
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে ;”
১৩২১ বঙ্গাব্দের ১৫ বৈশাখ তারিখে লিখেছিলেন:
শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।
আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
১৯৩৯ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন:
“ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও॥
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক–
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ওই মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরই ডাক।
ভয় করি না অজানারে,
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে দুর্দাড় বেগে ধাও॥”
এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিনতে গেলে চার্লস ডারউইনের সমসাময়িক আর এক বিশ্বমনীষার কথা উল্লেখ করা দরকার। তিনি কার্ল মার্কস, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা। ইতিহাস ও অর্থনীতি কেমন করে পড়তে হবে, তার রূপরেখাটা কার্ল মার্কস ( ০৫ মে ১৮১৮ – ১৪ মার্চ ১৮৮৩) অন্যরকম করে গড়ে দিয়েছিলেন। মানুষে মানুষে সম্পর্ক কিসের উপর দাঁড়িয়ে, সে নিয়েও পৃথিবীকে অনেক কিছু ভাবতে শিখিয়েছিলেন তিনি।
ইতিহাস, অর্থনীতি, আর দর্শনকে গভীর বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়ে পাঠ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিয়ম আবিষ্কার করেছেন মার্কস। অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। জন্ম দিয়েছিলেন শ্রমিক মুক্তির দিশা। ১৮৬৭ – ১৮৮৩ এই সময়কালে মার্কস লিখেছেন “দাস কাপিতাল”, বা “পুঁজি” নামে মহাগ্রন্থ। তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ( ২৮ নভেম্বর ১৮২০ – ০৫ আগস্ট ১৮৯৫), আর এক মহান দার্শনিক। তিনি ১৮৪৫ সালে পঁচিশ বছর বয়সে “দি কণ্ডিশন অফ দি ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যাণ্ড” নামে গুরুত্বপূর্ণ একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। দর্শনের সূত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনে ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিকশিত করেছিলেন। দুজনে মিলে শোষণমুক্তির একটা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলেন। এটাই মার্কসবাদ।
১৮৪৮ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। এটি একটি প্রচার পুস্তিকা। ঠিক ঠিক বলতে গেলে প্যামফ্লেট। কিন্তু এই পুস্তিকার মতো সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন কোনো পুস্তিকা আর নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মার্কসবাদী ছিলেন এমন কথা বলার কোনো মানে নেই। রবীন্দ্রনাথ সততার সঙ্গে নিজের অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অবস্থান স্পষ্ট করে বলেছেন। কিন্তু এও বলা দরকার তিনি ভিতরে ভিতরে ভীষণ ভাবে গরিব মানুষের মুক্তির রাস্তাটা খুঁজে পেতে চাইছিলেন। সেই আকুতি থেকে ১৯৩০ সালের সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শনকে “এ জন্মের তীর্থদর্শন” বলে পরিচিত করেছেন।
রক্তকরবী, মুক্তধারা, এই নাটকগুলি পড়লে শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা কিভাবে মানুষকে অমানুষ বানাতে চায়, আর তার থেকে বেরিয়ে আসতে হলে, শুধু ভালো ভালো কথা নয়, একটা সংঘর্ষের প্রয়োজন হয়, একথা বেশ টের পাওয়া যায়।
“দুই বিঘা জমি” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। এই কথাটা রাজাকে চোর হিসেবেই চেনায়। আর কার্ল মার্কস মুনাফা করাকে আইনসঙ্গত দস্যুবৃত্তি বলেছিলেন। এ দুটো কথার মধ্যে মিল অনেকটা।
সমাজ যে আসলে শ্রেণিবিভক্ত এবং ক্ষমতাবানদের হাতে ক্ষমতাহীনরা কেবলই নিষ্পেষিত হতে থাকে, এই কথাটা “পুরাতন ভৃত্য” কবিতাটি পড়লে আর অস্পষ্ট থাকে না। কৃষ্ণকান্ত লোকটি বাস্তবে তার মালিকের বাড়িতে একরকম ক্রীতদাসত্বের জীবন যাপন করে। কবি লিখেছেন, ‘যত পায় বেত, না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে’। তাকে যখন তখন গালি দেওয়া চলে। পাজি হতভাগা গাধা, কৃষ্ণকান্ত তার কর্মস্থলে এইসব শব্দে নিয়মিত আপ্যায়িত হয়ে থাকে। একটি সাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত ঘরেও যে একটি হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সৌজন্যে ক্রীতদাসত্বের জীবন যাপন করে চলে। ঘটনা পরম্পরায় কৃষ্ণকান্ত যদি সংক্রামক রোগাক্রান্ত প্রভুকে শুশ্রূষা করতে গিয়ে পর্যাপ্ত সুরক্ষা না নেওয়ার কারণে নিজেও সংক্রামিত হয়ে পড়ে। একমাত্র সেই সময়েই প্রভু বুঝতে পারেন, কৃষ্ণকান্ত তাঁকে কতদূর ভালবাসে। রাশিয়ার চিঠির গোড়াতেই ওই যে লিখেছিলেন, সব চেয়ে কম খেয়ে, কম প’রে, কম শিখে, বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা রোগে মরে, উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরে–জীবনযাত্রার জন্য যত-কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত, এই পুরাতন ভৃত্য কবিতায় সেই কথাই যেন আগেভাগে বলা হয়ে উঠেছে।
এই বাংলায় ইংরেজ প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কারণে কৃষির কোনো উন্নতি ছিল না। তার উপর কুটির শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এর সম্পূর্ণ সুবিধাটুকু নিয়েছিল মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শহুরে মানুষ। গ্রামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে ভূমিহীন মানুষ এঁদের বাড়িতে চাকরের কাজ করত। যে ইংরেজ নিজের দেশে স্বাবলম্বন ও পরিশ্রমকে শ্রদ্ধা করত, সেই তারাই ভারতে এসে শাসক সেজে গৃহে কর্মরত চাকরের সংখ্যা দিয়ে অবস্থা কৌলীন্য জাহির করত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ইংরেজ প্রভুর অনুকরণে নিজের নিজের বাড়িতে চাকর বাকর রাখত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন সহ বহু লেখায় এইসব চাকরবাকরের চোখের জল জড়িয়ে আছে। বলা দরকার, এই চাকরশ্রেণির লোকগুলি প্রকৃতই সর্বহারা। এবং স্বজাতি ও স্বধর্মী মানুষের কাছে নিদারুণ অত্যাচারের ও বঞ্চনার শিকার। জাত এবং ধর্মের দোহাই পেড়ে শ্রেণিশাসনকে বাগ মানানো যায় না।
‘গোরা’ উপন্যাসে গৌরমোহন নামে শিক্ষিত ও মেরুদণ্ডবান যুবকটি কেবলই ফোঁটা তিলক কেটে আচার অনুষ্ঠান মেনে সমস্ত রকম ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলতাকে ধর্মপালনের মোড়কে সমর্থন করে এক কপোলকল্পিত ভারতের স্বাধীনতার পূজা করছিল। তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল গ্রামে গিয়ে। সেখানে গরিব মানুষ কী জঘন্যভাবে কুসংস্কারে ডুবে আছে তা গোরা দেখতে পেল। আরো দেখতে পেল অর্থনৈতিক পরিচয়ে তার সমপর্যায়ের বাঙালি হিন্দুরা কিভাবে ব্রিটিশ প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটদের তোষামোদ করে। দেশের বিচার ব্যবস্থায় ভদ্রলোকের জন্য একরকম বিচার আর নিঃস্ব গরিবের জন্য ব্যবস্থাটা অন্য রকম। উপন্যাসের গোড়াতেই মুসলমান মুটে তার উপর অত্যাচারের প্রতিকারের ভার অদৃশ্য ঈশ্বরের উপর চাপিয়ে দিলে গোরার শিক্ষিত মন তার প্রতিবাদ করেছে।
ধীরে ধীরে গোরা ভারতে ব্রিটিশ শাসন, তার অমানুষিকতা, গরিব ভারতীয়ের লাচারি, আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদটা স্পষ্ট করে দেখতে পায়। ভারতের মুক্তি যে ওই গরিব মানুষের সচেতন সাবলীল সংঘশক্তিতে, ধর্মীয় উদ্দীপনায় নয়, এই কথাটা পাঠককে বুঝতে রবীন্দ্রনাথ সাহায্য করেন।
কার্ল মার্কস শিখিয়েছেন, Religion is the opium of the masses, ধর্ম জনগণের আফিম। বলেছেন, The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোরাও ফোঁটা তিলক কাটা বারব্রত পালন করা হিন্দুধর্ম এবং পানুবাবু ও বরদাসুন্দরীদের ব্রাহ্মধর্ম, এই দুইয়েরই অন্তঃসারশূন্য অবস্থাটা টের পায়।
কার্ল মার্কস বলেছেন, Capital is dead labour, which vampire-like, live only by sucking living labour, and live the more, the more labour it sucks.
এই কথাটার সঙ্গে রক্তকরবী নাটকের ঘটনাস্থল যক্ষপুরীতে সর্দারকুলের শীর্ষস্থানীয় পদাধিকারীর সম্বন্ধে নন্দিনী কী বলে তার খোঁজ নেওয়া যায়। নন্দিনী বলে, সর্দারের ভিতরে রস নেই, শুকিয়ে একেবারে লিকলিক করছে।
কার্ল মার্কস বলছেন, Social progress can be measured by the social position of the female sex.
গোরা উপন্যাসে ললিতা বিনয়ের সঙ্গে একই জাহাজে চলে এলে ছিছিক্কার হয়। কিন্তু সেই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাকে স্নেহের আশ্রয় দেন গোরার মা। রক্তকরবী নাটকেও অসচেতন কুসংস্কারে ডুবে থাকা খনিমজুররা নন্দিনীকে ডাইনি ভাবে, ভাবে যে ও ছেলেদের মন ভুলিয়ে তাদেরকে বিপদে ফেলে।
চতুরঙ্গ উপন্যাসে বাঙালি বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষের বেশ্যাগমনকে চিরে চিরে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর বিধবা যুবতী দামিনীকে নিয়ে শ্রীবিলাস ঘর বাঁধতে চাইলে বিরোধিতাও এসেছে সেখান থেকেই। একইসাথে তিনি দেখিয়েছেন শ্রীবিলাসকে নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছে নিচের তলার মানুষেরা।
স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্যকে নানা সৃষ্টিতে চিরে চিরে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। চতুরঙ্গে শিবতোষের আচরণ, গোরা উপন্যাসে আনন্দময়ীর প্রতি কৃষ্ণদয়ালের আচরণ, পরেশবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরীর আচরণ যেমন লক্ষ্য করা দরকার, তেমনই ভাবী পত্নী হিসাবে গণ্য করে সুচরিতার প্রতি পানুবাবুর ব্যবহারটাও নজরে রাখতে হবে। বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের পরিবারে মেয়েদের অবস্থানটা দেখাতে রবীন্দ্রনাথ পলাতকা কাব্যগ্রন্থে ফাঁকি কবিতায় বিনুর দাম্পত্যের গল্প বলেছেন। লিখেছেন, “নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে-আবডালে/ মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে;/ মিলন ছিল ছাড়া-ছাড়া..”
ওই পলাতকা কাব্যগ্রন্থের মুক্তি কবিতায় লিখেছেন:
“শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা–ঐ যে থামল যেন;”
১৩২৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্তিকে ( সেপ্টেম্বর অক্টোবর, ১৯১৯) লেখা পলাতকার এইসব কবিতা। যে মেয়েরা কচি বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছে, তারা বিয়ের বাইশ তেইশ বছর পরে এইসব বলছে। বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ঘরে নারীজীবনের সাংঘাতিক অপব্যয়ের প্রসঙ্গ লিখতে থাকেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র থেকে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ ( ১৯২৭ – ১৯২৯) পর্যন্ত লিখেছেন ‘মহুয়া’র কবিতা। সেখানে “সবলা” কবিতায় লিখেছেন: “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/ কেন নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা?” লিখেছেন: “যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী-/ আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।” লিখেছেন: “হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা-/ …উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের ‘পরে/ জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে /কণ্ঠ হতে/ নির্বারিত স্রোতে।”
আরো অনেক পরে, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে ২ আষাঢ় তারিখে ‘শ্যামলী’ কাব্যগ্রন্থের “বাঁশিওয়ালা” কবিতায় লিখেছেন: “তোমার ডাক শুনে একদিন/ ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে/ অন্ধকারের কোণ থেকে/ বেরিয়ে এল ঘোমটা খসা নারী। যেন সে হঠাৎ গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,…”
স্বাধীনতা পিপাসু মেয়েদের রবীন্দ্রনাথ কাছ থেকে দেখেছেন। এঁদের অন্যতম ভগিনী নিবেদিতা। তিনি তাঁর গুরু ও শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে ভারতীয় ধর্মচর্চার শিক্ষা পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু নিজস্ব দীপ্ত মনুষ্যত্বের স্পর্ধা প্রকাশ করতে গিয়ে গুরুর প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় সংগঠনটির কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হতে ভয় পান নি। তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। ১৩ অক্টোবর, ১৯১১ সালে মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে রক্ত আমাশয়ে ভুগে এই মহীয়সীর মৃত্যু হয়।
এই ১৯১১ সালেই ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ১৯ মার্চ গোটা ইউরোপ জুড়ে মহিলারা রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। মহিলাদের ভোট দেওয়ার অধিকার, জনপ্রতিনিধি হওয়ার অধিকার এবং একই কাজের একই মজুরির দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠলো ইউরোপের শহরগুলো। ওই ইংল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবীতে শহীদ হলেন এমিলি ডেভিডসন। ভারতের বিপ্লবীদের ওপর যে অত্যাচার পদ্ধতি প্রয়োগ করতো ব্রিটিশ সরকার, সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা শুরু হলো ভোটাধিকার দাবি করা মেয়েদের ওপর – জেলে অনশনরত মহিলাদের গলা বা নাক দিয়ে জোর করে টিউব ঢুকিয়ে তাদের খাওয়ানোর চেষ্টা চললো। ডিভোর্স, অ্যাবর্শন, যৌনতা, মাতৃত্ব – নারীদের অধিকারের কথা তুলে জনজাগরণের চেষ্টা চালিয়ে গেলেন আলেকজান্দ্রা কোলোনতাই, ক্লারা জেটকিন, রোজা লাক্সেমবার্গ। প্রেম, ভালোবাসা, বিবাহ, যৌনতা, পরিবার, মাতৃত্ব, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার – সমস্ত প্রশ্নে নারীদের সামনে এক নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটলো। লড়াইয়ের সাফল্যে শেষ পর্যন্ত ১৯২৮ এ ইংল্যান্ডের মহিলারা ভোটাধিকার পেলেন।
১৯১১ সালেই দ্বিতীয়বারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মাদাম মেরি কুরি। অসাধারণ প্রতিভা সত্ত্বেও কিভাবে পুরুষতন্ত্রের ছদ্মবেশে সমাজের অসম বিন্যাস তাঁকে আক্রমণ করে দাবিয়ে দিতে চেয়েছে, সে কথা আগেই এসেছে।
১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ছয় তারিখে বাংলার বীণা দাশ একুশ বৎসর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হল-এ বেঙ্গল গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর পাঁচ পাঁচটি বার গুলি ছোঁড়েন। অবশ্য পাঁচবারই ব্যর্থ হন। বীণাকে পিস্তল যুগিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কমলা দাশগুপ্তা। বিচারে বীণার নয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হলেও মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই তিনি ছাড়া পান।
ওই ১৯৩২ সালেই দেশের আরেকটি কোণায় চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান হয়। মাস্টারদা’র দলের মহিলা কর্মী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। দর্শন বিষয়ে স্নাতক হয়ে প্রীতিলতা শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি এগিয়ে আসেন। চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব ছিল স্থানীয়ভাবে ব্রিটিশ দম্ভ ও আত্মম্ভরিতার প্রতীক। ইউরোপিয়ান ক্লাবের প্রবেশ পথে লেখা ছিল ডগস্ অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ানস নট অ্যালাউড। এটা যে কোনো মর্যাদাবোধসম্পন্ন ভারতীয়কে আঘাত করার কথা। মাস্টার দার দল ইউরোপিয়ান ক্লাবের এই সীমাহীন ঔদ্ধত্যের নগ্ন প্রকাশকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন।
একুশ বছর বয়সের মেয়ে প্রীতিলতা পঞ্জাবী যুবক সেজে বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দিতে এগোন। ১৯৩২ সালের চব্বিশ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে এগারোটায় ক্লাবে ঢোকেন বিপ্লবীরা। ক্লাবে তখন জনা চল্লিশ ইউরোপীয়। তাঁদের দিকে গুলি ছোঁড়েন প্রীতিলতারা। এরপর ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। ধরা পড়ার আগে প্রীতিলতা আত্মহত্যা করেন। সেকালে এভাবে আত্মহত্যার প্রচলন ছিল বিপ্লবী মহলে।
বেথুন কলেজের ছাত্রী ছিলেন কল্পনা দত্ত। বিপ্লবী হিসেবে নিজেকে তৈরী করার জন্য স্কলারশিপের টাকায় সাইকেল কিনে কাকভোরে সবার চোখের আড়ালে কলেজের মধ্যেই শিখতো সাইকেল। প্রতি রবিবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নৌকা চালানো অভ্যাস করতেন। বেথুন কলেজের নানা আন্দোলনে যোগ দিতেন। তারপর মহান বিপ্লবী সূর্য সেনের ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির সদস্য হয়ে চট্টগ্রামে নিজের পড়ার ঘরে বসে বোমার জন্য গান কটন তৈরি করে পাঠিয়ে দিতেন জেলের ভেতরে। এমনই দুঃসাহসী ছিলেন কল্পনা দত্ত।
১৯৩১ সালের ডিনামাইট ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার আগের দিনেই পুলিশের নজরবন্দী হলেন কল্পনা। তবে কল্পনা কিন্তু আটকে থাকার মেয়ে ছিলেন না। তিনি রাতে পালিয়ে সূর্য সেন, নির্মল সেনের সঙ্গে গ্রামে গিয়ে দেখা করে আসতেন। শিখে নিয়েছিলেন রাইফেল চালানো। পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাথে দল কল্পনাকেও দায়িত্ব দিয়েছিল। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী মাস্টারদা ধরা পড়লেন। কিছুদিন আত্মগোপনের পর ১৯ মে কল্পনাও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেলে গেলেন। তাঁদের নামে শুরু হল ” চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি কেস”। মামলার রায়ে সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির আদেশ হল আর কল্পনার সাজা হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অনেক চেষ্টার পর দ্বীপান্তরের আদেশ স্থগিত হয়েছিল তাঁর।
জেলে থাকতেই বিভিন্ন বই পড়ে কমিউনিজমের ওপর আগ্রহ বেড়েছিল কল্পনার। এইসময়েই ঘটল এক অভাবনীয় কাণ্ড। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপরিসীম পরিশ্রমে ও আন্তরিক চেষ্টায় ১৯৩৯ সালের ১ মে মুক্তি পেলেন অগ্নিকন্যা কল্পনা।
১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সদস্য হয়েছিলেন কল্পনা। বিয়েও হয়েছিল ওই বছরের শেষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সেই সময়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর সঙ্গে।
বিয়ের দিনেও কল্পনা ঘটালেন অকল্পনীয় এক কাণ্ড। বিয়ের লাল বেনারসী পরলেন না। পরে সেই বেনারসী কেটে তৈরি করেছিলেন পার্টি ফ্ল্যাগ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বাঁশিওয়ালা” কবিতার মেয়েটি বলে, কুয়াশার পর্দা-ছেঁড়া / তরুণ সূর্য আমার জীবন।/ সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয় / আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,/ উড়ে চলে অজানা শূন্যপথে/ প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো।। জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী…”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য সৃজনশীলতায় বিদ্রোহিণী মেয়েরা নারী হিসেবে আত্মসচেতন ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন হতে চেয়েছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে গলা তুলে নিরুপমা তার বাবাকে বলেছে, আমি কি একটা টাকার থলি, যে যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণই আমার দাম? দেবে না তুমি টাকা। গোরা উপন্যাসে ললিতা গোরার বিপদ শুনে সামাজিক রীতিনীতি টপকে পাড়ি দিয়েছে জাহাজে, সঙ্গে গিয়েছে রক্তসম্পর্কহীন বিনয়। আনন্দময়ী বিনয়কে শশিমুখীকে বিয়েতে রাজি হতে দেখে আপত্তি করেছেন। বিধবা হলেও দামিনী দু দুটি পুরুষের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে এসেছে। “ল্যাবরেটরি” গল্পের বিধবা সোহিনী বিজ্ঞান গবেষণায় অধ্যাপক মশায়কে উৎসাহ দিতে চুমু দিতে পিছপা হয় নি। নিজেদের শরীর মন ব্যক্তিত্বের উপর পূর্ণ স্বাধীনতা তারা অর্জন করেছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম যৌবনে লিখেছিলেন:
“আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি–
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ–
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা?
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।”
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঁচিশ বছর বয়সে ১৮৮৬ সালে এই গান লিখেছিলেন ও রাজনৈতিক অঙ্গনে গেয়েছিলেন। সমাজ দরদের নামে মিথ্যা আচরণের প্রতি কবির আন্তরিক ধিক্কার বরাবর ছিল। নারীজীবনের মর্যাদা আদায়ের প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে যে স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমন স্বাধীনতা চাননি।
বিধির বিধান, বিধাতা, এইসব শব্দগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক কবিতায় এসেছে। এটা আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঘোষণা করার জন্য নয়। বিধি বা বিধাতা আসলে সর্ব্যব্যাপী নিয়মের রাজত্ব, নিয়মের অলঙ্ঘনীয় উচ্চতাকে বোঝাতেই ব্যবহার করেছেন তিনি। কোনো ভক্তহৃদয়ের থেকে করেননি। একেবারে সাধারণ মানুষের জীবনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক করতে যুক্তিসংগত ভাবে যে কাজ করা উচিত, তাতে তাঁর আস্থা ছিল। শোষণ শাসন হতে সাধারণ মানুষের মুক্তিই সামাজিক নিয়ম। সেই নিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনসূত্রে বিধি এবং বিধাতা কথাগুলি এসে গিয়েছে।
এইসূত্রে আমরা আরেকজন মহান দার্শনিকের জীবনের দিকে তাকাব। তিনি বারুখ স্পিনোজা।