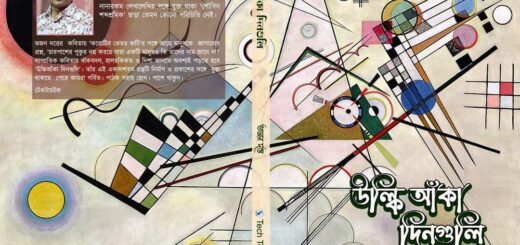সাপ্তাহিক ধারাবাহিক কথা সাগরে দীপশিখা দত্ত (অন্তিম পর্ব)

কাকাতুয়া বাড়ী
মেজো জেঠু
আজ বলবো আমাদের মেজজেঠুর কথা। আমরা বলতাম মেজ্জেঠু। ওই বাড়ীর সব সদস্যদের মধ্যে যাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগ ছিলো সবচেয়ে কম। ওই বাড়ীর সবচাইতে সুপুরুষ আর নীরব সদস্য ছিলেন দিদুর মেজো ছেলে শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার ঘোষ। কেউ কখনো ওনার গলার আওয়াজ শোনা তো দূর, কারো সাথে সেভাবে কথা অবধি বলতে শোনেনি! বড় ভাই ব্রহ্মচর্য পালন করলেন- দেখাদেখি মেজভাইও ইচ্ছে থাকলেও বিয়ে নামক শব্দটা সন্তর্পণে এড়িয়েই গেলেন- এইভয়ে, পাছে বৌ এলে মায়ের অযত্ন হয়। এমন মাতৃভক্ত সন্তানের দেখা সেযুগেও কমই মিলতো।
ওইটুকু বয়সে, ওবাড়ী যাতায়াতেই জেনে ছিলাম, পুরুষরাও পারে মহিলাদের মতো অফিস আর ঘরকন্না দুইই একসাথে সামলাতে। ছোট জেঠুর মৃত্যুর পর ক্রমশঃ দিদুও অশক্ত হয়ে গেলেন। শেষের বছরগুলোতে দিদুও আর ওপর নীচ করতে পারতেন না। দিদুকে যত্ন করে খেতে দেওয়া, কাপড় ধুয়ে দেওয়া, বিছানা পরিস্কার করা, ঘর ঝাড়া সবই করতেন মেজ্জেঠু।
আবার কাকাতুয়া বাড়ীর ভাঁড়ার ও রান্নার দায়িত্বেও ছিলেন উনি একাই একশো। দুষ্টু কাকাতুয়াটার একমাত্র গার্জিয়ান ছিলেন উনিই। সুন্দর সাহেবদের মতো ধবধবে ফর্সা গায়ের রং- একমাথা কোঁচকানো চুল, স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ মেজ্জেঠু সবসময় থাকতেন সবার চোখের আড়ালে।
আসমানী রংয়ের কলারওয়ালা পাঞ্জাবী আর ধুতিতে থাকতেন সবসময় ফিটফাট। ইছাপুর মেটাল ফ্যাক্টরীতে চাকরী করতেন। ভারী লাজুক মানুষটি, আমাদের ভালোবাসতেন খুউব কিন্তু কথা বলতে ভারী জড়োসড়ো! আমরা তখন কতো ছোটো ছিলাম, তাও আমাদের সঙ্গেও বেশী কথা বলতেন না কখনো। আর বাইরের লোকজন এলে সেই যে ভেতরবাড়ীতে ঢুকে যেতেন, আর কিছুতেই বাইরে আসতেন না। কথাবার্তা যা বলার সব বড়জেঠু বলতেন।
রোজ সকালে সাইকেলে চেপে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় তিনবাটির অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন কৌটোয় ভাত, মাছ, ডাল, ভাজা,রুটি, তরকারী ভরে নিয়ে কারখানায় যেতেন। কৌটোর গায়ে নাম খোদাই করা থাকতো ‘সুশীল’। সেসময় ফ্যাক্টরীর সাইরেনের শব্দে আমরা ঘড়ির সময় আন্দাজ করতাম। সাড়ে সাতটায় ফ্যাক্টরীর সাইরেনের ভোঁ পড়ার আগেই ঢুকতে হতো ফ্যাক্টরীতে।
রান্নার ভারী শৌখিন ছিলেন মানুষটি। বেলাদির রান্নার বই বলে সেসময় বাঙালীর ঘরে ঘরে বইটা বিরাজ করতো, সেই বই দেখে কতো রকমারী রান্না যে মেজ্জেঠু রবিবারে আমাদের জন্য রাঁধতেন তার ইয়ত্তা নেই- ওতে নিরামিষ- আমিষ দুইই থাকতো। খাসীর মাংস, হাঁসের ডিমের ডালনা, মাছের ডিমের বড়ার ডালনা, দৈ কাৎলা, ফুলকপি কড়াইশুটি দিয়ে কৈ মাছের ঝোল, তেল কৈ, মশলা বড়ি পোস্ত, মাংসের কিমা দিয়ে কড়াইশুঁটির ঘুগনি আরো কতো কি যে রাঁধতেন জেঠু- কি বলবো!
আসলে ও বাড়ীতে খাবার লোক তো কেউ ছিলো না,তাই জেঠু নিজের রান্নার যোগ্য সমঝদার মনে করতেন আমাদের। বড়ো আদর করে খাওয়াতেন আমাদের।
খুব ছোটবেলায় আমরা আর নিতান্তই ছাপোষা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে মানুষ হয়েছি। ওসব বাহারী খাবার আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে কমই হতো। মেজ্জেঠুর তৈরী হিং দিয়ে বানানো কড়াইশুঁটির কচুরী- আর বড়ো সাইজের নৈনিতাল আলুর সাদা আলুর দম আজও আমার মুখে লেগে আছে। সেসময় চন্দ্রমুখী আর জ্যোতি আলু নয়, নৈনিতাল আর দেশী আলু পাওয়া যেতো। ওনারা নৈনিতাল আলুই ব্যবহার করতেন। সাদা রংয়ের ময়দার ফুলকো লুচি আর সাদা আলুর তরকারী আমরা ওবাড়ীতেই খেতে শিখেছিলাম, কারণ আমাদের বাঙাল বাড়ীতে হলুদ ছাড়া তরকারী রান্নার কোনো চল ছিলো না।
কড়াইশুঁটি, কিশমিশ, কাজুবাদাম বাটা দিয়ে ঝালছাড়া মিষ্টি নিরামিষ ফুলকপির ডালনা, আহা অমৃত! আমাদের দুবোনের কারো সামান্য সর্দি হলেই ওবাড়ীতে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা তিনকোনা পরোটা আর আলুমরিচ বাঁধা ছিলো।
দোলে আর বিজয়ার পরে মেজজেঠু একা হাতে কুচো নিমকি, এলোথেলো, ঘুগনি আর জিবেগজা বানাতেন সব বাচ্চাদের জন্য। আমরাও নিয়ে যেতাম ঠাকুরমার হাতে তৈরী রাজভোগ সাইজের নারকেল নাড়ু।
রান্না করার সময় তরকারী একবার ছোট বাটিতে চাখতে দিতেন আবার দুপুরে দিতেন টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে বাড়ীতে খাবার জন্য। ছোটো জেঠু থাকতে তো আমাদের দুবোনের একজনের ছুটির দিনে নিমন্ত্রণ থাকতো ফি রবিবারে। মেজ জেঠু সুন্দর করে মেঝেতে আসন পেতে, কাঁসার থালায় সাজিয়ে খেতে দিতেন। আমরা ওখানে খেতাম কিন্তু ছোটজেঠু মারা যাবার পর আমাদের মনে হতো বাড়ীটা নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে- কোনো জনমনিষ্যি নেই। ওবাড়ীর মুখরোচক খাবার গুলো আমাদের দারুণ প্রিয় হলেও শেষের দিকে সেই স্বাদ আর পেতাম না – খুব বেশী মিষ্টি লাগতো খেতে।
আসলে মেজজেঠুর মধ্যেও ভাঙন ধরছিলো। ছুটির দিনে কাকাতুয়াটাকে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে জবা গাছের নীচে দাঁড়টা লটকে দিতেন। দেখতে দেখতে চোখের সামনে এলুমিনিয়ামকে পিছনে ফেলে টিফিন বাটি স্টীলের হলো- তাতেও লাল রং দিয়ে লেখা থাকতো ‘সুশীল’।
আপিস না থাকলে, সারাদিন ধরে মেজজেঠু একমনে রান্না করে যেতেন। উঠোনের কোনায় চওড়া শিলপাটায় উবু হয়ে বসে গোটা দুলে দুলে গোটা মশলা সুন্দর মিহি করে বাটতেন। যতোদিন বড়জেঠু সক্ষম ছিলেন ততদিন মেজজেঠুর ফরমায়েশি বাজার আনতেন বজ্জেঠু। উনি অশক্ত হয়ে পড়ার পর মেজ্জেঠু একাই বাজার, দোকান সবই করতেন। একটা জিনিস আনতে ভুলে গেলে চারশোবার যেতেন দোকানে। কাকাতুয়া পাখীটাও ততদিনে বুড়ো হয়েছে।কথা বললেও শোনে না, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলে না। সারাদিন দাঁড়ে বসে বসে ঝিমোয় আর নতুন কাউকে দেখলেই পরিত্রাহি চেঁচায়। ছোলা, আপেল ,পাকা পেয়ারা ঠুকরে ঠুকরে ফেলে দেয়- ঘর নোংরা করে বলে খুব বকুনি খায় মেজজেঠুর কাছে। প্রায়ই বলতেন, “তুই বড্ডো বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছিস বুড়ু! একদিন দেখবি তোকে কাউকে দিয়ে দেবো। তখন তুই বুঝবি মজা!”
রিটায়ারমেন্ট এর পর দুচারটে কথা মেজজঠু আমাদের সাথেই বলতেন। সারাজীবন ধবধবে ধুতি আর আকাশী পাঞ্জাবি পরা ফিটফাট ফুলবাবু মেজজঠুকে দেখতাম- হলুদের দাগ লাগানো তেলচিটে ময়লা লুঙ্গি পরে রান্না করতেন। রান্নার ফাঁকে ফোঁকড়ে বিড়ি ফুঁকতেন- বাইরের গাড়ী বারান্দায় বসার জায়গাটাতে এক পা তুলে বসে। ফর্সা শরীরের খাঁজে খাঁজে জমে থাকা ময়লা নিয়ে বড়ো অবহেলায় দিন কাটতো মেজ জেঠু র।দুপুরবেলায় কাকাতুয়ার ঘরটিতেই একটি লোহার খাটে মাথায় হাত দিয়ে শুয়ে থাকতেন। বড়জেঠুর অসুস্থতার সময় ধীরে ধীরে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন উনি।
কখনো গান শুনতে, সিনেমা -থিয়েটার দেখতে যেতে বা কারো বাড়ী যেতে দেখিনি ওনাকে। সংসার আর রান্নাঘরই ছিলো ওনার ধ্যান জ্ঞান। আসলে ছেলেরা পর হয়ে যাবে বলে দিদুও এসব সামাজিকতা, আত্মীয়তা থেকে ছেলেদের দূরে রাখতেন। তবুও আমাদের প্রতি কর্তব্যে কোনো ত্রুটি ছিলো না জেঠুদের।
আমরা তখন বেশ অনেকটাই বড়ো একদিন হঠাৎ আমাদের বললেন, “বাড়ীটাতো পুষ্পই নেবে! তাই গ্রাচুয়িটি আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাকটা হাসিকে দিলুম। কি অবলীলায় জীবনের শেষ সম্বলটুকুও বিলিয়ে দিলেন বোনদের! এখানেই বোধকরি এইসব গৃহী সন্ন্যাসীদের সার্থকতা।
তবে এই বোনেরাও শেষের দিকে আর মেজদার খোঁজ নিতেও আসতেন না। বড়জেঠু যখন সাংঘাতিক অসুস্থ তখন আমি চাকরী পেয়ে বাইরে চলে গেছি। মায়ের চিঠিতে জেনেছিলাম বড়জেঠু আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বড়জেঠু চলে যেতেই মেজ জেঠু একদম একা হয়ে গেলেন। শেষ কটা দিন বড়ো জেঠু কথা শুনতেন না বলে, মেজ জেঠু খুব বকাবকি করলে, দেখেছি ছেলেবেলার মতো দুইভাই ঝগড়া করতেন। ক্রমশঃ একাকীত্ব কবলিত মেজ জেঠু সময়ে রান্না বান্না, স্নান খাওয়া করা একরকম ছেড়েই দিলেন। সেসময় আমার ছোটবোন আর পাশের বাড়ীর দুটি বাচ্চা মেয়ে ওবাড়ীর উঠোনে খেলতে যেতো। অর্ধেক দিন ওরা দরজা ধাক্কিয়ে ফিরে আসতো- কেউ খুলে দিতোনা।
কোনোদিন খুলে দিলেও ওরা দেখতে পেত উস্কোখুস্কো চুলে মেজজেঠু উঠোনের রোদে বসে। উঠোনের জবা গাছের ফুলগুলো গাছেই শুকিয়ে যাচ্ছে। উঠোনটা শুকনো পাতায় ভরে রয়েছে। জলের অভাবে কামিনী গাছটার আধমরা দশা। এমন সময় একদিন শুনলাম ওনাদের আদরের বুড়ুকে কাকে যেন দিয়ে দিয়েছেন। শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। আসলে জ্ঞান হবার পর থেকেই কাকাতুয়াটাকে দেখে এসেছি তো তাই সেসময় বাড়ীটা কাকাতুয়াহীণ “কাকাতুয়া বাড়ী” হয়ে গেল।
এরপরের ঘটনা মায়ের মুখে শুনে আমি নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি। একদিন একগোছা স্টীলের দামী থালা- বাসন আমার ছোটো বোনকে দিয়ে বলেছিলেন,
“পাপু এগুলো বাড়ী নিয়ে যাও। আমি তোমাদের দিলাম।”
সেসময় ঘরে ঘরে কাঁসার থালায় খাওয়া হতো বলে, স্টীলের বাসনের প্রতি মানুষের এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিলো। বোধকরি সেই আকর্ষণেই ছোটোবোন সেগুলো বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলো আর মায়ের কাছে খুব বকুনি খেয়েছিলো।
কয়েকদিন পরে মা সেগুলো ফেরৎ দিতে গিয়ে দেখে- অনেকটাই দেরী হয়ে গেছে। মেজজেঠুর মধ্যে আস্তে আস্তে এলজাইমারসের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। একটা তরকারী রাঁধার জন্য জিনিস আনতে চারবার দোকানে ছুটতেন। বেশীরভাগ সময়ই রান্না করতেন না,বা করলেও আমাদের যে তরকারীপাতি দিতেন,তার বেশীরভাগই খাদ্যযোগ্য থাকতো না- আমরা ছোট থেকে কখনো খাবার ফেলতে শিখিনি বলে, কিছু আনতে ডাকলে কৌশলে এড়িয়ে যেতাম।
কিন্তু মেজজেঠু বাড়ী বয়ে এসে দিয়ে যেতেন। আস্তে আস্তে একদম অশক্ত হয়ে গেলেন উনি। বারান্দায় বসে একা একাই বিড়বিড় করে যেতেন অনর্গল আবার কখনো রাস্তার একপাল নেড়ী কুকুরকে দামী বিস্কুট কিনে খাওয়াতেন। কোনোদিন একদল বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মিষ্টির দোকানে জিলিপি সিঙ্গাড়া খাওয়াচ্ছেন পেটপুরে। আবার বাচ্চাগুলোকে খুচরো পয়সাও দিতেন কিছু কিনে খাবার জন্য। পয়সার লোভে বাচ্চাগুলোও সময়ে অসময়ে দারুণ উৎপাত করতো মেজজেঠুকে। মায়ের মুখে শুনেছি বড়জেঠুর মৃত্যুর পর এক তীব্র একাকিত্ব গ্রাস করেছিলো মেজজেঠুকে। আমি সেসময়ে চাকরী সূত্রে কলকাতার বাইরে চলে যাই। এসব কথা কিছু কিছু মায়ের মুখে শুনতাম।
বাড়ীর মানুষগুলোর মতোই একদিন বাড়ীটার ঔজ্জ্বল্যও চলে গেলো। একদিন যে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাবা আমাদের কান্না থামাতেন, পরে সেই বাড়ীর জীর্ণদশা দেখে আমাদেরই কান্না পেতো! মিতভাষী মেজজঠু একদম নিজেকে ঘরবন্দী করে ফেললেন- একেবারেই বেরোতেন না। এমনকি আমরা গিয়ে ডাকলেও দরজা খুলতেন না। যদিও বা খুলতেন দেখেছি মুখভর্তি না কামানো কতো দিনের বাসী খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা তেলচিটে ধুতি বা লুঙ্গি, বগল ছেঁড়া গেঞ্জি পরণে। মাথায় কাকাতুয়ার ঝুঁটির মতো বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল। একসময়ের ফিটফাট সুপুরুষ মানুষটির দুর্দশা আমাদের ভিতর থেকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিতো।
বেশীরভাগ সময়ে হয় চুপচাপ বসে থাকতেন, নয়তো একা একাই বকবক করতেন। কি যে বলতেন কেউ জানেনা। আসলে ওঁরা তো পাড়ার কারো সাথেই তেমন মিশতেন না। চাঁদা দেওয়া ছাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগই ছিলো না। এই রকম মানসিক অবস্থায় একদিন ওনার বোন পুষ্প পিসীমা ও তার ছেলে এলেন জেঠুকে দেখভালের জন্য। দুয়েকদিন থাকার পরেই ওঁরা জেঠুকে নিয়ে চলে গেলেন নিজেদের বাড়ীতে। আমরা খুব কাছের ছিলাম বলে, পুষ্প পিসীমা আমার মাকে বলে গেলেন, “মেজদার চিকিৎসা আর যত্নের দরকার। আর এখানে থেকে সেটা সম্ভব নয়,তাই বাড়ীতে তালাবন্ধ করে নিজেদের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। সুস্থ হয়ে গেলে আবার চলে আসবে।”
এই ঘটনার দিন পনেরোর মধ্যেই দেখলাম খোলামেলা বাড়ীটার চারদিকে মিস্ত্রীরা গ্রিল দিয়ে ঘিরে বাড়ীটাকে একটা জেলখানার আদলে বদলে দিলো। লোকমুখে জানলাম বাড়ীটা আরিফদারা কিনেছে।
আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝলমলে সোনালী শৈশব, গরাদ বন্দী স্মৃতি হয়ে গেলো। আমরা বাড়ীটার দিকে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম।
পরে লোকমুখে জেনেছিলাম, বোনের বাড়ী যাবার অল্পদিনের মধ্যেই মেজজেঠু মারা যান।
আজো কখনো আরিফদাদের বাড়ী গেলে, বাড়ীটার আনাচে কানাচে, ওপরে ওঠার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ি, শৈশবের ছবিগুলো হাতড়াই। কান পাতলেই শুনতে পাই, দিদু, বড়জেঠু,মেজ জেঠু ডাকছেন, “টুটুল….! ও টুটুল….! একা একা ওপরে যেও না মা! সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যাবে……..!”
আমি ওদের বলতে ইচ্ছে করে, “না গো! ভয় পেয়ো না তোমরা! আমি এখন পড়ে গেলেও আর কাঁদি না। উঠে দাঁড়াতে শিখে গেছি যে……”