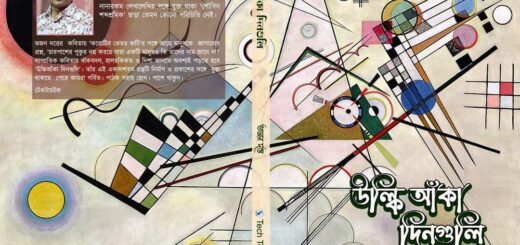রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প – ৪
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)
মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিভাবে ভেবেছেন, তা জানতে তাঁর নিজের কলমের দিকে একটু লক্ষ্য করতে চাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মায়ের ছোটছেলে, চতুর্দশতম সন্তান। তাঁর জন্মের সময় তাঁর মায়ের বয়স ছিল চৌত্রিশ। তাঁর ভাই বুধেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ছোটছেলে হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর মা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সারদাসুন্দরী দেবী ১৮৭৫ সালের ১১ মার্চ তারিখে ঊনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রয়াত হন। রবির বয়স তখন তের বছর দশমাস। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথের কলমে পাই:

মা’ র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। অনেক দিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এত দিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়— তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ‘ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে।’ তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা’র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না— সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম— তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ— শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম— তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত— আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই— তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়— কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।
জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারি দিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল— এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!” (‘জীবনস্মৃতি’ থেকে গৃহীত)

মৃত্যু প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা আলোচনা সূত্রে কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর কথা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। ভাষাতত্ত্ববিদ ও রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনুর সন্ধানী অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছিলেন, শমীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মকে এক অভিনব ভক্তিরসের দিকে চালিত করেছিল। এই চলা ১৩১৭ বঙ্গাব্দে গীতাঞ্জলির রূপ নিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়েছিল ১৮৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর, শনিবার সন্ধ্যা ছয়টায়। শমীন্দ্রনাথ ছোট থেকেই শারীরিক ভাবে রুগ্ন ও দুর্বল ছিলেন। তাঁর যখন ছয় বছর বয়স, তখন মৃণালিনী দেবী মারা যান। মৃণালিনী ঊনত্রিশ বছর বয়সে পাঁচটি সন্তানকে রেখে প্রয়াত হন। মাতৃস্নেহবঞ্চিত শমী মানুষ হতে থাকেন মায়ের পিসির কাছে।
বাবার লেখা গান খুব ভালবাসতেন শিশু শমী। ১৯০৭ সালে এপ্রিল মাসে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ” শমী ঠাকুর সেদিন লাইব্রেরির বই গোছাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে জ্বরে পড়েছে। জ্বরে পড়ে খুব গান ও কাব্য আলোচনা করছে। আজকাল হঠাৎ গানের উৎসাহ খুব বেড়ে উঠেছে। প্রায়ই “একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ” গেয়ে বেড়াচ্ছে।

ওই ১৯০৭ সালেই পুজোর ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে খবর আসে তাঁর ছোট মেয়ে মীরা ভীষণ অসুস্থ। সে খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্রুত শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মাতৃহারা বালকপুত্র শমীকে কোথায়, কার কাছে রেখে যাবেন, সেই নিয়ে যথেষ্ট দুর্ভাবনা ছিল তাঁর। কেননা, শমী কলকাতার পরিবেশ পছন্দ করতেন না। এদিকে ওই সময় পুজোর ছুটি উপলক্ষে আশ্রমের সকলেই বাড়ি চলে গিয়েছিল। নিরুপায় রবীন্দ্রনাথ ছোট ছেলেটিকে তার বন্ধু ভোলার সঙ্গে মুঙ্গেরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। ১৬ অক্টোবর তারিখে বিজয়া দশমীর দিন বন্ধু ভোলার সঙ্গে বালক শমী মুঙ্গেরে যাত্রা করেন। মুঙ্গেরে যাবার একমাসের মধ্যেই খবর আসে শমী কলেরায় আক্রান্ত হয়েছেন। খবর পাওয়া মাত্র ১৭ নভেম্বর তারিখে একজন চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুত্রের উদ্দেশে মুঙ্গের রওনা হন। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯০৭ সালের ২৪ নভেম্বর, বাংলা ১৩১৪ সালের ৭ অগ্রহায়ণ, মাত্র এগারো বছর নয় মাস বয়সে শমীন্দ্রনাথ প্রাণ হারিয়েছিলেন।
পুত্রকে দাহ করে রাতে রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে চেপে ফিরছেন, দেখলেন জোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। তাঁর মন বললে, কম পড়েনি – সমস্তের মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে। সমস্তের জন্য আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে। কোন খানে কোন সূত্র ছিন্ন হয়ে না যায় – যা ঘটেছে যেন সহজে স্বীকার করি। যা কিছু রয়ে গেল তা কেউ যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।
সেই রাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-
“অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো,
অন্তরতর হে।
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।”
অনেক পরে কনিষ্ঠা কন্যা মীরার পুত্র নীতীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু হলে, শমীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি কন্যাকে লিখেছিলেন:
“যে রাত্রে শমী গিয়েছিল, সে রাত্রে সমস্ত মন দিয়ে বলেছিলুম, বিরাট বিশ্বসত্তার মধ্যে তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও পিছনে যেন না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা শুনলুম, তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি, সেখানে তার কল্যাণ হোক্। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয় – নইলে ভালোবাসা এখনও টিঁকে থাকে কেন?”
শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আবহে ওই যে গীতাঞ্জলি সৃষ্টি ধারা নিঃসরিত হল, সেখানেও যত্নশীল পাঠক এক রহস্যময়ীর অস্তিত্ব লক্ষ করতে পারবেন। মৃত্যুকে স্বীকার ও সম্মান করেও তার ঊর্ধ্বে যাবার একটা চেষ্টা লক্ষ করতে পারবেন। রয়েছে বীণা, তরণী আর অন্ধকারের চিত্রকল্প। গীতাঞ্জলির যে কয়টি কবিতা সঞ্চয়িতায় সংকলিত হয়েছে, তার গুটিকয়েক উদ্ধৃত করব।
‘আত্মত্রাণ’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে –“
‘বেলাশেষে’ কবিতায় লিখেছেন “জানি নে আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা–
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।”
‘অরূপরতন’ কবিতায় লিখছেন
“..যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।…”
‘স্বপ্নে’ শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন – “স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে,
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধূলায়-লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।।”
‘সহযাত্রী’ কবিতায় লেখেন –
“কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
….কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।।”
‘বর্ষার রূপ’ কবিতায় লক্ষ করি
” …. কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।।
…নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে।।
…স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে…।”
‘সীমায় প্রকাশ’ কবিতায় লেখেন-
“তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে–
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।…
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর–।”
‘যাবার দিন’ কবিতায় লেখেন —
“বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,…”
‘শেষ নমস্কার’ কবিতায় লেখেন —
“হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবস-রাত্রি …
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে।।”
ক্রমশঃ