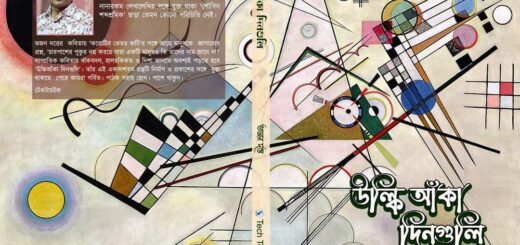আর্কাইভ থেকে তুষ্টি ভট্টাচার্য
ছায়াবাদী কবি মহাদেবী বর্মা
১৯০৭ সালের ২৬শে মার্চ, ফারুকাবাদে মহাদেবী বর্মার জন্ম হয়। উকিল পরিবারের চার ভাইবোনের মধ্যে তিনিই ছিলেন বড়, মাত্র ন’বছর বয়সে ১৯১৬ সালে ডঃ স্বরূপ নারায়ণ বর্মার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। যদিও পড়াশুনোর জন্য তিনি বিয়ের পরেও বাপের বাড়িতেই থেকেছেন। কনভেন্ট স্কুলে তিনি পড়তে চাননি, এলাহাবাদের ক্রসওয়েট গার্লস স্কুলে তিনি ভর্তি হন। এই স্কুলটিতে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাষার ছাত্রীরা পড়তে আসতেন, হস্টেলে থাকতেন, এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁকে আরও উদার ও মুক্তমনা করে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই স্কুলেই সুভদ্রা কুমারী চৌহানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়, যিনি নিজেও একজন বিখ্যাত হিন্দী লেখক ও কবি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। যে সময়ে অন্যরা খেলায় ব্যস্ত থাকত, মহাদেবী আর সুভদ্রা তখন গাছের নীচে বসে তাঁদের লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন, ইনি এক লাইন লিখতেন তো উনি দু লাইন। সুভদ্রা খারিবোলি-তে লিখতেন প্রথম থেকেই, মহাদেবীও খারিবোলিতে লিখতে থাকলেন বন্ধুর প্রভাবে। লিখতে লিখতে সারাদিনে একটি দুটি কবিতা লেখা রপ্ত করে ফেলেন। এভাবেই এক সময়ে তাঁরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা পাঠাতে শুরু করেন, কিছু প্রকাশিতও হতে থাকে। বিভিন্ন কবিসম্মেলনে ধীরে ধীরে ডাক পেতে থাকেন, বিখ্যাত হিন্দী কবিদের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়, তাঁরা ওঁদের থেকে পাওয়া উপদেশগুলো সযত্নে লালন করতে থাকেন। মহাদেবী ও সুভদ্রার এই যুগলবন্দী ক্রসওয়েট স্কুল পেরিয়ে সেই গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত টিঁকে ছিল। এই সময়ে তাঁর স্বামী লখনৌ-তে পড়াশুনো করতেন। এরপর এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯২৯-এ বিএ পাশ করেন, ১৯৩৩-এ সংস্কৃত নিয়ে তাঁর মাস্টার্স ডিগ্রি শেষ করেন।
মহাদেবী তাঁর বাল্যজীবনী ‘মেরে বচপন কে দিন’-এ বলেছেন, যে সময়ে একজন মেয়ে সন্তান পরিবারের কাছে বোঝা বলে গণ্য হত, সেই সময়ে তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবতী বলেই এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তাঁর দাদু তাঁকে স্কলার রূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তাঁর মা নিজেও হিন্দী আর সংস্কৃতে তুখোড় ছিলেন, তাঁকে লিখতে উৎসাহিত করার পেছনে মায়ের ভূমিকা ছিল সব থেকে বেশি। অথচ ধার্মিক এই পরিবারটিই আবার প্রথা অনুযায়ী গৌরীদান করেছিলেন!
গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে তাঁর স্বামী ডঃ স্বরূপ নারায়ণ বর্মা, তিনি যথেষ্ট সুন্দরী নন, এই অজুহাতে তাঁর সঙ্গে সংসার করতে অস্বীকার করেন। আর এই সময়ে মহাদেবী তাঁর স্বামীকে আবার বিয়ে করার জন্য বোঝাতে থাকেন, যদিও তা সম্ভব হয়নি। এম এ পড়ার সময়ে কীভাবে যেন রটে যায়, তিনি নাকি বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হয়ে গেছেন! অথচ সেই সময়ে তাঁর সিলেবাস অনুযায়ী তিনি পালি আর প্রাকৃত চর্চা করেছিলেন মাত্র।
১৯৩০ সালে এলাহাবাদের এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষক হিসেবে তিনি যোগ দেন। সেই সময়ে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও, গান্ধীবাদী আদর্শে মনেপ্রাণে উজ্জীবিত হয়ে পড়েন। ইংরেজি ভাষা সহ, বিদেশী জিনিস ব্যবহার করা বন্ধ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে খাদি পরতে শুরু করেন। ১৯৩৩-এ প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠ নামে এক প্রাইভেট কলেজের সূচনা হয়, সেখানে তিনি অধ্যক্ষ হয়ে যোগ দেন। এই কলেজের উদ্দেশ্য ছিল, পড়াশুনোর পাশাপাশি মেয়েদের নিজস্ব সংস্কৃতি, সাহিত্য নিয়ে অন্যরূপে শিক্ষিত করে তোলা। এই কলেজে, সেই সময়ে তিনি বিভিন্ন কবি সম্মেলন, গল্প পাঠের অনুষ্ঠানও করেছিলেন। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের লেখাও চলছিল তাঁর সমান ভাবে। ‘চাঁদ’ নামের এক হিন্দী পত্রিকা করতেন তিনি। এই পত্রিকায় মেয়েদের লেখাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হত। পত্রিকার সম্পাদকের ভূমিকা ছাড়াও ইলাস্ট্রেশনের কাজটিও তিনি করতেন নিজের হাতে। তাঁর এই সম্পাদকীয় গুলো নিয়ে পরে, ১৯৪২-এ ‘শৃঙ্খলা কে কারিঁয়া’ নামের এক সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি পাকাপাকি ভাবে এলাহাবাদে চলে আসেন, আর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই থেকে যান।
মহাদেবী বর্মাকে হিন্দীতে চারজন ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে অন্যতম মানা হত, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী ‘নিরালা’, জয়শঙ্কর প্রসাদ ও সুমিত্রনন্দন পন্থের সঙ্গে তাঁর নাম আজও উচ্চারিত হয়। তিনি কবিতার সঙ্গে অনেক ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন, ‘যামা’ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কবিতার পাশাপাশি তিনি গদ্যও লিখেছেন অনেক। আর এঁকেছেন। তাঁর ‘দীপশিখা’, ‘যাত্রা’-য় নিজেই ইলাস্ট্রেট করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কাজগুলোর মধ্যে ‘অতীত কে চালচিত্র’ ও ‘স্মৃতি কে রেখায়েঁ’ উল্লেখযোগ্য। ‘নীহার’, ‘রশ্মি’, ‘নীরজা’ আর ‘সান্ধ্যগীত’-এর উল্লেখ যেমন করতেই হবে তেমনই ‘সাহিত্যকার কী আস্থা’ এক মূল্যবান গদ্য সঙ্কলন। সিবিএসসি বিদ্যালয় স্তরে তাঁর বিভিন্ন রচনা, গল্প পড়ানো হয়, যেমন ‘নীলকন্ঠ’, ‘গৌরা’, ‘গিল্লু’, মেরে বচপন কে দিন’, ‘মধুর মধুর দীপক জল’, ইত্যাদি।
এই প্রসঙ্গে তাঁর পোষ্যদের নিয়ে যে গল্পগুলো চালু আছে সেগুলোরও একটু ছোঁয়া নেওয়া যাক।
নীলকন্ঠ আর রাধা নামের দুটি ময়ূরের বাচ্চা কিনেছিলেন মহাদেবী বর্মা। যদিও অনেকেই সন্দেহ করেছিল, ওগুলো আদৌ ময়ূরের বাচ্চা নয়। নীলকন্ঠ বড় হবার পরে বাড়িতে কুব্জ নামের আরেকটি ময়ূরী এল, রাধার সতীন হয়ে উঠেছিল যে। আর এক সময়ে নীলকন্ঠের মৃত্যুর পর কুব্জকেও কাজলি নামের এক বেড়াল মেরে ফেলল। এরপর রাধা যতদিন বেঁচে ছিল, অশোক গাছের ওপর বসে নীলকন্ঠকে আকুল হয়ে ডেকে যেতে দেখা গেছে।
গরু পোষার অভিজ্ঞতা ছিল না ওঁর। তাঁর বোনের থেকে গৌরকে উপহার পেয়ে খুব অসুবিধেয় পড়েছিলেন। সাময়িক ভাবে এক গোয়ালাকে গৌরের দেখভালের জন্য, দুধ দোয়ার জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু সে ব্যাটা নিজের গরুর দুধের বিক্রী কমে যাচ্ছে এই হিংসেয় গৌরকে খাবারের সঙ্গে পেরেক মিশিয়ে দিয়েছিল। ক্রমশ গৌর অসুস্থ হয়ে পড়ল, তার লালমণিকেও সে দুধ খাওয়াতে পারত না। আর অবোধ বাছুর লালমণি সারাদিন মায়ের পাশে খেলে বেড়াত, আদর চাইত, এমনকি একদিন কখন মা চলে গেল, টেরও পেল না।
সোনা নামের ওঁর একটা হরিণ ছিল। মালকিন বাড়ি না থাকলে সে অস্থির হয়ে পড়ত। প্রতি বছর মহাদেবী বদ্রীনাথ ভ্রমণে যেতেন, পোষ্যরা বাড়িতে থাকত চাকরদের কাছে। সোনা কিন্তু একবার মালকিনকে খুঁজতে জঙ্গলে পালিয়ে চলে গেছিল। তাই কেউ ওকে গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। সে এমনই অস্থির ছিল যে দড়ি টানাটানি করতে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে মরেই গেল সবার অলক্ষ্যে। মহাদেবী বাড়ি এসে প্রিয় সোনাকে আর দেখতে পেলেন না।
দুর্মুখ নামের এক খরগোশও ছিল ওঁর। নামের মতই সে ছিল অত্যন্ত আক্রমণাত্মক। একে, ওকে কামড়ে দিত প্রায়ই। হিমানীকে ওর সঙ্গী হিসেবে আনার পরেও সে শুধরোল না। এমনকি ওদের তিনটে বাচ্চাকেই খেয়ে নিল। বাড়িতে একটা সাপ ঢুকে গেলে, একবার দুর্মুখ সাপকে তাড়া করে, আর সেই সাপের সঙ্গে কামড়াকামড়িতেই মরে যায়। নীলকন্ঠ পর্যন্ত এই দুর্মুখকে সামলে চলত, সাপ আক্রমণ করা তার দ্বারা যে হবেই না, সহজেই অনুমেয়।
আর একবার বাগান থেকে এক আহত কাঠবেড়ালি, গিল্লুকে তিনি সেবা করে সুস্থ করে তোলেন। ওঁর সঙ্গেই সে এক বিছানায় ঘুমত, এমনকি, ওঁর থালা থেকে খাবার অধিকার ছিল একমাত্র গিল্লুরই। একবার গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মহাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময়ে গিল্লু তার ভাগের কাজুবাদাম খাওয়া ত্যাগ করেছিল মনের দুঃখে। বাড়ি ফিরে সেই কাজুবাদাম জড়ো হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন উনি।
আর ছিল এক হিমালয়ান শিপ ডগ, নীলু। তার আবার আভিজাত্য ছিল প্রবল। কেউ খাবার ছুঁড়ে দিলে সে খেত না। মহাবীর বারান্দায় সে থাকত, আর অতিথি এলে প্রথম ওঁকেই খবর দিয়ে দিত। মহাদেবী একবার বলেছিলেন, নীলুর মত অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণী উনি আর দেখেননি।
মহাদেবীর কাজের যা সবথেকে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ঠ, তা হল, তার নিজস্ব কন্ঠ আর খাঁটি কারিগরি দক্ষতা। এর মিশ্রণে আমরা পাই এক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক ছোট ছোট লিরিক, যা তাঁর পাঁচ খন্ডের কবিতাগুলোয় ছড়িয়ে রয়েছে। বস্তুবাদের সঙ্গে তিনি প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বিশালতা আর শূন্যতাকে মিশিয়ে গেছেন এক দক্ষ শিল্পীর তুলি দিয়ে।
বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা তিনি ভীষণ ভাবেই প্রভাবিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন নন্দনতত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর কবিতায় অবিরাম দুঃখ, প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ, বিরহ, এই রসের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও এই প্রেম বা বিরহ, বিচ্ছেদ, দুঃখ সবই ছিল এক দূরাগত শক্তির সঙ্গে বা বলা ভাল ঈশ্বরের সঙ্গে। আর এগুলোই ছিল তাঁর ছায়াবাদী কবিতার বস্তু বা বিষয়। ঠিক এই কারণেই তাঁকে মীরাবাঈ বলা হত।
‘দীপশিখা’ গ্রন্থের ৫১টি কবিতার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল এই দূরে থাকা প্রেমিকের সঙ্গে কথোপকথন, যেখানে সেই প্রেমিক বরাবরই চুপ করে থেকে গেছে, নিঃশব্দে রয়ে গেছে। এই গ্রন্থেই তিনি হিন্দী সাহিত্যের আর এক ধারা ‘রহস্যবাদ’-এর সূচনা করেন।
তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল-
১।নীহার (১৯৩০)
২।রেশমী (১৯৩২)
৩।নীরজা (১৯৩৪)
৪।সান্ধ্যগীত(১৯৩৬)
৫।দীপশিখা(১৯৩৯)
৬।অগ্নিরেখা(১৯৯০,এটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়)
‘নীরজা’ কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৩৪-এ পান ‘সেক্ষরীয় পুরস্কার’, ‘যামা’ কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান। ১৯৫৬-এ পদ্মভূষণ সম্মান লাভ করেন। আর তিনিই ছিলেন সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রথম মহিলা সদস্য (১৯৭৯)। এছাড়াও পদ্মবিভূষণ পান ১৯৮৮ সালে। ১৯৮৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি ধরাধাম ত্যগ করেন।
আগেই বলেছি, ছায়াবাদী কবিদের মধ্যে মহাদেবী বর্মা ছিলেন অন্যতম। ছায়াবাদ এমন এক সময়ের (১৯১৪-১৯৩৮) কথা, যখন হিন্দী কবিতার চূড়ান্ত রোমান্টিক যুগ চলছে। যখন প্রেম, প্রকৃতি আর আত্মলব্ধ রচনা সেই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে। মহাদেবীর লেখায় সেভাবেই অব্যক্ত প্রেম আর বিষাদ মিলেমিশে থেকেছে। আর যেহেতু তিনি নারী, এক নারীর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই লেখাগুলি এসেছে। বিভিন্ন বয়সে সেই নারী কখনও মেয়ে, কখনও প্রেমিকা, কখনও মা হয়ে তার দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভূমিকাগুলিকে আত্মস্থ করে প্রদীপের মত অনির্বান শিখায় জ্বলতে থেকেছেন। লেখাতেও তার সুস্পষ্ট ছাপ থেকে গেছে। আমরা বরং নামবর সিংহ-র লেখা ‘ছায়াবাদ’ বইতে লেখক মহাদেবী বর্মার লেখনী বিষয়ে কী বলেছেন, বাংলা অনুবাদে একবার দেখে নিই।
নামবর লিখছেন, “একজন নারীর মতই মহাদেবী বর্মা ঘরের গন্ডীতেই বাস করতেন। কিন্তু ওঁর কিছু কিছু লেখায় যে ভাবুক অংশ ও তীব্র ব্যথার প্রকাশ পাওয়া যায়, সেগুলো শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন ভাবের সন্তষ্টির দিকে চলে যায়। প্রথমে যেখানে অতৃপ্তি ছিল, পরে সেই অতৃপ্তিই কাল্পনিক তৃপ্তির আনন্দ এনে দিয়েছে। এরপরেও ওঁর লেখায় নিজস্ব শীক্ষণশৈলীর ছাপ থেকে গেছে। ওপরে ওপরে আনন্দ আর শান্তির হাল্কা হাসি নিয়ে ভেতরে ভেতরে সেই মনই চুপচাপ এই কথাই বলতে চেয়েছে-
’মধুর মধুর মেরে দীপক জল’,
তাঁর এই জ্বলে ওঠায় আনন্দ, তিনি বুঝে গেছিলেন, জীবনের চলার পথে এই একটাই গতি। এই কারণেই তাঁর অন্তর্দহনে বাইরের কোন রকম হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করেন নি। জীবন যেদিকে ইচ্ছে গড়িয়ে যায় যাক, কেউ বারণ করবে কেন? কেউ দয়া দেখাবে কেন? যা হবার তা হোক।
’ইয়ে মন্দির কা দীপ, ইসে নীরব জলনে দো।’
অব ‘সাঁসো কী সমাধি-সা জীবন’ হো গয়া। কোই রাস্তা নহী সুঝতা।‘ মসি সাগর-সা পথ বন গয়া।‘
যে প্রদীপ কঠিন পাথরের তৈরি মন্দিরের ভেতরে জ্বলে, তার জীবন যদি নিঃশ্বাসের ভেতর সমাধিস্থ না হয়, তাহলে কী হবে? যদি ওর প্রতিধ্বনির ইতিহাস পাথরের দেওয়ালে হারিয়ে না যায়, তাহলে কী হত? নিঃসন্দেহে সে ওই নিষ্করুণ মন্দিরে তার মধুর গান গাইত, কিন্তু তবুও ওই দেবতার ওপর তার কোন প্রভাব পড়ত না। এই সব প্রশ্নের উত্তর একটাই ‘বিহঁসা উপল, তিমির থা খেলা।‘
ওই প্রদীপ দেখল তার চোখের সামনে না জানে কত ভক্ত এল আর নিজের নিজের প্রশ্নগুলোর মাথায় চন্দন মাখিয়ে এখানে রেখে দিয়ে চলে গেল। বরলাভের আশায় ‘ঝরে সুমন বিখরে অক্ষত সিত।‘ আর আশার বিফলতা দেখে তাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে এই ভাবেই ‘তম মে সব হোংগে অন্তর্হিত্।‘
যে এত ভক্তর বিফলতার সাক্ষী রয়ে গেল, সেই প্রদীপের মনের নিজের ব্যথার থেকে ভক্তদের কষ্টর ব্যথা যে অনেক বেশি এই অনুভব হল সহজেই। আর এরপরেও সকাল হওয়া পর্যন্ত তার ভেতরে জ্বলতে থাকার আত্মসংকল্প রয়ে গেল। তার নিজের জ্বলতে থাকা জীবনের সবথেকে সার্থকতা এটাই –
‘জব তক জাগে দিন কী হলচল
তব তক ইয়ে জাগেগা প্রতিপল।‘
যখন দিন জেগে উঠবে হৈহৈ করে , তখন এত আত্মার সমাধি শরীরে বহন করা এই মন্দিরের কী গতি হবে? কিন্তু এরই মধ্যে এই মন্দিরের আঙিনায় যে শূন্যতা রয়েছে, তাকেই গলানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনিতেই এই মোমের তৈরি বাতিকে গলতেই হবে, আর এই গলে যাওয়া সার্থক করে তুলতে নিজের সঙ্গে সঙ্গে ওই শূন্যতাকেও গলিয়ে ফেলতে চায়। এছাড়া ও আর কী করবে! এত পুরনো মন্দিরে পাথরের ওই একলা দীপটি গলতে পারবে না। এই কারণে নিরুপায় হয়ে সে ওই শূন্যতাকেই গলাতে চাইছে। এক জন্মের শেষ হওয়ার পর আর এক জন্মের আসার মধ্যে যে অবকাশ পড়ে থাকে, সেই সময়কে সে নিজের ক্ষীণ আলোয় পূর্ণ করতে চায়।
‘ইসে অজির কা শূন্য গলানে কো গলনে দো।‘
এই সেই উদাত্ত কন্ঠ যা মহাদেবীর গীতগুলিতে এত গভীর যন্ত্রণা উৎপন্ন করে।এই কারণে মহাদেবীর শেষ গীতটি যথার্থই এক গভীর আত্মদান। প্রসাদ বা পণ্যের মত আদর্শ বা ব্যবহারিক জীবনে তাঁর পালিয়ে যাওয়া আর হয় নি। ভারতীয় নারী পালিয়ে কোথায়ই বা যাবে! তবুও কিছু গীতে যে তীব্র অতৃপ্তির ফলে পাওয়া হতাশা আর সতেজ অনুভব পাওয়া যায়, শেষ গীতের মন্থর অবসাদে তা অনুপস্থিত। পদাবলী আর বাক্য রচনায় হতাশা ভারী হয়ে চেপে বসেছে। প্রথম দিকের গীতে যে ‘চোট হ্যায়, উও তো কভী কী গায়ব হো গয়ী।‘ “
মহাদেবী বর্মার কবিতা নিয়ে কিছু কথা না বললে, এই লেখা সম্পূর্ণ হবে না। আমি যেটুকু কবিতা পড়েছি ওঁর, তাতে নামবর সিং-এর সঙ্গে সহমত হয়েই বলি, দুঃখ, বেদনা, হতাশাকে তিনি অঙ্গে জড়িয়েছিলেন ভূষণের মত করে। যখন ইচ্ছে করেছেন পোশাক বদলেছেন। যেন দুঃখকে উপভোগ করে তার ভেতরের পথ দিয়ে গিয়ে পেয়ে গেছেন এক আনন্দের দিশা। এখানেই তাঁর সফলতা। সব কিছুর ওপরে স্থান পেয়েছে এক পজিটিভ অ্যাটিটিউড। নিজেকে ক্ষয় করেছেন, অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তবুও স্তিতধী তিনি, মাথা উঁচু করে চলেছেন, নুয়ে পড়েননি। তাঁর শিক্ষা, জীবনবোধ, কবিতার ওপর একাগ্র মনোভাব, তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। ছায়াবাদ বা মিস্টিসিজম অথবা নিও-রোমান্টিসিজম, যাই বলুন না কেন, একে এককথায় বলে বোঝানো, বা ভাষায় প্রকাশ করা খুবই শক্ত কাজ। আর তাঁর লেখার স্টাইল এতটাই পেলব, নরম, জটিলতাহীন যে মনের ভেতরে এর মর্মার্থ সহজেই প্রবেশ করে। আলাদা করে পাঠককে ছায়াবাদ সম্বন্ধে শিক্ষিত না হলেও চলে। এখানেই তাঁর সার্থকতা। তাঁর পান্ডিত্যের ভারি ছায়া কোথাও যেন কবিতাকে দুর্বোধ্য করে তোলেনি। অথব গূঢ়তার বিচারে তা রয়ে গেছে উচ্চ স্থানে। কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেছি এখানে, আলোচনাও করেছি আমার স্বল্প ক্ষমতায়। যদিও মহাদেবীর কবিতার ছন্দময়তা আর ভাববাদ বাংলায় তর্জমা করা সম্ভব কিনা আমি জানি না। অন্তত আমার অনুবাদে এই ছন্দময়তার অভাব হয়ত রয়েই গেল অনেকটা।
কে? (কউন?)
অশ্রুর মত কোমল
স্বপ্নের মত অজ্ঞাত,
অরুণার সিঁদুর চুরি করে
আমার প্রভাত যখন হাসত
চুপচাপ লাল রঙে লুকিয়ে তখন
কে নিয়ে এল এই সোনালী পেয়ালা?
এই উদয় ছুঁলে ছেঁড়ে তার
প্রাণের ভেতর মরে উন্মাদ,
মিঠে ব্যথা নিয়ে প্রিয় তৃষ্ণা
অসারে ঘুমোয় আর্তনাদ
চুমুকে সাথী হয়েছে সাকী
শূন্য হাতে কে ফিরে ফিরে যায়?
‘কে’ কবিতাটি ছায়াবাদী কবিতার এক প্রকৃত রূপ। সূর্য ওঠার ঠিক পরেই এক সকাল, যেখানে কিনা অশ্রু আর ভাঙা স্বপ্নের ছোঁয়া লেগে আছে, অথচ যা কিনা হৃদয় বিদারী নয়, দুঃখেরও নয় ততটা। সকালের লাল রঙ যাব যাব বলেও যায় নি এখনো, কিছুটা যেন লেগে আছে, মুখের সামনে এসে বসেছে তৃষ্ণার্তের পেয়ালা হয়ে। এই তৃষ্ণা মিষ্টি স্বাদের, যার কাছে এলে ব্যথা, যন্ত্রণা দূর হয়, দুঃখী আহত চিৎকার থামিয়ে স্থির হয়ে বসে। যে প্রাণ উন্মাদ হয়ে ছিল এতদিন, সেও চুপ হয়ে আসে ক্রমশ। এই সকাল এমনই এক অদ্ভুত, আশ্চর্য, যার কাছাকাছি গেলে তৃষ্ণা মেটে বটে, কিন্তু ছুঁতে গেলেই সুরতাল কেটে যাবে নিশ্চিত। এই সকাল এক সাকীর মত, পেয়ালা ভরে দিতে জানে, আকন্ঠ পান করাতে জানে, প্রতিটি চুমুকে চুমুকে রয়েছে যখন সে, শূন্য হাতে এখান থেকে কেউ ফিরে যাচ্ছে না। বাস্তবের খালি হাত আর প্রকৃত অনুভব যে এক নয় মহাদেবীর এই কবিতায় তা স্পষ্ট।
একাকিত্ব (সুনাপন)
কালো কাজলে মেলে
সন্ধ্যার চোখের রাগ
যখন তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে
শূন্যে গুনতে বসে আকাশ
ওর হারিয়ে যাওয়া ইচ্ছের
দম বন্ধ করা মূক কষ্টের!
ঢকঢক করে মাতালের মত
পান করে বেদনার পেয়ালা
প্রাণে নিঃশ্বাস চেপে রেখে
পরে নেয় মেঘমালা
ওর থেমে থেমে আসা কান্নায়
বিদ্যুতের হারাবার ভয় মেলায়!
ধীরে ধীরে শূন্য উঠোনে
রাত যখন গড়িয়ে নামে,
ঠাণ্ডা শ্বাস তোলে ভরিয়ে
মুক্তোর মত অশ্রুর পাতায়;
ওর শিহরিত কম্পনে
কিরণের তৃষ্ণার্ত চুম্বনে!
না জানি কোন অতীত জীবনের
খবর পৌঁছে দেয় মৃদু সমীরণ,
নিজের ডানা দিয়ে ছুঁয়ে দেয়
স্থিমিত ফুলের নয়ন;
ওর ফিকে হাসিতে
ফের অলস ঝরে পড়াতে!
চোখের নীরব শিক্ষায়
অশ্রুর দাগ মুছে যায়,
ঠোঁটের হেসে ওঠার পীড়ায়
ত্যাগী আঘাত ভুলে থাকায়;
কার কার মাঝে ঘনায় এই নির্মম!
আমার মনের একাকিত্বে!
সলটিচুড আর লোনলিনেস-এর মধ্যে পার্থক্য তো থাকেই। এই কবিতার নাম একাকিত্ব হলেও, একাকিত্ব এখানে উপভোগের, যাকে আমরা সলটিচুড বলতেই পারি। কবি এখানে একাকিত্বকে উপভোগ করেছেন। নিজের বিষাদ, যন্ত্রণাকে একাকী বহন করেছেন যেম্ন, তেমনই ওদের উপেক্ষা করে নতুন আলোর সন্ধান করেছেন। একাকিত্ব তাঁকে মেরে ফেলেনি, বরং একা একাই তিনি মুক্তির স্বাদ পেতে চেয়েছেন। যতই দুঃখ আসুক, ঝড় ঝাপ্টা আসুক, তিনি নিজের মনে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন।
অধিকার
ওই হাসিখুশি ফুল, যে
স্থিমিত হতে জানে না,
ওই তারার প্রদীপ, যে
নিভে যেতে জানে না,
ওই নীলিমার মেঘ, যার
ধুয়ে যেতে ইচ্ছে করে না,
ওই অনন্ত ঋতুরাজ, যে
ফেরার পথ দেখেনি,
ওই শূন্য নয়ন, যেখানে
অশ্রুর মুক্তো জমে না,
ওই প্রাণের দীপ, যেখানে
অসুখ ঘুমোয় না;
এমনতর মানুষ, যার
বেদনা নেই, নেই যার অবসাদ,
জ্বলতে জানে না, না জানে
মুছে যাওয়ার স্বাদ!
স্বর্গীয় এমন মানুষই কি
তোমার করুণার উপহার?
রেহাই হে দেব! আর
এ আমার মুছে যাওয়ার অধিকার!
অধিকার আসলে কোন অধিকার রক্ষার কবিতা নয়। বরং কবি এখানে তাঁর বিষাদ, দুঃখ, পীড়া, যন্ত্রণাকেই জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার করতে চেয়েছেন। আগুনে পুড়ে যেমন লোহা আরও শক্তপোক্ত হয়, তেমনই এই দুঃখ, যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেলেই একজন মানুষ, সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন। স্বর্গীয় সুখ, আয়েশের তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি দুঃখ আর যন্ত্রণায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠার অধিকারে বিশ্বাসী।