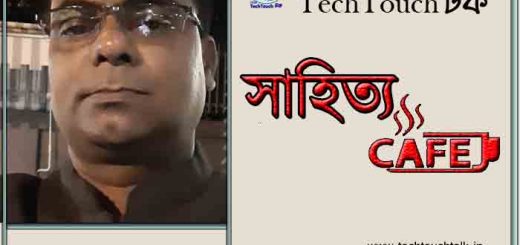ক্যাফে আলোচনায় তন্ময় কবিরাজ

চর্চায় পান্তাভাত
সময় পাল্টাচ্ছে। রাজনীতি বিনোদন থেকে বদল হচ্ছে মানুষের রসনার সুখও। একসময় বাঙালির বিলাসী জীবনে চাউমিন মোগলাই তেলেভাজার একচেটিয়া ঝোড়ো ব্যাটিং ছিল। সেদিন অবশ্য অতীত। ভেতো বাঙালির পরকীয়াতে এখন বিরিয়ানি। সৌজন্যে অবশ্য ইউটিউবারদের দাপট। শহরের দামি রেস্তোরাঁ থেকে পাড়ার মোড়ে লাল কাপড়ে মোড়া বিরিয়ানির হাঁড়িতেই মন মজেছে আট থেকে আশি – সবার। এমন জাদু বোধহয় শেক্সপিয়ারের ওথেলোও করতে পারেনি।বিরিয়ানিতে কতো গ্রামের মাংস আর রাইস আনলিমিটেড কিনা সেটাই চর্চার সাবজেক্ট। খানিকটা ট্রেলার দেখে সিনেমা দেখার মত। ট্রেলার ভালো হলে সিনেমা কনফার্ম। তবে হালফিলের প্রচণ্ড দাবদাহে সেই বিরিয়ানিকেই কিছুটা ব্যাকফুটে সরিয়ে দিয়েছে পান্তা ভাত। আধুনিক বাঙালি যেমন ঘরে পান্তা খাচ্ছে, তেমনই উইকএন্ডে বাইরে দামি হোটেলে পান্তা ভাত খেতে যাচ্ছে। ডাক্তারবাবুরাও পান্তা ভাতের সুপারিশ করছেন। অফিসবাবু তাই তার চেনা ডায়েটের পরিবর্তন এনে টিফিনে পান্তা নিয়ে যাচ্ছে। কারো আবার পান্তা ভাতে শৈশবের ইমোশন জড়িয়ে। তাই সেন্টু খেয়ে কেস খাচ্ছেন কাঁচা পিয়াঁজে। সুন্দরী সহকর্মী মুখে গন্ধ বলে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ আবার নস্টালজিক হয়ে মা, ঠাকুমার কথা ভাবতে বসে যাচ্ছেন। তবে সাবেক পান্তার সঙ্গে আধুনিক পান্তার পরিবেশনে এসেছে ফিউশন। সেকেলের পান্তাতে আগের রাতে ভাতে জল দিয়ে রাখা হতো ,পরের দিন তেল লঙ্কা, আলু সেদ্ধ, চপ বা পোস্ত বাটা বা মাছের টক দিয়েই স্বাদ গ্রহণ করা হতো, সঙ্গে কাঁচা পিঁয়াজ। তবে পান্তা ভাতেও আর্থিক বৈষম্যের ছবিটা প্রকট। ধনবানরা পোস্ত বা ডিমের বড়া আর গরীবের পাতে চপ বা আলু মাখাই একমাএ সম্বল।একসময়, চাষের ধান কাটার সময় হলে ভিন রাজ্যে থেকে যারা জন মজুরির কাজ করতে আসতো তাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য খাবার এই পান্তা ভাত। তবে আধুনিক পান্তা ভাতে অনেকটাই বদল এসেছে। ৮ – ১০ ঘণ্টা জল দিয়ে না রেখে সাময়িকভাবে বা দুপুরের ভাতে জল দিয়ে রাতে খাওয়া হয়। সঙ্গে সাবেক মেনু বা শাক, পাপড়, টক দই, লেবু, চুনো মাছ ভাজা। তবে প্রচন্ড গরমে মন প্রানকে চাঙ্গা রাখতে বাঙালির ভরসা পান্তা ভাত। সমাজে সবার কাছে তাই পান্তার ক্রমশ গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। এক প্রকার পান্তা ভাতই সর্বসাধারণের “রাহুল দ্রাবিড়”, সব খাবার ফেল করলেও এই দাবদাহে পান্তা ব্যাট করছে, তার রানে যেমন শান্তি, তেমনই পুষ্টিগুণ। ডাক্তারবাবুরা বলছেন, পান্তা ভাতে অক্সিজেনের মাত্রা বেড়ে, ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি পায়।তবে পান্তা ভাতের হরেক নাম। সংস্কৃত ভাষাতে একে বলা হয় কাঞ্জিকা, আসামে বলা হয় পৈতা ভাত,তামিলনাড়ুতে পাজাও সাদাম। উড়িষ্যাতেও পান্তার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পুরীর সমুদ্রের সুখের দোসর এখন এই পান্তা।তবে এই খাবারের জনপ্রিয়তা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও পাড়ি দিয়েছে। চিনেও পান্তার কদর রয়েছে। সেখানে পান্তার নাম জিউনিয়াং। ভারতের উত্তর পূর্ব ত্রিপুরা রাজ্যে এর ভালোই কদর রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পান্তা ভাত সকালের জল খাবার হিসাবে গ্রহণ করে। আসলে ডায়বেটিসে ভীত মানুষ একবার ভাত খাওয়াতে দুপুরের মেনুতে পান্তা ঢুকে পড়েছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গে পান্তার সঙ্গে শুটকি মাছ বেশ পছন্দ করে। পান্তা ভাতের তরল অংশ হলো আমানি আর পান্তার জলকে বলে কাঞ্জি। মানুষ অবশ্য এতো টেক্সট বুক মেনে পান্তা খেতে বসে না, মন চায় তো ওয়ান্স মোর। তবে এই পান্তা নিয়েও কম ঝামেলা হয়নি। পান্তা উৎসব হয়নি বলে পূর্ববঙ্গে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ হয়।রাজনৈতিক দিক থেকে পান্তা রসগোল্লার মত বিতর্ক তৈরি করতে না পারলেও পান্তার কিন্তু ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। সাহিত্যের পাতাতেও পান্তা নিজের জায়গা করে ফেলেছে। পান্তার জাদুতে কোনো বিভাজন নেই,রয়েছে সংহতি আর কাঁটাতার ভেঙ্গে মেলবন্ধন। গোলাম রব্বানী লেখায় জানা যে, মুঘল আমলেও পান্তার প্রচলন ছিল। পান্তা ধ্রুপদী, পান্তার হেরিটেজ রয়েছে। নৃ বিজ্ঞানী তপন কুমার স্যানাল তাঁর গবেষণায় বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার বিশেষ এক সম্প্রদায় সন্ধে বেলায় রান্না করতো আর পরের দিন সেটা খেতো। তবে পান্তাকে দরাজ সার্টিফিকেট দিয়েছেন ফ্রে সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক। তিনি বলছেন, ১৭শতকের সব মানুষই পান্তা খেত। আসলে মাঝখানের সময়টায় পান্তার ভাটা পড়েনি, সভ্য সমাজ পান্তাকে সেভাবে পরিচয় দিতে লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি, ডারউইনের অস্তিত্বের লড়াই সব কিছু নিয়ে জীবন যখন অস্থির,তখন পান্তা ভাত ছাড়া গতি নেই। তাছাড়া পান্তা ভাতে রয়েছে ধর্মীয় প্রসঙ্গও। চন্ডীমঙ্গলে পান্তা ভাতের উল্লেখ রয়েছে। বৈষ্ণবরা পান্তা ভাতকে ভোগ হিসাবে নিবেদন করেন। বিভিন্ন জায়গায় পয়লা বৈশাখে পালিত হয় পান্তা উৎসব। পান্তা ভাতের ব্যঞ্জনায় রাখা হয় দই, চিনি, কলমির শাক ও দু রকমের তরকারি। মানুষের আবেগ রয়েছে এই পান্তা ভাতে।পান্তা নিয়ে ছড়া তৈরি হচ্ছে। “বান্দির কামে যশ নাই
পান্তা ভাতে কাশ নাই।” তাই ঘরোয়া জীবনে পান্তা আজ অতিথি নয়, বরং স্থায়ী সদস্য।