T3 নববর্ষ সংখ্যায় সুজাতা দে
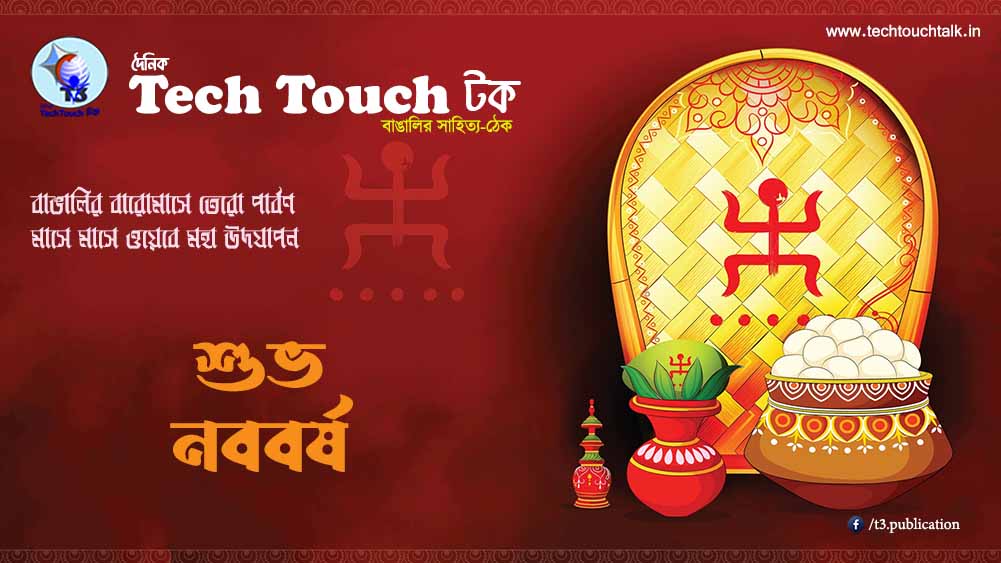
কলকাতার ট্রাম ট্রেন
জনপরিবহণের ক্ষেত্রে যানবাহন হিসাবে ১৮৭৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর রাজত্ব করেছে কলকাতার ট্রাম।
জনপরিবহনের ক্ষেত্রে গোটা এশিয়া তথা কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হওয়াটা সেই যুগে ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা।
যদিও এর অনেক আগেই ১৮০৭ সালে ব্রিটেনের ওয়েলস শহরে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হয়ে গিয়েছিল।ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা মাম্বলস রেলওয়ে আইন পাসের মাধ্যমে বিশ্ব প্রথম এই যাত্রীবাহী ট্রাম পরিষেবা চালু হয়।
সেযুগে সুতানুটি গোবিন্দপুরকে ঘিরে গঙ্গার গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ক্রমবর্ধমান হয়ে বেড়ে চলেছে কলকাতা। জনবসতির সাথে সাথে বাড়ছে গ্রামগঞ্জ থেকে
ট্রেনে করে কলকাতায় আসা বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষজনের ভিড়। ব্যবসায়ী,শ্রমিক, কর্মচারী,অফিসবাবুদের পাশাপাশি ধর্মের পীঠস্থান হিসাবেও কলকাতায় বাড়ছিল লোক সমাগম।
চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখিত কালিঘাটের সুপ্রাচীন সতীপীঠ মন্দিরটি ১৮০৯ সালে সুন্দরভাবে তৈরি করিয়ে দেন বড়িশার সাবর্ণ জমিদার শ্রী শিবদাস চৌধুরী। সেই মন্দিরের অলৌকিক মাহাত্ম্যের টানে দর্শনার্থী এবং ভক্তদের ভীড় বাড়তে থাকে কলকাতায়। আর একদিকে রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির ভক্তদের জনপ্রিয়তা পায় মন্দিরের পূজারী রামকৃষ্ণদেবকে ঘিরে।
পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক গ্রামীণ উপভাষায় ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা সাধারণ জনমানসে বিরাট প্রভাব আনে। প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বল্পশিক্ষিত হলেও রামকৃষ্ণ বাঙালি বিদ্বজ্জন সমাজ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্ভ্রম অর্জন করেন। ১৮৭০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নিকট রামকৃষ্ণ হয়ে ওঠেন হিন্দু পুনর্জাগরণের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তিনি সংগঠিত করেন একদল অনুগামী। তাঁর অনুগামীরা রামকৃষ্ণদেবকে ঐশ্বরিক অবতার বলে মনে করতেন।রামকৃষ্ণের বাণী শুনে মান সিক শান্তি পেতে ও তাঁকে শুধুমাত্র চাক্ষুষ দর্শন
করতে দূরের মানুষজন ছুটে আসতেন কলকাতায়।
সূদুর গ্রাম থেকে সুচিকিৎসার আশায় আসা অসুস্থ রোগীদেরও ভিড় এইসময় বাড়তে থাকে কলকাতায়।
ট্রেনে করে রোগীর দল কলকাতায় আসতে থাকে ১৮৭৩ এর ১লা ডিসেম্বর সদ্য স্থাপিত হওয়া শিয়ালদহ মেডিক্যাল কলেজে। কলকাতার দক্ষিণ অংশে ১৭০৭ এ শুধুমাত্র ইউরোপিয়ানদের চিকিৎসার জন্য তৈরি হওয়া প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল এর দরজাটিও নন-ইউরোপীয় মানুষদের চিকিৎসার্থে এসময় খুলে দেওয়া হয় ১৮৭০ সালের ২ রা এপ্রিল। সেখানেও রোগীরা আসতে শুরু করেন।
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ শীতলপ্রসাদ খড়গ হাওড়ায় ‘অভ্যুদয় কটন মিল’ স্থাপন করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলাল ক্ষেত্রী হাওড়ার ঘুসুরিতে ‘এমপ্রেস অফ ইণ্ডিয়া জুট প্রেস’ স্থাপন করেন। তারপর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব দামোদর চৌবে এসে কলকাতায় শেয়ার ও কোম্পানির কাগজ কেনাবেচার কাজ করতে শুরু করেন।
১৮৬২-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানি দিল্লী পর্যন্ত লাইন স্থাপন করেন। এর ফলে রাজস্থানের লোকদের কলকাতায় আসার পথ সুগম হয়। রাজস্থানী ব্যবসায়ীরা দলে দলে কলকাতার দিকে আসতে শুরু করে।মুসলমান ব্যবসায়ীরাও আসতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এম. এম. ইসপাহানি চা রপ্তানীর কারবার শুরু করেন। তাছাড়া আরও অনেক মুসলমান ব্যবসায়ী এসে ক্যানিং ষ্ট্রীট ও দিল্লীপটিতে আমদানীকৃত নানা রকম জিনিষের কারবার শুরু করেন।
দিনে দিনে নিত্যযাত্রীদের ভিড় বাড়ছিল কলকাতায়। এর জন্য প্রয়োজন হয়ে উঠছিল সুষ্ঠু সুলভ গণ পরিবহনের।
ধীরগতিতে চলা এবং অল্প সংখ্যক যাত্রী পরিষেবা প্রদান তথা ব্যাক্তিগত সম্পত্তির কারণে সাধারণ মানুষেরা কাছে পালকি, ছ্যাকড়া গাড়ি বা অভিজাত বিত্তবানদের আটফুকার, দশফুকার ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে পড়ছিল। সেইদিকে তুলনায় দ্রুতগামী ঘোড়ায় টানা গণ-যান পরিষেবার কথা শুবে মানুষ একটু বেশিই আগ্রহ দেখিয়েছিল।
সেই দিনটা ছিল ১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি।
ঘোষণা অনুযায়ী কলকাতায় প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলবে। ব্রিটেনের ওয়েলস প্রথম ১৮০৭ সালে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলেছিল। মানুষ সেই গল্প শুনেছে এতোদিন এবার কলকাতায় চলবে সেই ট্রাম।
তাই সেই বিশেষ ক্ষণের সাক্ষী হতে সকাল নটায় শিয়ালদহ স্টেশনে অতি উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষমান প্রচুর মানুষজন। তখন কল কাতায় পূর প্রশাসন ছিল জাস্টিস অফ পিসের হাতে। এই ট্রাম প্রকল্প চালু করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রামগঞ্জ থেকে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে আসা মালপত্র হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বা গুদামে সরবরাহ করা। প্রথম ট্রাম লাইন পাতা হয়েছিল ৩.৯ কিলোমিটার রাস্তায়। শিয়ালদহ বৈঠকখানা রোড থেকে বৌবাজার ডালহৌসি স্কোয়ার হয়ে কাস্টমস হাউজের ভিতর দিয়ে স্ট্যান্ড রোড হয়ে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। জনবসতির মধ্য দিয়ে এই লাইন পাতার একটাই উদ্দেশ্য যাতে ট্রাম পরিষেবা লোকসানের মুখে না পড়ে। হাওড়া তখন ইস্ট ইন্ডিয়া রেলের কলকাতা স্টেশন নামে পরিচিত ছিল। রাধারমণ মিত্রের “কলিকাতা দর্পণ” থেকে আম রা জানতে পারি অনেক তথ্য। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে আমরা জানতে পারি “সেদিন শেয়ালদা স্টেশন থেকে দুটি ট্রাম-ট্রেন ছাড়ে।”
ট্রাম চলবার পূর্বমুহুর্তে তদারকি করছিলেন ট্রামওয়ের সুপারিটেন্ডেন্ট মিস্টার সি এফ এবরোএবং ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ক্লার্ক।
প্রচুর যাত্রী ও দর্শক তখন ট্রাম দেখার জন্য অধীর আগ্রহে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিয়েছে। এসে গেছে দুটি ট্রাম। ছটি ঘোড়ায় টানা একটা ট্রেনের মতো তিন বগি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাম অন্যটা চার ঘোড়ায় টানা দুই বগি নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায়। প্রত্যেক বগিতে পঁয়তাল্লিশ জনের বসবার ব্যবস্থা।
প্রথম ট্রামে একটা প্রথম শ্রেণী,অন্য দুটো দ্বিতীয় শ্রেণী। দ্বিতীয় ট্রামে একটা প্রথম শ্রেণী এবং অন্যটা দ্বিতীয় শ্রেনী।
দ্বিতীয় শ্রেনীর ভাড়া কম তাই কে যে আগে উঠবে ওই যানে,সেই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি। সকলেই কম ভাড়ার দ্বিতীয় শ্রেনীতে উঠতে ঠেলাঠেলি শুরু করে দেয়। মালপত্র রইল পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেনীর বগির ছাদে দ রজায় উঠে ঝুলতে লেগেছে মানুষজন। প্রথম শ্রেনীতে জুটেছে মাত্র পাঁচজন।
তিনজন ইউরোপীয় এবং দুই জন ভারতীয়।
সকালপ সাড়ে নটায় সিগন্যাল দেওয়া মাত্র প্রথম কাম রার ঘোড়াদুটো টগবগিয়ে ছুটে গেলেও উপছানো ভিড় নিয়ে দ্বিতীয় কামরার ঘোড়াদুটোকে চাবুক মারলেও গাড়িটা টানতে পারে না।শেষে কোম্পানির কর্মচারীরা গাড়িটা পিছন থেকে ঠেলে ঠেলে অতি ধীরে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।
শুধুমাত্র মাল পরিবহনের কথা ভেবেই ভুল করেছিলেন ট্রামওয়ে ককর্তৃপক্ষ। কলকাতার অতিরিক্ত গরমে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে মৃত্যু হত। এছাড়া ক্লান্ত ঘোড়ার বদলি হিসাবে পথের মাঝে আস্তাবল বানিয়ে অন্য তাজা ঘোড়াকে গাড়িতে জুড়ে দিতে হতমাঝে মাঝেই।অষ্ট্রেলিয়ান
ঘোড়া এনেও অতিরিক্ত গরমে তাদের পরপর মৃত্যু হওয়া ঠেকানো গেল না। ট্রাম ককর্তৃপক্ষ এই খতে দেড় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেও সেই খরচ বেড়ে দাঁড়ায় আড়াই লক্ষে। ট্রামের জনপ্রিয়তা স্বত্তেও ঘোড়াগুলোর মৃত্যুতে লোকসানের মাত্রা বাড়তেই থাকলো। তাই ট্রাম রিষেবা বন্ধ হল ১৮৭৩ সালের ২০ নভেম্বর। ট্রাম পরিবহনের প্রথম উদ্যোগ ব্যার্থ হল।
ক্যালকাটা ট্রাম ওয়েজ কোম্পানি (CTC) নামে লন্ডনের এক সংস্থাটি এক হাজার ঘোড়া ও একশো সতেরোটি ট্রাম নিয়ে কলকাতায় ফের ট্রাম পরিষেবা চালু করে।
ট্রাম টানার জব্য ভবিষ্যতে ঘোড়াকে বাদ দিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হয়।
অবশেষে ১৯০২ সালে প্রথম ট্রাম পরিষেবা বৈদ্যুতিক রণ হয় যা ছিল এশিয়া মহাদেশের প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম পরিষেবা।
স্বাধীনতার পর ৯৫১ সালে পশ্চিম্বঙ্গ সরকার কলকাতা ট্রামওয়েজ কে অধিগ্রহণ করে নেয়। নাম হয়
WBTCL বা ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। কলকাতার সাতটি ঠাম ডিপো হল- বেল গাছিয়া,রাজাবাজার,পার্ক স্ট্রিট, গড়িয়াহাট,টালিগঞ্জ,কালীঘাট এবং খিদিরপুরে। এছাড়াও ট্রামের ৯ টি টার্মিনাল আছে- শ্যামবাজার, গ্যালিফ স্ট্রীট, বিধাননগর, বালিগঞ্জ,এসপ্ল্যানেড,,বিবাদীবাগ ও হাওড়া ব্রিজ। শিয়ালদহ নোনাপুকুরে কলকাতা ট্রামের ওয়ার্কশপ আছে। ট্রাম মূলত ৫৫০ ভোল্ট ডি সি পাওয়ার থেকে চলাচল করলেও ২০২৪ সামে পশ্চিম্বঙ্গ সরকার এই যানকে মন্থরগামী এবং পথে যানজট সৃষ্টিকারী যান হিসাবে বাতিল ঘোষণা করে। আধুনিক কলকাতার বুকে ট্রাম অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।
দীর্ঘ ১৫০ বছর কলকাতাকে যান পরিষেবা দিলেও এর উপকারিতা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।
ট্রামে যাত্রী ধারণের ক্ষমতা পেয়ায় তিনশো যেখানে বাস সর্বাধিক ষাট জন যাত্রী বহন করতে পারে। ট্রামের পরিষেবা
সুলভ ও খোলামেলা জানালা বিশিষ্ট তাই স্বাস্থ্যকর। ট্রাম নির্দিষ্ট ট্র্যাকে চলায় শৃঙ্খলা মেনে পথ চলে। তাই দুর্ঘটনার হার প্রায় নেই বললেই চলে।
যদিও দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটা রাস্তা পার হতে গিয়ে ১৯৫৪ সালের ১৪ অক্টোবর বিশিষ্ট কবি জীবনানন্দ দাশ ট্রামের ধাক্কায় আহত হন। ঠিক আট দিন পর ২২ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু ঘটে। অবশ্য এটা একটা ব্যাতিক্রমী এবং দু:খজনক দুর্ঘটনা।
সর্বরি কলকাতাকে দূষণবিহীন রাখতে এবং পরিবেশ বান্ধব হিসাবে ট্রামের মতো বিদুৎ চালিত যানের গ্রহণযোগ্যতাকে অস্বীকার করা একেবারেই অনুচিত। ১৮৭৫ সালে ট্রামের বৈদ্যুতিক সংস্করণ করেছিলেন যে রশিয়ান মানুষটি সেই উদ্ভাবক- ফিওদর পিরোটস্কি-র কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে থাকব।
************
তথ্যসূত্র
১)রজতকান্তি সুর
( গবেষক এবং কলকাতার ইতিহাস বিশেষজ্ঞ)
২) কলকাতার ট্রাম (দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত)
৩) শ্রীপান্থ, কলকাতা আনন্দ পাবলিসার্স)
৪)পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতা সংক্রান্ত( দেজ পাবলিসার্স)
৫) আর্ন্তজালের “ট্রাম” বিষয়ক বিভিন্ন সাইট।


















