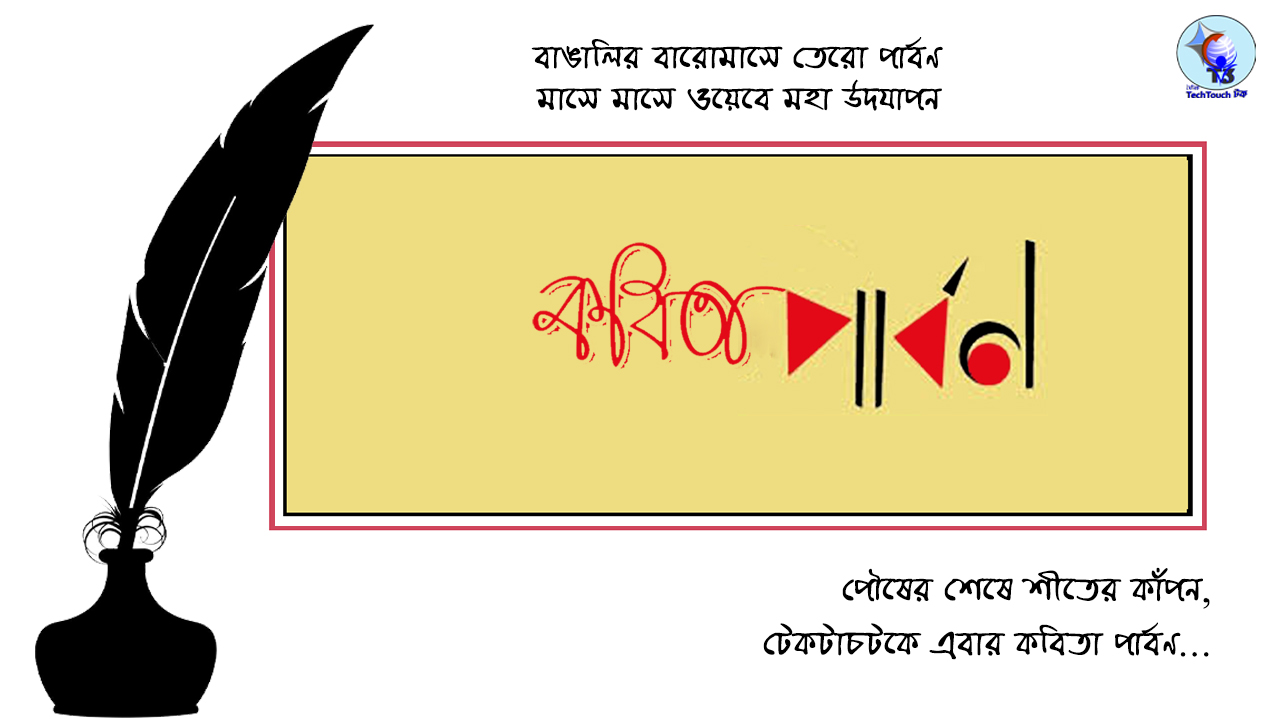T3 || আমার উমা || বিশেষ সংখ্যায় সমরজিৎ চক্রবর্তী

পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার
হাওড়াকে আমরা পূর্ব ভারত তথা কলকাতার প্রবেশদ্বার বলে অভিহিত করি। এই প্রবেশদ্বারের অন্যতম প্রধান ফটক হলো হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্রসেতু। জনসাধরণের জন্য এই ব্রিজ আড়ম্বরহীন ভাবে খুলে দেওয়া হয় ১৯৪৩ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে। ১৯৪২ সালে ডিসেম্বর মাসে জাপানীরা দিনের বেলাতেই কলকাতায় বোমা ফেলেছিল।
হাওড়া ব্রিজের আগে হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে সংযোগকারী হিসাবে আরও একটি ব্রিজ ছিল। ভাসমান সেতু। নাম পন্টুন বা পল্টুন ব্রিজ। লম্বায় ১৫৩০ ফুট (অর্দ্ধ মাইল) এবং চওড়ায় ৪৮ ফুট গাড়ি চলাচলের রাস্তা বাদ দিয়েও দু পাশে ছিল ৭ ফুট চওড়া ফুটপাত। কতকগুলো ভাসমান নৌকা (পন্টুন) পরস্পর জুড়ে নির্মাণ করা হয়েছিল এই ব্রিজ। জনতার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। এই ব্রিজের ওপর দিয়ে বাস, লরি, মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি চলাচল করত। মাঝখান থেকে ইচ্ছেমত দুটি নৌকা সরিয়ে নিলেই অনায়াসে জাহাজ কিংবা বড় বড় স্টিমার করতে পারত।
পন্টুন ব্রিজের ওপর চাপ কমানোর জন্য পাশেই নির্মিত হয় আজকের রবীন্দ্রসেতু বা হাওড়া ব্রিজ। সময় লেগেছিল আট বছর। নকশা করেছিলেন তিনজন মিলে। মেসার্স রেন্ডেল (Rendel), পামার (Palmer), এবং ট্রিটন (Tritton)। ইংলন্ডের মেসার্স ক্লিভল্যান্ড ব্রিজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড ছিলেন প্রধান কনট্রাক্টর। এই কোম্পানি আবার ফ্যাব্রিকেশনের স্টীল ওয়ার্কিংয়ের বরাত (সাব কনট্রাক্ট) দিয়েছিল তিন কোম্পানিকে (বি.বি.জে)। মেসার্স ব্রেইথওয়েট (ভদ্রেশ্বর), বার্ন (হাওড়া) এবং জেশপকে (টিটাগড়)। সংক্ষেপে এই তিন কোম্পানির ডাক নাম বি.বি.জে। ঝুলন্ত এই ব্রিজ তৈরী করতে মোট খরচ হয়েছিল তিন কোটি টাকা তেত্রিশ লক্ষ টাকা। ইস্পাত লেগেছিল ছাব্বিশ হাজার পাঁচশো টন। বিশেষ ধরণের কিছু পরিমাণ স্টীল ছাড়া সম্পূর্ণটাই যোগান দিয়েছিল টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী। অথচ এই টাটা কোম্পানি ১৮৮০ সালে মধ্যপ্রদেশে কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকার তথা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে পণ্য পরিবহনের জন্য রেলওয়ের সামান্য সুযোগ সুবিধা চেয়ে জামশেদজি টাটা অনুরোধ করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিশনার তা প্রত্যাখান করে দিয়েছিলেন। কারণ ১৮৫৪ সালে ১৫ আগষ্ট রেল চালু হওয়ার পর ইস্পাত শিল্পে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল তা দেখে ব্রিটিশরা ভেবেছিল তাঁরা এদেশে একচেটিয়া ব্যবসা করবে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে একচেটিয়া অধিকার খর্ব করতে ব্রিটিশদের সামনে দাঁড়াল বেলজিয়াম। আর এর ফলে বিশ শকের প্রথম দিকে লর্ড কার্জনের সময় সরকারি মনোভাব বদল হতে শুরু করল। এই সময় ভারতীয় উদ্যোগপতিদের লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনে কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল সরকার। ১৯০৭ সালে স্থাপিত হল ‘টাটা আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি। কারখানার নির্মাণ কাজ শুরু হল ১৯০৮ সালে। প্রথম লোহা তৈরী হল ১৯১১ সালে। ১৯১৩ সালে ভারতে আধুনিক কারখানায় তৈরী হল প্রথম ইস্পাত। ২৩ বছর পর সম্পূর্ণ ইস্পাত যোগান দিল হাওড়া ব্রিজকে, যা আজও আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।
এই ব্রিজের টাকার যোগান দেওয়া হয়েছিল বাজারে ঋণ পত্র ছেড়ে। শোধ করার জন্য চাপানো হয়েছিল ট্যাক্স। কলকাতা কর্পোরেশন অঞ্চলে বাড়ির করের ওপর ১/২ শতাংশ। হাওড়া, দক্ষিণ শহরতলী, টালিগঞ্জ ও গার্ডেনরিচ অঞ্চলে বাড়ি-করের ওপর ১/৪ শতাংশ। এ ছাড়াও ছিল ট্রেন, ট্রাম ও বাসের ওপর ট্যাক্স। এই ব্রিজের উপর প্রথম ট্রাম চলেছিল ১৯৪৩ সালে ১ ফ্রেব্রুয়ারি। কলকাতায় ট্রাম চালু হয়েছিল ১৮৮০ সালে ২৯ সেপ্টেম্বরে। ব্রিজের ওপর জ্যাম-জট নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ানোয় ১৯ শতকের শেষদিকে হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে ট্রাম চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।
বি.বি.জে অর্থাৎ ব্রেইথওয়েট, বার্ন আর জেশপ এই তিন কোম্পানির হয়ে আসল কোম্পানির সঙ্গে যিনি ফ্যাব্রিকেশনের কাজে কনসালটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি হলেন একজন বাঙালী। স্বনামখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার হাওড়া সালকিয়ার বাসিন্দা ললিতমোহন দাস। ২১৫০ ফুট দীর্ঘ বিশ্বের তৃতীয় এই ঝুলন্ত আজও আমাদের সামনে স্বমহিমায় বিরাজমান।
হাওড়া স্টেশন তৈরী হওয়ার যেমন ক্রম-বর্ধমান যাত্রী ও পণ্য চলাচলের ভার যেমন পন্টুন ব্রিজ বহন করতে পারছিল না, তেমনই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলকাতা-মুখী জীবনযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না হাওড়া ব্রিজ, ফলে মিটিং-মিছিল আর যানবাহনের ব্যাপকতায় জ্যাম-জট রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনযাত্রার এই দুর্বিসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১৯৭২ সালে ৩৬ কোটি টাকার নিয়ে এই ব্রিজের দক্ষিণে কাজ শুরু হয় দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজের। বিশ্বের দ্বিতীয় ‘কেবল স্টেইড’ এই সেতুর শিলান্যাস করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দশ বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও গঙ্গা দিয়ে বিস্তর জল বহে যায়। অবশেষে ভারতের আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি.ভি. নরসিমা রাও ২০ বছর পর এই সেতু জনগণের জন্য উৎসর্গ করলেন। ১৯৯২ সালে ১০ অক্টোবর। শেষ বিকেলের ধূসর আলোয়। পাইলন তথা স্তম্ভের মাথায় তখন জ্বলে উঠেছে অটোমেটিক আলো। আর মঞ্চ আলো করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামানুসারে সেতুটির নাম রাখা হয় বিদ্যাসাগর সেতু। দীপাবলী উৎসবের কয়েকদিন আগেই আলোকমালায় সজ্জিত সেতুর উদ্বোধন পর্ব রাজ্যের মানুষের মনে বয়ে এসেছিল অফুরন্ত আলোর বিচ্ছুরণ। স্বস্তির নিঃশ্বাস। বিশেষ করে যাঁরা কলকাতায় রোজ যাতায়াত করেন তাঁদের মনে।
বিশ্বখ্যাত এই সেতুটির নির্মাণ করতে মোট খরচ হয়েছে ৩৮৮ কোটি টাকা। নদীর দুই পাড়ে সেতুর ওপর দুটি করে মোট চারটি স্তম্ভ। প্রতিটির উচ্চতা ৪৩৫ ফুট। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথা থেকে ৮২৪ মিটার দৈর্ঘের ঊনিশটি করে তার (কেবল) সম্পূর্ণ সেতুটাকে টেনে ধরে রেখেছে অসম্ভব উচ্চতায়। সেতুটি স্থাপন করতে লেগেছে চল্লিশ (৪০) একর জমি। হাওড়া ব্রিজের মতন এই সেতুও সেই তিনি কোম্পানির ওপর নির্মাণের দায়িত্ব বর্তেছিল। বি.বি.জে অর্থাৎ ব্রেথওয়েট, বার্ণ এবং জেশপ কোম্পানির ওপর। মেন গার্ডার, মিডল গার্ডার এবং ক্রস গার্ডার ফেব্রিকেশনের দায়িত্বে ছিল ব্রেথওয়েট ও বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড। পাইলন এলিমেন্ট, পাইলন ইরেকশন ক্রেন ফেব্রিকেশন এবং পি.ই.সি সংস্থাপনের কাজে পরামর্শ পরিষেবা দায়িত্বে ছিল জেশপ। এই তিন কোম্পানির সঙ্গে সমন্বয় সাধনকারীর হিসেবে ছিল ‘ভারত ভারী উদ্যোগ নিগম লিমিটেড’ বা বি.বি.ইউ.এন.এল.। প্রতিটি স্তম্ভে ঊনিশটি করে যে তারের বা কেবলের টানা দেওয়া হয়েছে, সেই কেবল তৈরী হয়েছে রাঁচিতে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে। তৈরী করেছে ঊষা মার্টিন ইনডাস্ট্রিজ লিমিটেড। ইস্পাত লেগেছে মোট ১৩,৩০০ টন। নাটবোল্ট যোগান দিয়েছে হাওড়ার গেস্টকিন উইলিয়াম। এই সেতুর মোট খরচের আশি শতাংশই বহন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাকি কুড়ি শতাংশ বহন করেছে রাজ্য সরকার। সেতুর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের খরচ আদায়ের জন্য রাজ্য সরকার চালু করেছে ‘টোল-ট্যাক্স’। কলকাতার দিকে জায়গা না থাকায় ‘টোল-ট্যাক্স’-এর দপ্তর বসানো হয়েছে হাওড়ায়।
শেষ বিকেলের অপসৃয়মান আলোয় হাওড়া ব্রিজ বা রবীন্দ্রসেতু থেকে বিদ্যাসাগর সেতুর দিকে তাকালে মনে হয় দূর আকাশের নীচে কোনো পরী বসে আছে।
নমস্কার
বিনীত
সমরজিৎ চক্রবর্তী
তথ্যসূত্রঃ ১) বাংলায় ভ্রমণ / ১ম খন্ড – অমিয় বসু ২) পাঁচশো বছরের হাওড়া – হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩) হাওড়া জেলার ইতিহাস / ১ম খন্ড – অচল ভট্টাচার্য ৪) হাওড়া জেলার ইতিহাস – হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।