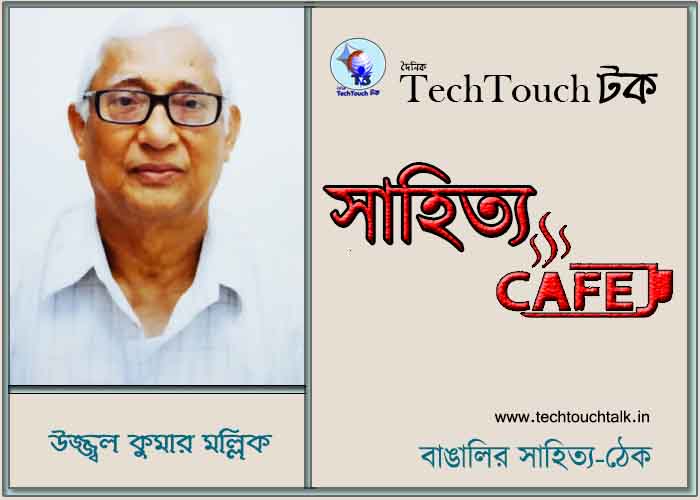রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

১৯২৪ সালের ১ অক্টোবরে হারুনা মারু জাহাজের বিশিষ্ট যাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আহ্বান’ কবিতায় লিখেছিলেন:
“অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে
রচিয়া রাখেনি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে..”( পূরবী কাব্যগ্রন্থ)।
৭ অক্টোবরে ‘খেলা’ কবিতায় লিখেছিলেন:
“তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেবো তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।” (পূরবী কাব্যগ্রন্থ)।
‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থে ‘প্রণাম’ কবিতায় লিখলেন:
“হে মানব তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্য ক্ষণে;…”
(শান্তিনিকেতন, ৬ এপ্রিল ১৯৩১)।
এই সময়েই নীতুকে পড়তে পাঠাচ্ছেন জার্মানিতে। এরই বছরখানেক পরে নাতির অসুস্থতার খবরে ভেতরে ভেতরে মর্মাহত কবি লিখছেন:
“কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।”
(প্রশ্ন, পরিশেষ, পৌষ ১৩৩৮)।
এর আগে রবীন্দ্রনাথ কখনো বলেননি তাঁর বাঁশি সংগীত হারিয়ে ফেলেছে; বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে; দুঃস্বপ্ন গ্রাস করেছে তাঁর সাধনার ভুবনকে। আমাদের মনে পড়ে যাবে ‘ছবি ও গান’ কাব্যগ্রন্থের ‘রাহুর প্রেম’ কবিতার কথা।
“এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ, এ অশ্রুজল, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্যের মতন বাজিবে সাথে সাথে দিবানিশি।।..”
লিখেছিলেন:
“কাঁটার মতন দিবসরজনী পায়েতে বিঁধিয়ে রব…
রোগের মতন বাঁধিব তোমারে…
বুকের মাঝারে ছুরীর মতন,
মনের মাঝারে বিষের মতন,
রোগের মতন, শোকের মতন…”
এক সাংঘাতিক অমঙ্গল চেতনার কথা লিখেছিলেন সেখানে। জীবনের উপান্তে সত্তর বছর বয়সে এসে ‘প্রশ্ন’ কবিতায় আরো একবার যেন গরলায়িত প্রসঙ্গ পথরোধ করে দাঁড়াল।
১৩৩৮ বঙ্গাব্দের পৌষ, অর্থাৎ ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৩২ এর জানুয়ারির কোনো একটা সময়ে লেখা এই প্রশ্ন কবিতার প্রেক্ষাপটে ওই ১৯৩১ এ তেইশে মার্চ তারিখে তেইশ বৎসরের তরুণ বিপ্লবী ভগৎ সিংহের ফাঁসির কথাটা স্মরণ করার যোগ্য মনে করি। বক্সা দুর্গের বিপ্লবী বন্দীরা এই ১৩৩৮ এর বৈশাখে বক্সা দুর্গের বিপ্লবী বন্দীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করেন। রবীন্দ্রনাথকে জন্মদিনের অভিনন্দন পাঠান। সেই সংবাদ পেয়ে ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ তারিখে কবি দার্জিলিংয়ে বসে যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা এখানে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন:
“বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি
নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুত্থ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।
‘ অমৃতের পুত্র মোরা ‘ — কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।”
এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের হিজলী জেল হত্যাকাণ্ডটিও স্মরণীয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবপ্রচেষ্টা তীব্র গতি নিতে থাকায় ১৯৩০ সালে বন্দীদের আটক রাখার জন্য হিজলী ডিটেনশন ক্যাম্প গড়ে ওঠে। এখানে নিরস্ত্র দুই বিপ্লবী, সন্তোষকুমার মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখে ডিটেনশন ক্যাম্প চত্বরের মধ্যে ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। প্রতিবাদী কণ্ঠকে থামাতে নিরস্ত্র দুই যুবকের উপর গুলি চালায় জেল প্রশাসন। জেলের ভিতরে নিরস্ত্র মানুষকে এই গুলি করে হত্যার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র হিজলী জেলে এসে শহীদদ্বয়ের মরদেহ সংগ্রহ করেন। এই সূত্রে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ তারিখে কলকাতার অক্টর্লনি মনুমেন্টের নিচে আহূত প্রতিবাদী জনসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।
উল্লেখ করা দরকার যে ‘প্রশ্ন’ ও ‘বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি’, এই দুটি কবিতাই ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।
১৯৩২ সালের ৫ আগস্ট প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ‘এদিকে কবিতা অনেকটা লেখা হচ্ছে -পূজার আগে বই বেরিয়ে যাবে। নাম দেবো ভাবছি পরিশেষ যা অবশিষ্ট ছিল। এবার কিন্তু নানা রকমের। সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা, বলাকা, বা আমার অন্য অন্য বইতে যেমন একটা ইউনিটি আছে এতে তা খুঁজে পাবে না। নানা রকম কবিতা আছে। এগুলি সব টুকরা টুকরা।’ পরিশেষ প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে। প্রকাশক শ্রী জগদানন্দ রায়। সেটা ছিল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ১৯৩২ সালের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাস। এই কাব্যগ্রন্থটি তিনি ব্যারিস্টার ও বিশিষ্ট সংগীতকার অতুলপ্রসাদ সেনকে উৎসর্গ করেছিলেন।
পরিশেষের প্রথম কবিতাটির শিরোনাম ‘প্রণাম’। এই কবিতায় তিনি লিখেছিলেন এক বাঁশির কথা । বিচিত্রের নর্মবাঁশি। নিজেকে বাঁশি ও বীণা হিসাবে ভাবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে বার বার লক্ষ করা যায়। এটা তাঁর একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল।
‘প্রমিথিউস আনবাউন্ড’ এর
“Ode to the West Wind” কবিতায় ইংরেজ কবি পার্সি বিশি শেলি লিখেছিলেন:
Make me thy lyre, even as the forest is:
What if my leaves are falling like its own!
The tumult of thy mighty harmonies
Will take from both a deep, autumnal tone,
Sweet though in sadness. Be thou, Spirit fierce,
My spirit! Be thou me, impetuous one!
এই কবিতায় শেলি আরো লিখেছিলেন:
Scatter, as from an unextinguish’d hearth
Ashes and sparks, my words among mankind!
Be through my lips to unawaken’d earth
The trumpet of a prophecy! O Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind?
রবীন্দ্রনাথ এই ‘প্রণাম’ কবিতায় লিখলেন নিজেকে বিচিত্রের নর্মবাঁশি ভেবে লিখলেন:
“আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে।”
বাঁশি কথাটা বারে বারে ফিরে ফিরে ফিরে এসেছে এই কবিতায়। পৃথিবীতে সূর্যের উদয় ও অস্ত, সৌর কিরণস্পর্শে প্রাণের যে চঞ্চলতা, তা কবি অনুভব করেন, এবং বলেন:
“..তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে;” ।
মহাবিশ্বের গভীরে অপার অন্ধকারের মধ্যে যে নীহারিকা ও নক্ষত্রের পথচলা, তাকেও তিনি উপলব্ধি করে বলেন:
“….আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের ‘পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম;..”।
কবির বাঁশরি কলস্বনা হয়ে উঠেছে, নিখিলের অনুভূতি তাঁর সংগীতসাধনায় আকুতি রচনা করেছে, তারপর সেই নানা-বর্ণে-চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি একের চরণে রেখে তাঁর চলে যাওয়া।
ওই ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৩ বৈশাখে শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছেন:
রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।…
বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হোক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।…
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, ‘আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা।’
‘অপূর্ণ’ কবিতায় লিখেছেন:
“আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা–
মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা..”
লিখেছেন:
“জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।”
প্রশ্ন তোলেন:
“অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।”
মৃত্যু প্রসঙ্গে আরো একটি কবিতা ‘বর্ষশেষ’। এটি লিখেছেন অনেকটা আগে, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০ চৈত্র তারিখে। এখানে পাই:
যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।…
বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।…
অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি আপন চারি ধার
জীবনমৃত্যুরে দিল করি একাকার;
বেদনার পাত্র মোর বারংবার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব অমৃতে।…
কতদিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে।..”
যে সময় পরিশেষ প্রকাশিত হল, তার মাসদুয়েক আগে, ৩ আষাঢ় ১৩৩৯ তারিখে ‘স্পাই’ নামে একটা কবিতা লিখেছিলেন। ওখানে লিখেছেন,
“উপোস করে মারা গেল সোনার-টুকরো ছেলে
নন্-ভায়োলেনস প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।”
তারপর শহীদ বিপ্লবীর সম্বন্ধে লিখেছেন –
খুলে দেখি পাতার পরে পাতা–
দেশের কথা কী বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে…
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ
মৃত্যুসুধার নিত্যপরশ দিয়ে।”
এইসূত্রে হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য যতীন দাশের আত্মাহুতি মনে পড়া স্বাভাবিক। বিপ্লবী যতীন দাশ ( জন্ম: ২৭ অক্টোবর ১৯০৪) লাহোর জেলে বন্দী ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে জেল সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের উপর ব্রিটিশ প্রশাসনের জঘন্য ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যতীন অহিংস পথে অনশন আন্দোলনে ব্রতী হন। ১৯২৯ সালের ১৩ জুলাই যতীন অনশন আন্দোলন শুরু করেন। কিছুতেই তাঁকে দমানো যায় নি। জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলেও সে সুবিধা গ্রহণ করেন নি যতীন। তিনি সকল রাজনৈতিক বন্দীর প্রতি জেল অভ্যন্তরে মানবাধিকারের দাবিতে অনড় থাকেন। লাহোর জেলে তেষট্টি দিন একটানা অনশন করে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তারিখে শহীদ হন যতীন দাশ। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ।
১৭ আষাঢ় ১৩৩৯ সালে ‘মৃত্যুঞ্জয়’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। এই কবিতায় মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর একটি উপলব্ধি ধরা পড়ে। লিখেছিলেন
“যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো ব’লে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।”
পরিশেষ এর একমাস পর এল পুনশ্চ। তার প্রকাশ হল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ফাল্গুন ১৩৪০ বঙ্গাব্দে আরো কতকগুলি কবিতা জুড়ে পুনশ্চের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এর কতকগুলি একেবারেই নূতন। আর কতকগুলি পরিশেষ থেকে খসিয়ে নেওয়া।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুচেতনা বিষয়ক আলোচনায় পুনশ্চের ‘বিশ্বশোক’ কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতা ও তার পশ্চাৎপট নিয়ে আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই কবিতায় গোটা বিশ্বজগতের প্রেক্ষিতে নিজের দুঃখকে কণার কণা বলে চিনেছিলেন। বলেছিলেন
“এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে”
আরো বলেছিলেন:
‘চিরকালের সেই মানুষের শোক নামল হঠাৎ আমার বুকে;
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল পাঁজরগুলো–
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,…’
বিশ্বশোক কবিতার একেবারে শেষে বললেন:
‘আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে,
লজ্জা দিও না।…
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিও
বিশাল বিশ্বসুরে।’
পুনশ্চের তীর্থযাত্রী কবিতাটি চলতি অর্থে মৌলিক রবীন্দ্র কবিতা নয়। টমাস স্টার্নস এলিয়ট (১৮৮৮ – ১৯৬৫) ছিলেন একজন অগ্রণী ব্রিটিশ কবি। তিনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পেলেও অনেক আগে থেকেই সাহিত্যানুরাগীদের গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি ‘জার্নি অফ দি ম্যাজাই’ নামে ৪৩ লাইনের একটি কবিতা প্রকাশ করেন। বাংলা আধুনিক কবি ও ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক বিষ্ণু দে পুনশ্চের গদ্য কবিতার ধাঁচটা বুঝতে চেয়ে জার্নি অফ দি ম্যাজাই কবিতার একটি স্বকৃত অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন পুনশ্চের লিখনশৈলীর আদলে কবিতাটির একটি পুনর্নির্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রকৃত অনুবাদটি পরিচয় পত্রিকার মাঘ ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।
মূল কবিতায় টি এস এলিয়ট লিখেছিলেন:
Birth or Death? There was a Birth, certainly,
We had evidence and no doubt. I had seen birth and death,
But had thought they were different; this birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death.
….
I should be glad of another death.
রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:
“জন্ম একটা হয়েছিল বটে–
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও–
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর–
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
…
আর একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।”
বলা দরকার, পুনশ্চের প্রথম সংস্করণ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। তারপর অনুজকবি বিষ্ণু দে জার্নি অফ দি ম্যাজাইকে পুনশ্চের লিখনশৈলীর আদলে দেখতে চাইলে তীর্থযাত্রী লেখা হয়েছিল। অর্থাৎ পুনশ্চের ছন্দের চলনটা ঠিক কেমন, তা রবীন্দ্রনাথ এই তীর্থযাত্রী কবিতার মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। মাঘ মাসে লেখা এই তীর্থযাত্রী ফাল্গুন ১৩৩৯ এ প্রকাশিত পুনশ্চের দ্বিতীয় সংস্করণে রয়েছে।
টমাস স্টার্নস এলিয়ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাইতে বয়সে বেশ খানিকটা ছোট ছিলেন। অনুজ একজনের কবিতা যত্ন নিয়ে অনুবাদ করা, এবং সেই কবির নামোল্লেখ করে নিজের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা, এই বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। জন্ম এবং মৃত্যুকে একই রকম যন্ত্রণাময় করে দেখতে পারা এবং জন্মকে যন্ত্রণাবিদ্ধ হবার সামিল করে লক্ষ করতে পারা রবীন্দ্রচিন্তার নতুন একটা দিককে উন্মোচিত করে।
যীশুখ্রীস্ট জন্মেছিলেন এবং দু দুটো চোরের সঙ্গে
তাঁকে হাতে পায়ে গজাল বিঁধে ক্রুশে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ক্রুশে ঝুলানোর আগে যীশুকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল। মৃত্যুর নবম প্রহরে প্রবল শারীরিক যন্ত্রণা ও ততোধিক মনোবেদনায় আর্তনাদ করে উঠে বলেছিলেন–এলি এলি লামা সাবাকতানি
আরামাইক ভাষায় যীশু কথিত এই বক্তব্যের রবীন্দ্রকৃত অর্থ: ‘হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর, কেন আমায় পরিত্যাগ করলে!’
১৩৩৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে মানবপুত্র’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।
হয়তো কবি তাঁর আজীবনের বন্ধু ও গুণগ্রাহী চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ডরুজের লেখা What I Owe to Christ বইটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে এই মানবপুত্র কবিতাটি লিখেছিলেন। এই সময়েই নীতুর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, এইভাবে পরবর্তীকালে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু যীশুর মৃত্যুকালীন সময়ে সেই ধরনের প্রচার থেকে থাকলে ওই নিষ্ঠুর অসম্মান, ওই মাপের শারীরিক নির্যাতন তাঁকে বহন করতে হত না। ঈশ্বরের ভূমিকা মরজগতের মানুষের পক্ষে ঠিক কি এবং কতটুকু, তা যীশুর মৃত্যু দিয়েই সুচিহ্নিত হয়ে গিয়েছে। লোককথায় যীশুকে ঈশ্বরের প্রতি অনুগত মানুষ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। যদি তাই হয়, তবু লক্ষ করা যায় যে যীশুক্রুশবিদ্ধ হবার পর নবম প্রহরে যন্ত্রণাকাতর হয়ে হাহাকার করেছিলেন – ‘হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর, কেন আমাকে ত্যাগ করলে।” এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চের মানবপুত্র কবিতায় যীশুর উক্তি হিসাবে ব্যবহার করলেন। সচেতন পাঠককে এই উক্তির মধ্যে “ঈশ্বর” এবং “মানুষের ঈশ্বর” এই দুটি এক্সপ্রেশনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ করবেন। রবীন্দ্রনাথ যেন অনুভব করছেন — বিশ্বচালনার পিছনে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের নিয়ম। তা মানুষের আবেগ নিরপেক্ষ। আর মানুষের নিজের ভিতরে হৃদয়ে মননে বিবেকী পরাক্রমে শুভবোধে তার কোনো এক আপন ঈশ্বর রয়েছেন। যিনি মানুষের ভালবাসা পাবেন বলে অপেক্ষা করে থাকেন, যাঁর সাথে মানুষী বিবেকের দেওয়া নেওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে।।… ‘ (গীতবিতান, পূজা পর্যায়, ২৯৪ সংখ্যক গান)।
লিখেছিলেন, ‘নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।’
স্পষ্টতই রবীন্দ্রকল্পিত এই ভগবানের সঙ্গে মানুষের দেওয়া নেওয়া। আর ‘বিশ্বশোক’ কবিতায় লিখেছিলেন,
অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি–“
বার বার অবিচলিত, অকরুণ, অনিমেষ, অকম্পিত, অনিভৃত, অসংখ্য, এই গোত্রের শব্দগুলির অমোঘ ও অব্যর্থ প্রয়োগ যত্নশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না।
এই পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থেই ২৬ ভাদ্র ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে লেখা ‘মৃত্যু’ শীর্ষক কবিতায় লিখেছিলেন–
“সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এধারে।
এক পা তখনো আছে সে প্রান্তসীমায়
অন্য পা আমার বাড়িয়েছি রেখার ওধারে…”
এই কবিতাতেই মহাজাগতিক নীহারিকা নক্ষত্রমালাকে ‘রজনীর অক্ষমালা’ হিসাবে চিনেছিলেন। এই ‘অক্ষমালা’ শব্দটি আমাদের পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের প্রণাম কবিতাটিকে মনে করিয়ে দেবে, যেখানে তিনি বলেছিলেন,
‘যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনা মন্ত্র-জপে।”
নীতুর মৃত্যুতে কন্যা মীরাকে লিখেছিলেন
” এসেছি সংসারে, মিলেচি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েচে, এমন কত বারবার হোলো, বারবার হবে– এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠচে। যতবার যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলচে, অবিচলিত মনে তার যাত্রার সঙ্গে আমার যাত্রা মেলাতে হবে। লজ্জা হয় যদি আমার শোক নিয়ে একটুও সরে পড়ি সকলের সংসার থেকে, লেশমাত্র ভার চাপাই নিজের অচল বেদনা নিয়ে বিশ্ব-সংসারের সচল চাকার উপরে।.. এরপরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক…” (২৮ আগস্ট, ১৯৩২)।
পরিশেষ থেকে তিনি পুনশ্চ হয়ে ওঠেন সমস্ত ব্যক্তিগত যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেয়ে।