রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প – ১৪
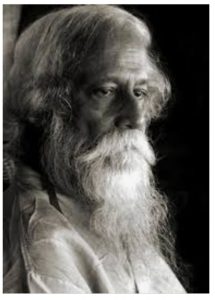
কালিম্পং এর গৌরীপুর ভবনে বসে ২২ মে ১৯৪০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:
“রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর;
আদিম বন্যতা তার উদবারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।…”
কবিতাটি আরো দীর্ঘ। এটি প্রবাসী পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪৭ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, এবং জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থে ২১ সংখ্যক কবিতা হিসেবে সংকলিত হয়েছিল।
‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখে যাওয়া তাঁর শেষ বই। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, ৮ মে, ১৯৪১, বাংলা ক্যালেণ্ডারে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখের প্রথম দিন। বিশ্বভারতী থেকে বইটি প্রকাশ করেন পুলিনবিহারী সেন। ‘নির্বাণ’ গ্রন্থে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী লিখেছেন, ‘তিনি এই শুভ জন্মতিথিতে দেশকে ও মানুষকে শেষ উপহার দিলেন, এই কবিতাগুলি তাঁর জীবনযজ্ঞের আহুতির শিখা, অনেক দুঃখের তপস্যার ফল। এর পাতায় পাতায় রয়েছে তাঁর শেষ বর্ষের ইতিহাস।’
এই জন্মদিনে কাব্যগ্রন্থের ২১ সংখ্যক কবিতাটি বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা পালনের প্রশ্নে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই কবিতার শেষ অংশে রয়েছে:
‘শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,….
…আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।’
এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিম্পং এ আছেন এবং ওখান থেকে ১৯৪০ সালের ১৫ জুন তারিখে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে তিনি একটি টেলিগ্রাম বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন, All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and there few lines of mine merely convey my hope even if unnecessary, that she will not fail in her mission to stand against this universal disaster that appears so imminent.
এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে কী লিখেছেন লক্ষ করা যাক। তাঁর স্মৃতিচারণে: … কালিম্পং এ একদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর কাছে বসে আছি, – তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলেছে, প্যারিসের সেদিন পতন হয়েছে। কিছুদিন থেকে রোজই সবাই মিলে রেডিওর সংবাদ শোনা হচ্ছে, খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে, আর চলেছে উত্তেজিত আলোচনা।

বিশেষ করে মাদমোসেল বসনেক বলে একটি ফরাসি ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে ছিলেন, ফ্রান্সের খবর তাই খুঁটিয়ে শোনা হত। সেদিন গুরুদেবের শরীরটা ক্লান্ত ছিল, চুপচাপ বিশ্রাম করছেন। হঠাৎ দরজার কাছে উত্তেজিত অথচ মৃদু করুণ কণ্ঠস্বরে গুরুদেব বলে মাদমোসেল ঘরে ঢুকে তাঁর বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন – “গুরুদেব আজ ওরা প্যারিসে ডাকঘর অভিনয় করছে এখন!” তিনি উঠে বসলেন। বেশ বুঝলুম মনের ভিতরে একটা নাড়া লাগল। “আজ? আজ ওরা ডাকঘর অভিনয় করেছে?” একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে আবার যেমন ছিলেন তেমনি শুয়ে পড়লেন, শুধু উত্তেজিতভাবে পা নড়ছিল। অনেকক্ষণ পরে বল্লেন – সেবারও রাশিয়াতে ওদের দারুণ দুঃখের দিনে ওরা বার বার অভিনয় করেছে কিং অফ দি ডার্ক চেম্বার। আবার দীর্ঘক্ষণ নীরবতা -‘একেই বলে পুরস্কার।’
যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন কবি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ( ১৪ মার্চ ১৮৭৯ – ১৮ এপ্রিল ১৯৫৫), রম্যাঁ রলাঁ ( ২৯ জানুয়ারি ১৮৬৬ – ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৪), জর্জ বার্নার্ড শ ( ২৬ জুলাই ১৮৫৬ – ০২ নভেম্বর ১৯৫০), এবং বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮ মে ১৮৭২ – ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০) এর মতো বিশ্ববিখ্যাত নোবেল জয়ী মানুষেরা।
আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে জার্মান ভাষায় চার চারটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করে বিজ্ঞানচর্চার এক নতুন যুগসৃষ্টি করেছিলেন। পদার্থ যে প্রকৃত পক্ষে শক্তির ঘনীভূত রূপ, তা তিনি তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ওইসূত্রে পারমাণবিক বোমার কথাটা নাড়াচাড়া হচ্ছিল। জার্মানির উদ্যোগে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা মারণাস্ত্রের জন্ম দিতে পারে, আইনস্টাইনের মনে এই উদ্বেগ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সহযোগী গবেষক ছাত্র লিও জিলার্ড। ছাত্রের উদ্যোগে আইনস্টাইন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কে অনুরোধ করেছিলেন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে। তবে লিও জিলার্ড সেই অস্ত্র জাপানের উপর প্রয়োগ হোক, এটা চাননি। বরং আমেরিকার ম্যানহাটান প্রকল্পে কর্মরত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের সম্মিলিত করেছিলেন বোমা নিক্ষেপ করার বিরুদ্ধে। পরে দেখা গেল জার্মানি আদৌ বোমা তৈরি করতে পারেনি। শোনা যায়, আইনস্টাইন হাহাকার করেছিলেন, আমি যদি জানতাম, জার্মানি পারবে না, তাহলে কিছুতেই আমেরিকাকে বোমা বানাতে বলতাম না। এরপরে বিশ্বশান্তি গড়ে তুলতে আইনস্টাইন গভীর ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বড়মাপের মনীষীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ পেয়ে গিয়েছিলেন। রম্যাঁ রলাঁ লিখেছিলেন ‘অ্যাবাভ দ্য ব্যাটল।’ ওটা একটা শান্তিবাদী ম্যানিফেস্টো ছিল। ১৯১৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ওটি চিকাগোর দি ওপেন কোর্ট পাবলিশিং কোম্পানি প্রকাশ করেন। ওই বছরের এপ্রিলেই এটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছিল।
বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন বড়মাপের গণিতপ্রতিভাধর মানুষ। তিনি ১৯১৬ সালে লেখেন ‘হোয়াই মেন ফাইট।’ আর লেখেন ‘জাস্টিস ইন ওয়ার টাইম।’ এটি প্রকাশ করেছিলেন দি ওপেন কোর্ট পাবলিশিং কোম্পানি। ১৯২৭ সালের ছয় মার্চ তারিখে ন্যাশনাল সেক্যুলার সোসাইটিতে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। ওরই লিখিতরূপ ‘হোয়াই আই অ্যাম নট এ ক্রিশ্চিয়ান।’ লণ্ডন থেকে এ বই বেরোলো। এই বইয়ের অনুষঙ্গে অনেক বই বেরিয়েছিল। ১৯৩০ সালে ভগৎ সিংহের ‘কেন আমি নাস্তিক’ বইটি প্রকাশ পেয়েছিল।
১৯২৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ’। ১৮৮৫ সালের সার্বিয়া বুলগেরিয়ার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে শ’ লিখেছিলেন ‘আর্মস অ্যাণ্ড দি ম্যান।’ পুস্তকাকারে প্রকাশের আগেই ২১ এপ্রিল ১৮৯৪ তারিখে ওটি অভিনীত হয়েছিল। প্রকাশ করা হয়েছিল ১৮৯৮ সালে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিণত জীবনের কবিতাগুলিতে যুদ্ধ বিরোধিতা ও একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা একটি মূলসুর হয়ে ওঠে। মুসোলিনির ন্যক্কারজনক রূপটি রবীন্দ্রনাথকে চিনতে সাহায্য করেছিলেন রম্যাঁ রলাঁ।
হিটলারের চেহারাটা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন কবি। আর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাও যে তাঁর কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল, সে আমরা রক্তকরবী নাটকের সূত্রে লক্ষ করেছি।
জাপানের মধ্যেও যে একটা দানবিক শক্তি মাথা তুলে ফেলেছে, এও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।
‘প্রান্তিক’ কাব্যগ্রন্থের ১৭ নং কবিতাটি লিখেছিলেন শান্তিনিকেতনে বসে। ১৯৩৭ সালের বড়দিনে। ওই কবিতায় পাই:
“যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে; তপ্তধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে। দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল– সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। মহাকালসিংহাসনে
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-‘পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।”
১৯৩৯ সালের ১ এপ্রিল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বসে লিখেছেন “আহ্বান”। সেখানে পাই:
কানাডার প্রতি
বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধনধন যত
দানবপদদলনে হল গুঁড়া।
তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়,
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।
মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে, রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলীর পদে দুর্বলেরে কোরো না বলিদান।
এই কবিতা স্থান পেয়েছে ‘নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থে। নবজাতকের আরেকটি কবিতা ‘পক্ষীমানব।’ এটি লেখার তারিখ ২৫ ফাল্গুন, ১৩৩৮, বা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস।
কবিতাটি এ রকম:
পক্ষীমানব
যন্ত্রদানব, মানবে করিলে পাখি।
স্থল জল যত তার পদানত
আকাশ আছিল বাকি।
বিধাতার দান পাখিদের ডানাদুটি।
রঙের রেখায় চিত্রলেখায়
আনন্দ উঠে ফুটি;
তারা যে রঙিন পান্থ মেঘের সাথি।
নীল গগনের মহাপবনের
যেন তারা একজাতি।
তাহাদের লীলা বায়ুর ছন্দে বাঁধা;
তাহাদের প্রাণ, তাহাদের গান
আকাশের সুরে সাধা;
তাই প্রতিদিন ধরণীর বনে বনে
আলোক জাগিলে একতানে মিলে
তাহাদের জাগরণে।
মহাকাশতলে যে মহাশান্তি আছে
তাহাতে লহরী কাঁপে থরথরি
তাদের পাখার নাচে।
যুগে যুগে তারা গগনের পথে পথে
জীবনের বাণী দিয়েছিল আনি
অরণ্যে পর্বতে;
আজি একি হল, অর্থ কে তার জানে।
স্পর্ধা পতাকা মেলিয়াছে পাখা
শক্তির অভিমানে।
তারে প্রাণদেব করে নি আশীর্বাদ।
তাহারে আপন করে নি তপন,
মানে নি তাহারে চাঁদ।
আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশস্বরে গর্জন করে
বাতাসেরে জর্জরি।
আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে–
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।
দেবতা যেথায় পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।
আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন–
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।
:নবজাতক’ কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা এ রকম
প্রায়শ্চিত্ত
উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ-আলো–
নিম্নে নিবিড় অতিবর্বর কালো
ভূমিগর্ভের রাতে–
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।
দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল
ভূমিকম্পের রোল,
জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে
লাগিল ভীষণ দোল।
বিদীর্ণ হল ধনভাণ্ডারতল,
জাগিয়া উঠিছে গুপ্ত গুহার
কালীনাগিনীর দল।
দুলিছে বিকট ফণা,
বিষনিশ্বাসে ফুঁসিছে অগ্নিকণা।
নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
বিদীর্ণ হয়ে, তার
কলুষপুঞ্জ ক’রে দিক উদগার।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা,
রক্তসিক্ত লুব্ধ নখর
একদিন হবে ঢিলা।
প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্লভতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন–
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।
ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়।
দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা
ভীত প্রার্থনারবে
শান্তি আনিবে ভবে।
কৃপণ পূজায় দিবে নাকো কড়িকড়া।
থলিতে ঝুলিতে কষিয়া আঁটিবে
শত শত দড়িদড়া।
শুধু বাণীকৌশলে
জিনিবে ধরণীতলে।
স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা।
সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।
এটি লিখেছেন ১৭ আশ্বিন, ১৩৪৫। ওইদিন বিজয়াদশমী ছিল।
১৯৩৮ সালে লেখা আরেকটি কবিতাও বিশেষ করে লক্ষ করা দরকার। এটি লিখেছেন শান্তিনিকেতনে, ৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮ তারিখে।
বুদ্ধভক্তি
(জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি, জাপানি সৈনিক
যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে যুদ্ধমন্দিরে
পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে,
ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।)
হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ,
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির–
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।
গর্জিয়া প্রার্থনা করে–
আর্তরোদন যেন জাগে ঘরে ঘরে।
আত্মীয়বন্ধন করি দিবে ছিন্ন,
গ্রামপল্লীর রবে ভস্মের চিহ্ন,
হানিবে শূন্য হতে বহ্নি-আঘাত,
বিদ্যার নিকেতন হবে ধূলিসাৎ–
বক্ষ ফুলায়ে বর যাচে
দয়াময় বুদ্ধের কাছে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।
হত-আহতের গনি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস–
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ধাঁচটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। আমেরিকার সোশ্যালিস্ট ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার এর লেখা ‘দি ব্রাস চেক’ তিনি পড়েছিলেন। দি ব্রাস চেক লেখা হয়েছিল ১৯১৯ সালে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি কিভাবে সাংবাদিকদের পর্যন্ত গোলাম বানিয়ে ফেলে সে ব্যাপারে সোজা সাপটা লেখা লিখেছিলেন সিনক্লেয়ার। রক্তকরবী তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখলেন মুনাফালোভী শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা কিভাবে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটিয়ে শাসন দীর্ঘায়িত করে। এমনকি ধর্মকেও কাজে লাগায়। তার মন্দির, মদের ভাঁড়ার আর অস্ত্রশালার একত্র অবস্থান আর জপমালার সুতো ও চাবুকের উপাদানের অভিন্নতা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করা দরকার।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ বেরিয়েছিল ১৬ জানুয়ারি ১৯১২ তারিখে; লেখাটি হয়েছিল ওই বছরের আগস্টে। ওই একই আগস্ট মাসের ০২ তারিখে অচলায়তন নাটক প্রকাশ হয়েছিল। মুক্তধারা বেরিয়ে ছিল দশ বছর পরে, ১৯২২ সালের ২৮ জুন তারিখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্তধারা, রক্তকরবী এইসব নাটকের ভিতরে কবি বলতে চেয়েছেন, “জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের ‘পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি।তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, সে জীবন।
… জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায় — তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে।” কবির এই লেখাটা “সবুজ পত্র” পত্রিকায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন কার্তিক সংখ্যায় বেরিয়েছিল। পরে আত্মপরিচয় গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আরো নজর করতে হবে যে এইসব নাটক বিশেষ করে ফাল্গুনী, রক্তকরবী রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করাচ্ছেন, নিজেও করছেন, বাঁকুড়ার দুর্গত মানুষ বা বিহারের ভূকম্পপীড়িত মানুষের ত্রাণের আয়োজনের লক্ষ্যে। শিল্প কেন, শিল্প কার জন্য, এ ব্যাপারে কোনো দোলাচল থাকলে এমন উদ্যোগ নেওয়া হত না।
১৯২১ সালের ০৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিউ ইয়র্ক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ডরুজকে লিখেছিলেন, I cannot tell you how deeply I am suffering, being surrounded in this country by endless ceremonials of this hideously profane cult. .. Negroes are burnt alive…. Conditions in Russia are deliberately misrepresented.
রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় পৌঁছেছেন ১৯৩০ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে। দিন পনেরো সেখানে ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কী দেখলেন আর কী ভাবলেন তা পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, নির্মলকুমারী মহলানবীশ, আশা অধিকারী, সুরেন্দ্রনাথ কর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু, কালীমোহন ঘোষ, ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছেন। চিঠিগুলি প্রবাসী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ০৮ মে এই চিঠিগুলি একত্রে রাশিয়ার চিঠি নামে প্রকাশিত হয়।
রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় অধ্যাপক পেট্রফকে বলেছিলেন, In America I read a book devoted to questions of education in USSR. The book was written by an American woman. It gave me the first idea of how education works in the USSR, and made a strong impression on me. Since then I have been an admirer of your system of education. This book inspired me and showed that there was much in common between the dream of my life and what you are doing.
রবীন্দ্রনাথ নিজের পুত্রবধূকে চিঠিতে লিখেছেন, “আমি যা বহুকাল ধ্যান করেচি রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারিনি বলে দুঃখ হোল। … নিজের প্রজাদের সম্বন্ধেও আমার অনেক কালের বেদনা রয়ে গেচে। মৃত্যুর আগে সে দিককার পথও কি খুলে যেতে পারব না?”
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লব পরবর্তী দেশগঠনকে দুহাত তুলে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন কবি। কেননা সেখানে নিচের তলার সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা বিস্তার করার চেষ্টা চলছিল।
বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা যে সত্যিই সাধারণ মানুষের সমস্যা দূর করতে পারে, এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক দিন ধরে ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে তার সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।
নিজের যৌবনে, ১৩০৪ বঙ্গাব্দে, বা ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে “কল্পনা” কাব্যগ্রন্থে একটি দীর্ঘকবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতার নাম ‘জুতা আবিষ্কার।’ এটি ছাত্রপাঠ্য ও কৌতুকমূলক কবিতা হিসেবে সাধারণভাবে পরিচিত হলেও বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের আলোচনায় কবিতাটির দু একটি পংক্তি অসম্ভব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। জুতা আবিষ্কারের পিছনে হবু রাজার সঙ্গে গোবু মন্ত্রীর কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ লক্ষ করি রাজা বলছেন, ‘কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা/ উপাধি ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে।’ এই পংক্তিতে রাজার কাছে একজন বৈজ্ঞানিক যে নিছক একজন ভৃত্য মাত্র, এবং বৈজ্ঞানিকের ডিগ্রি ডিপ্লোমার বাস্তব মূল্য রাজার কাছে ঠিক কতটুকু তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন এবং মেডিসিনের বহু কিছু আবিষ্কার বাকি। আইনস্টাইনের যুগান্তকারী তত্ত্ব আসতে দেরি আছে। ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন আবিষ্কার হয়নি। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে সদ্য সদ্য কাজ হয়েছে। মেডিসিনের জগতে পেনিসিলিন আসতে দেরি আছে। হিটলার এবং স্ট্যালিন, দুজনের কেউই ক্ষমতাধর রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন নি। রাইট ভাইয়েরা তখনো এরোপ্লেন ওড়াননি।
এইরকম সময়ে বিংশ শতাব্দীর সূচনার আগেই একজন বৈজ্ঞানিক যে আধুনিক রাষ্ট্রনায়কের হাতের পুতুল, ও আদেশপালনকারী ভৃত্য মাত্র, কবির এই ধারণাটা কি আশ্চর্যজনক নয়?
এই সূত্রে আমরা ফ্রিৎস হেবার এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, এই দুই নামজাদা নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীর কী হাল করেছিল রাষ্ট্রশক্তি, তা দেখে নিতে পারি।
লিও জিলার্ড, এডওয়ার্ড টেলার, রবার্ট ওপেনহাইমার প্রমুখের জীবনেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও আমরা লক্ষ্য করতেন পারি।
১৩৪৪ বঙ্গাব্দে ‘মাধো’ নামে একটি কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। কবিতাটি ‘ছড়ার ছবি’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ছড়ার ছবি পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়েছে ১৯৩৭ সালের ০৫ অক্টোবরে। কবিতাটি দীর্ঘ। তার অংশ বিশেষ এই রকম:
…এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার
মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার
ধর্মঘটে বাঁধল কোমর; সাহেব দিল ডাক—
বললে, ‘মাধাে, ভয় নেই তাের, আলগােছে তুই থাক্।
দলের সঙ্গে যােগ দিলে শেষ মরবি-যে মার খেয়ে।’
মাধাে বললে, ‘মরাই ভালাে এ বেইমানির চেয়ে।’
শেষ পালাতে পুলিস নামল, চলল গুঁতােগাঁতা;
কারাে পড়ল হাতে বেড়ি, কারাে ভাঙল মাথা।
মাধো বললে, ‘সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে,
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে না যে।’
বলা দরকার যে, ‘মাধো’ রচনার অল্প কিছুদিন আগেই কলকাতার ধারে পাশের পাটকলগুলিতে একটি ধর্মঘট শুরু হয়েছিল এবং শ্রমিকদের সমর্থন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে মজুরির বৃদ্ধি এবং কার্যের উন্নততর ব্যবস্থার জন্য শ্রমিকদের দাবি ন্যায্য ও সঙ্গত। কবির এ কথা আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল।
মানুষের সভ্যতা শেষপর্যন্ত দরিদ্রতম ও দুর্বলতম মানুষের সুস্থভাবে বাঁচার ও বিকশিত হতে দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু গরিব মানুষের মধ্যে এক অংশ যদি অন্য অংশকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়?
১৯৩৯ সালের ২৮ মার্চ শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে। কবিতাটি আছে “আকাশ প্রদীপ” কাব্যগ্রন্থে। দেশের মানুষের হাতে দেশের মেয়ে ধর্ষিত হয়ে খুন হচ্ছে, এমন একটা বিষয়কে লিখছেন তিনি। ভয়ঙ্কর কষ্টে বলছেন, দেশের মানুষ একই শ্রেণির মানুষ যদি এভাবে দুর্বলকে যৌন অত্যাচার করে খুন করে, তাহলে কোন্ আইন তার প্রতিকার করবে? হাহাকার করে বলেন, ‘শাস্ত্রমানা আস্তিকতা ধুলোতে যায় উড়ে/ উপায় নাই রে নাই প্রতিকার বাজে আকাশ জুড়ে।’ এই রবীন্দ্রনাথই ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত ‘শেষ সপ্তক’ কাব্যগ্রন্থের ‘পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ’ কবিতায় এক রোঘো ডাকাতের কথা বলেছিলেন। রোঘো ডাকাতের সর্দার, আর গরিব মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিত সে। শেষসপ্তক থেকে আকাশ প্রদীপে এসে যুগান্তর হয়ে গেল। নিচের তলার মানুষের নৈতিকতায় হল ভয়াবহ ক্ষয়। আমরা মনে করতে পারব ‘রক্তকরবী’ নাটকে নন্দিনীর প্রতিবাদী চরিত্রকে কালি মাখানোর চেষ্টা করছে শ্রমিকদের একাংশ। তাকে ডাইনি বলছে। বলছে, নন্দিনী কেবল তরুণদের মন ভোলাবার জন্য সুন্দরীপনা করে বেড়ায়। আর হুমকি দিচ্ছে নন্দিনীকে তারা নষ্ট করে দেবে। আমাদের মনে পড়ে যাবে মাদাম মেরি কুরির কথা। ১৯১১ সালে এই প্রতিভাময়ী বিজ্ঞানীর চরিত্রহননে ও কেচ্ছা ছড়ানোয় উঠে পড়ে লেগেছিল ফ্রান্সের একদল মানুষ। তবু রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহে নয়, শাস্ত্রমানা আস্তিকতায় নয়, মানুষের উপরেই বিশ্বাস রাখেন। বলেন, ‘ওই মহামানব আসে।’ ঈশ্বর নয়, রবীন্দ্রনাথের ভরসা শেষ পর্যন্ত মানুষের উপরে।

















