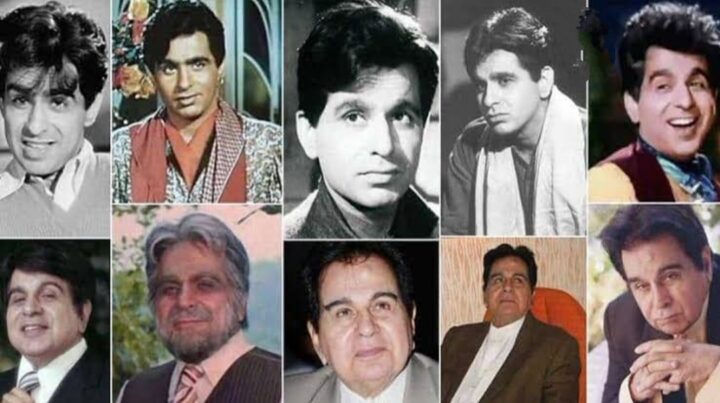রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী
রাষ্ট্রনীতি, জনপ্রশাসন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতা
একটি পরাধীন দেশ আর তার বাসিন্দাদের মনে স্বাধীনতার আকুতি আমরা দেখেছিলাম ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে। এর আগে যে বিদেশি শক্তি ভারতে আসে নি, তা কিন্তু নয়। পাঠান এবং মোগলেরা ভারতে এসেছিল। কিন্তু তখন যুগটা ছিল অন্যরকম। তারা ভারতের আবহাওয়ায় মিলে মিশে ভারতীয়ই হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রচেতনা, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও নাগরিক অধিকার বলতে যা বোঝায়, তা ব্রিটিশপূর্ব ভারতে ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, দেশটা কেমন দেখতে, তা সাধারণ মানুষ জানতই না। গুটিকয়েক ব্যবসাদার, এবং হাতে গোণা রাজপ্রতিনিধি পর্যটক লোক লস্কর নিয়ে হাতি ঘোড়া উটের পিঠে দেশভ্রমণ করতেন। আর দেশভ্রমণ করতেন ধর্মসংস্কারকেরা, প্রচারকেরা। অতি সাধারণ লোকে ঘর হতে আঙিনা বিদেশ জানত।
ব্রিটিশের বস্তুবাদী বিজ্ঞান প্রকৌশল এবং অনুসন্ধিৎসা কাশ্মীর থেকে কেরালা, আর আরাকান থেকে আরব সাগর তীর কেমন দেখতে তার ভূবৈজ্ঞানিক ধারণা দিয়েছিল। নদীর গতিপথ, মরুভূমির বিস্তার, পর্বতের উচ্চতা সাধারণ মানুষ জানত। কিন্তু সেটা ছিল ভাসা ভাসা ধারণা। ব্রিটিশ তাকে দিল গাণিতিক স্পষ্টতা। আর রেলপথ দিয়ে দেশের এক অংশের সাথে অন্য অংশের যোগসাধন করে দিল।
এর সাথে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে ভারতীয় পুঁথিতে ধৃত মহাকাব্য, বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, এইসব ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও মুদ্রণ হওয়ায় তা সাধারণ লেখাপড়া জানা মানুষের হস্তগত হল।
জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার ( ০৬.১২. ১৮২৩ – ২৮.১০. ১৯০০) সহ এশিয়াটিক সোসাইটি (১৫.০১.১৭৮৪) র প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোনস ( ২৮.০৯.১৭৪৬ – ২৭.০৪.১৭৯৪) এবং এশিয়া মহাদেশে আধুনিক কালে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরি ( ১৭.০৮.১৭৬১ – ০৯.০৬.১৮৩৪) এ ব্যাপারে সর্বাগ্রগণ্য।
দেশের মাটিতে দেশমাতৃকার মূর্তি কলমের আঁচড়ে যে কবিরা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে লুই হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ( ১৮.০৪.১৯০৯ – ২৮.১২.১৮৩১) এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত ( ২৫.০১.১৮২৪ – ২৯.০৬.১৮৭৩) কে স্মরণ করতে হয়।
মনে রাখতে হবে ইংরেজ সভ্যতা ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখে, পলাশীর যুদ্ধে হীনকৌশলে জয়লাভ করে ভারতে ক্ষমতা বিস্তারের প্রথম ধাপটি সেরে ফেলে। এই যুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফে নেতৃত্ব দেন রবার্ট ক্লাইভ ( ২৯.০৯.১৭২৫ – ২২.১১.১৭৭৪)। ইংরেজের যুদ্ধের গোলা বারুদ সাজ সরঞ্জাম ছিল উন্নতমানের। যুদ্ধকৌশলও ছিল আধুনিক। কিন্তু নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে হারাতে ক্লাইভকে ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল। ঘুষের প্রয়োগে নবাবের লোকেদের প্রভাবিত করে ইংরেজ পলাশীর যুদ্ধে জয় হাসিল করে। এই যুদ্ধে ইংরেজের বীরত্ব ও রণকৌশল নয়, নবাবের অজ্ঞতা আর ভারতীয়দের ঘুষ খাওয়ার জয় হয়েছিল।
মনে রাখতে হবে, রবার্ট ক্লাইভ বাংলাকে নির্মমভাবে লুঠ করে সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেন। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ অবধি বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে অখাদ্য খেয়ে মারা পড়ে। একে আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হিসেবে চিনি। বাংলাকে এত ভয়ংকর ভাবে লুঠ করে, বিস্তর ধনসম্পত্তি কুক্ষিগত করেও রবার্ট ক্লাইভ শেষরক্ষা করতে পারেন নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাঁর দুর্নীতি ও অবৈধভাবে ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করা নিয়ে মামলা হয়েছিল। ক্লাইভ তাঁর লুঠতরাজের জন্য স্বজাতির ভদ্রলোকেদের কাছে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়েছিলেন। বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের হাহাকার ও কান্না ব্রিটেনে শোনা গিয়েছিল। ১৭৭৪ সালে নিঃসীম আত্মগ্লানিতে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন। তখন বয়স তাঁর পঞ্চাশ ছোঁয় নি।
ভারতে যাঁরা শাসন করতে এসেছেন, ভারতীয় শিক্ষিত অভিজাত ও ধনিকগোষ্ঠী তাঁদের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তুলেছে। পাঠান ও মোগল আমলে অনেক সময়েই স্থানীয় ভূস্বামীরা প্রথাগত হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করে শাসকের ধর্ম গ্রহণ করেছেন। শাসকের বিশ্বাস অর্জনের খাতিরে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়েছেন।
শাসকেরাও ভারতের রুচি সংস্কৃতি আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র ও সাহিত্যের অনুবাদ ঘটেছে আরবি ফারসিতে। হিন্দি ও আরবি ফারসির মেলবন্ধনে উর্দিপরা লোকের হাতে উর্দূ জন্ম নিয়েছে।
স্থাপত্যশৈলী ও রন্ধনশৈলীতেও মেলবন্ধন পাওয়া গিয়েছে। শাসকের সাথে এই হৃদ্যতার সম্পর্ক ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রেও বন্ধ হয় নি। ভারতে প্রথম আসেন পর্তুগিজ নাবিকের দল। নেতৃত্বে ছিলেন ভাস্কো ডা গামা। ২০.০৫.১৪৯৮ তারিখে তিনি দলবল নিয়ে তিনি গোটা আফ্রিকার উপকূল বরাবর পাড়ি দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে কালিকট বন্দরে পৌঁছান।
মনে রাখি যে মাত্র কয়েকটি বৎসর আগে ১৪৯২ এর অক্টোবরে আরেকজন বিশ্ববিখ্যাত নাবিক অভিযাত্রী, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, ইণ্ডিয়া ভেবে বাহামায় পা রেখেছেন।
ভাস্কো ডা গামার অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে পর্তুগিজ সরকার তাঁকে ১৫২৪ সালে গভর্নর অফ ইণ্ডিয়া খেতাব দেন, ও ভাইসরয় পদে সম্মানিত করেন। ওই ১৫২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে চব্বিশ তারিখে এখনকার কোচিতে তিনি দেহরক্ষা করেন। ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পর্তুগিজদের পরে ভারতে এসেছিলেন যথাক্রমে ইংরেজ, ডাচ, ডেনিশ আর ফরাসি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এরা প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন। ১৬০০ সালে ইংরেজদের, ১৬০২ তে ডাচদের, ১৬১৬তে ডেনমার্কের আর সবার শেষে ১৬৬৪ তে ফরাসিদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।
ইতিমধ্যে ১৬১৯ নাগাদ কুশলী কূটনীতিক স্যর টমাস রো ( ১৫৮১ – ০৬.১১.১৬৪৪) কে আনিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ। স্যর টমাস রো মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর এর সভায় ব্রিটিশ স্বার্থের হয়ে দরবার করে সুরাটে ব্যবসা করার অনুমতি আদায় করেন।
ইংরেজদের প্রভাবে অন্য ইউরোপীয় জাতিগুলি ভারতে বিশেষ কিছু ক্ষমতা বিস্তার করতে পারে নি।
বণিকদের সাথে খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণও এদেশে এসেছেন। এদেশের মানুষ অশিক্ষা কুশিক্ষা র অন্ধকারে ডুবে আছে। এদেরকে আলোর সন্ধান দেবেন, উদ্ধার করবেন, খ্রীস্ট ধর্মের স্বাদ দিয়ে এদের জীবন সার্থক করবেন, এমন উদ্ভট মানসিক গঠন নিয়েই ধর্মপ্রচারকগণ ভারতে আসতেন।
এই সময় প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবস্থাপকগণও ভারতে এসেছেন। ধর্মপ্রচারকগণ তাঁদের আসতে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা মুদ্রণযন্ত্র এনে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র গড়ে তুলেছেন। ১৪৪০ সালে জোহান গুটেনবার্গ প্রথম আধুনিক অর্থে ছাপাখানা গড়ে তোলেন। অনেক দেরিতে ১৭৯৫ সালে এসেছে পুরোপুরি ধাতুর তৈরি প্রেস। ১৮০০ সালে এসেছে স্ট্যানহোপ প্রেস।
ধর্মপ্রচারকগণ এইসব মুদ্রণযন্ত্রে দেশীয় বিভিন্ন পুঁথি ছাপিয়ে তার অসারতা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা তুলে ধরে দেখাতে গিয়ে দেশীয় মানুষের কাছে তার হারিয়ে যাওয়া অভিজ্ঞান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। ভারতে মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উইলিয়াম কেরি ( ১৭৬১ – ১৮৩৪)র অবদান সর্বাগ্রগণ্য। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারে বাধা পেয়ে তিনি ডেনিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে ১৮০০ সালের জানুয়ারি মাসের দশ তারিখে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এর আগে যদিও অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের আয়োজনে ব্যাণ্ডেল প্রেস থেকে ১৭৭৮ সালেই নাথানিএল ব্রাসি হালেদ সাহেবের ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়েছে, তবুও কাজের ব্যাপ্তিতে ও গুণমানে শ্রীরামপুর প্রেস তুলনাহীন। কেরির আগ্রহে বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও লিপিবিশারদ স্যর চার্লস উইলকিনস (১৭৪৯ – ১৩.০৫.১৮৩৬) বিভিন্ন পুঁথির হস্তলিপি পাঠ, পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে বাংলা হরফের মান্য বয়ান তৈরি করে দেন। তারপর পঞ্চানন কর্মকার ও জামাতা মনোহর কর্মকার সেই অনুযায়ী লোহার হরফ তৈরি করেন। শ্রীরামপুর প্রেসে প্রথম মুদ্রক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।
ব্রিটিশেরা স্বজাতীয় কর্মচারীকে ভারতীয় ভাষাভাষী লোকের উপর শাসন, বিচার ও পরিচালনার যোগ্য করে তুলতে গিয়ে তাঁদেরকে দেশীয় ভাষা ও দেশীয় মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। ১৮০০ সালের ১০ আগস্ট তারিখে লর্ড ওয়েলেসলির পৌরোহিত্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগেই ১৭৮১ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে ক্যালকাটা মাদ্রাসা, আর ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিভিন্ন ধ্রুপদী প্রাচ্যভাষার পাশাপাশি ভারতীয় ভাষা পড়ানোর গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই কলেজের ফারসি ভাষাবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন নিল বি. এডমনস্টোন, আর তাঁর সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন জন এইচ হ্যারিংটন ও ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন।
আরবিক ভাষাশিক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন লেফটেন্যান্ট জন বেইলি। উর্দূ ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন জন বর্থউইক গিলক্রিস্ট। সেই সময় সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত মানুষের পছন্দের ভাষা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন হেনরি টমাস কোলব্রুক। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ধ্রুপদী ভাষার পাশাপাশি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন উইলিয়াম কেরি ( ১৭.০৮.১৭৬১ – ০৯.০৬.১৮৩৪)। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইউরোপীয় সিভিল সারভেন্টদের বাংলা ভাষাশিক্ষা দেবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বাচস্পতি, রামরাম বসু প্রমুখকে পণ্ডিত হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পড়িয়েছেন।
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পরে বুদ্ধিনাথ মুখার্জির আগ্রহে, ও ফোর্ট উইলিয়াম স্থিত সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস স্যর এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর বাড়িতে ২০ জানুয়ারি, ১৮১৭ তারিখে আহূত গুণী বিদ্যানুরাগীদের একটি সভায় প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন নাম ছিল হিন্দু কলেজ। তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং গোপীমোহন ঠাকুর হিন্দু কলেজের প্রথম গভর্নর হয়েছিলেন। সেক্রেটারি হয়েছিলেন বুদ্ধিনাথ মুখার্জি। একটি কমিটি হিন্দু কলেজের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা দেখাশোনার জন্য নির্দিষ্ট হয়। ওই কমিটির শীর্ষে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রথমে গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে বিদ্যায়তনের কাজ শুরু হয়। পরে তা ফিরিঙ্গি কমল বোসের বাড়িতে উঠে আসে। ১৮১৮ সালের ১৫ জুলাই তারিখে উইলিয়াম কেরি সাহেবের উদ্যোগে ও উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং জোশুয়া মার্শম্যানের সহযোগিতায় শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
এই সূত্রে আমরা লুই হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও ( ১৮.০৪.১৮০৯ – ২৮.১২.১৮৩১) কে স্মরণ করব। ডিরোজিও ছিলেন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কবি শিক্ষাবিদ ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি নজর কেড়েছিলেন। বালক বয়সেই তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে কবিতা লিখতে শুরু করেন। জন কীটস, পি বি শেলি, ও বায়রণের চিন্তাধারার প্রভাব তাঁর কবিকৃতিতে খুঁজে পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক জন গ্রাণ্ট ডিরোজিওর লিখনশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সহ সম্পাদক হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। ডিরোজিও তা স্বীকার করেন। পরে তিনি নিজেই ক্যালকাটা গেজেট নামে একটি পত্রিকা বের করেছেন।
মাত্র সতের বৎসর বয়সে ১৮২৬ সালের মে মাসে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের ইংরেজি ও ইতিহাস বিভাগে সহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। পাঠদানের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের সৌরভে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সহপ্রধান শিক্ষক পদে উন্নীত হন।
ছাত্রদের মধ্যে তাঁকে ঘিরে এক মহৎ উদ্দীপনা গড়ে ওঠে। ডিরোজিও ছাত্রদের মধ্যে জিজ্ঞাসা ও যুক্তিবোধির বীজ বপন করতে করতে ১৮২৮ সালে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে বিতর্ক সভা গড়ে তোলেন। জ্ঞানপিপাসা, যুক্তিবাদ, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণকে পুঁজি করে ডিরোজিওর ছাত্ররা কলকাতার বুকে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। এই ছাত্ররা ইয়ং বেঙ্গল নামে বিখ্যাত হন। রক্ষণশীল সমাজ ছেড়ে কথা বলে নি। অত্যন্ত গুণী ছাত্রদরদী ডিরোজিওকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছে। মাত্র বাইশ বছর বয়সে এই চিরস্মরণীয় চিরবরণীয় শিক্ষক কলেরায় ভুগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পর ছাত্রদের দিশা দেখাবার দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন আরেকজন শিক্ষানুরাগী মহাপ্রাণ ডেভিড হেয়ার।
খুব স্পষ্টতঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সমকালীন বাংলা তথা ভারতকে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। কোম্পানি আর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট অভিন্ন ছিল না। যদিও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির কাজের উপর নজর রাখত। কোম্পানির লক্ষ্য ছিল বাংলার মানুষের উপর শাসন চালিয়ে আর্থিক লাভের নিশ্চিতি বিধান করা। সেই কারণে তারা স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজপতিদের নিজেদের পক্ষে রাখার নীতি গ্রহণ করেন। ঠিক ওই কারণেই কোম্পানির পরিচালকগণ কেরিকে ধর্মপ্রচারকের কাজে বাধা সৃষ্টি করে শ্রীরামপুর কলেজ গড়ে তুলতে বাধ্য করেন। আবার ডিরোজিও হিন্দু সম্প্রদায়ের সমাজপতিদের বিরাগভাজন হলে ডিরোজিওকে সুরক্ষাদানে তাঁরা নিস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাব অবলম্বন করেন।
এই একই কারণে কোম্পানি চায় নি প্রথাগতভাবে চলে আসা শিক্ষা পদ্ধতিতে বদল করে আধুনিক যুগের উপযোগী জ্ঞান বিজ্ঞান গণিত ভূগোল জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির পাঠক্রম চালু হোক।
সংস্কৃত ও ফারসি, এই দুই ভাষায় প্রথাগত শিক্ষা চালু রাখার মধ্যেই কোম্পানি স্বস্তিবোধ করত। রক্ষণশীল প্রাচীনমনস্ক সনাতনী ভারতের কিছুমাত্র বিপক্ষতা করার আগ্রহ কোম্পানির পরিচালকদের ছিল না। তার সামান্য রদবদল হল গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ( ১৪.০৯.১৭৭৪ – ১৭.০৬.১৮৩৯) এর আমলে।
ভারতে শীর্ষ প্রশাসক তথা গভর্নর জেনারেল হিসেবে ০৪.০৭.১৮২৮ থেকে ২০.০৩.১৮৩৫ অবধি দায়িত্ব পালন করেছেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক । তিনি ক্ষমতায় আসার বৎসর খানেকের মধ্যেই বেঙ্গল সতী রেগুলেশন, ১৮২৯ জারি করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হয়।
ভারতে শীর্ষ প্রশাসক তথা গভর্নর জেনারেল হিসেবে ০৪.০৭.১৮২৮ থেকে ২০.০৩.১৮৩৫ অবধি দায়িত্ব পালন করেছেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক । তিনি ক্ষমতায় আসার বৎসর খানেকের মধ্যেই বেঙ্গল সতী রেগুলেশন, ১৮২৯ জারি করে সতীদাহ নিষিদ্ধ করা হয়। চার্লস মেটকাফ (৩০.০১.১৭৮৫ – ০৫.০৯১৮৪৬), পরবর্তীতে এক বৎসরের জন্য যিনি কাজ চালানো গভর্নর হয়েছিলেন, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন সতীদাহের বিরুদ্ধে কোম্পানি কথা বললে ভারতীয়গণ ভীষণ ভাবে বিরোধিতা করবেন।
০৪.১২. ১৮২৯ তারিখে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হলে রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থী ভারতীয় রা বেন্টিঙ্কের রেগুলেশনের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে মামলা দায়ের করেন। তবে সতীদাহের মতো বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে কাউন্সিল রায় দেন। প্রগতিশীল মানসিক গঠন সম্পন্ন উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আরো গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কাজ হল, নরবলি রদ, কন্যাভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ করা, এবং ঠগী দমন।
বেন্টিঙ্কের সময়ে, তাঁর শাসনের একেবারেই শেষের দিকে ১৮৩৫ সালের ২৮ জানুয়ারি তারিখে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল স্থাপিত হয়। আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যায় গোটা এশিয়া মহাদেশের প্রথম মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় পণ্ডিচেরীতে, কিন্তু ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা বিদ্যাদান শুরু হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। সাধারণ ভাবে কোম্পানি প্রশাসন এতদিন ধরে রক্ষণশীল গোঁড়াপন্থী ভারতীয়দের না চটাবার নীতি গ্রহণ করে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষে থাকলেও, উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই সুবিধাবাদী অবস্থান মেনে নেন নি। তাঁর শাসনকালের শেষ বৎসরে ১৮৩৫ সালে তিনি ইংলিশ এডুকেশন অ্যাক্ট চালু করেন। এই কাজে তাঁর খুব বড় সহায় ছিলেন আরেক জন উচ্চশ্রেণির প্রশাসক টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ( ২৫.১০.১৮০০ – ২৮.১২.১৮৫৯)।
মেকলে নিজের দেশে পার্লামেন্টে সদস্য ছিলেন। ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসবিদ স্কলার। ভারতে এসে তিনি কোম্পানির প্রশাসন চালনার উচ্চস্তরের সংস্থা বোর্ড অফ কন্ট্রোল এর সদস্য হন ও পরে এর সেক্রেটারি হন।
ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান সরকারের তরফে নীতি ও আইন হিসেবে গৃহীত হয়ে গেলে পড়াশুনা চর্চাভাবনা একটা সর্বভারতীয় চেহারা ও চারিত্র্য পেল।
এইপথে ১৭৫৭ তে ক্ষমতা দখলের পর ১৮৩৫ এ এসে ব্রিটিশ শাসকেরা আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন দেখাতে পারলেন। যাই হোক, যত দুর্বলতাই থাক, কোম্পানির শাসনেই আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার সুযোগ ভারতে তৈরি হয়। মানবিক মূল্যবোধ প্রশাসনের অন্যতম পালনীয় নীতি হিসেবে গ্রাহ্য হয়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সরকারি সমর্থন লাভ করায় ভারতীয় অভিজাত ও উচ্চবিত্ত অংশ বিদেশি জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন গণিতের সন্ধান পান। এঁরা অনেকেই বিদেশে পাড়ি দিয়ে পড়াশুনা করে ব্যারিস্টার হয়েছেন, আইসিএস হয়েছেন। এই পথে দেশীয় লোকেদের মধ্য থেকে এক ধরনের মানুষ তৈরি হয়েছে, যাঁরা পেশার প্রয়োজনে উকিল, ব্যারিস্টার, সিভিল সারভেন্ট হয়ে দেশের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং এরা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণে মতপ্রকাশের একটা সুচারু বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনে দাসত্বের গভীর তলে দাসত্বমুক্তির শর্ত হিসাবে শিক্ষা, মতবিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগের সাথে অতীত গৌরবের পুনরুজ্জীবন মিলেমিশে একটা নবীন জাতিগঠনের প্রক্রিয়া চলেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিপরীত বস্তুর সহাবস্থান বা ইউনিটি অফ অপোজিটস বলে ধারণা আছে। ইংরেজ শাসনে উপরে উপরে দাসত্বের কঠোর বন্ধনের নিচের তলায় দাসত্বমুক্তির আয়োজন তারই উদাহরণ বলে মনে করি।
একইসাথে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে শ্রদ্ধাপূর্ণ পড়াশুনা এবং আধুনিক শিক্ষার সুযোগ যাঁদের মধ্যে সঞ্জীবিত হয়েছিল, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন ভারতে মানবাধিকার এবং ইহমুখী পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি অচেনা ছিল। (তা থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা, এই ধারণাগুলি ইতিহাসের একটা পর্যায়ে গড়ে উঠেছে। ) বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সীতার বনবাস এবং শকুন্তলা গ্রন্থে পাঠকের হৃদয়ে পরিচিত কাহিনির অনুষঙ্গে নারীজীবনের প্রতি সহমর্মিতা গড়ে তুললেন। এ জিনিস প্রাচীনকালে অজানা ছিল।
সে যুগের রাজা তার প্রজাদের কাছে ভাল সাজতে চেয়ে গর্ভবতী বধূকে বনবাসে পাঠাতে পেরেছে। জুয়ায় হেরে গিয়ে কুলবধূকে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত হতে দিতে বাধা দেয় নি। বিবাহ করার পর পছন্দের নারীকেও ভুলে যেতে অসুবিধা বোধ করে নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গল্প কাঠামো ব্যবহার করে তাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বীজ বপন করলেন। সীতার আহত মন, শকুন্তলার প্রতারিত হওয়া পাঠকের মনকে ছুঁয়ে গেল। আগেও তো রামায়ণ পড়া হয়েছে। গানে কথকতায় রামকথা সাধারণ ভারতীয়ের কণ্ঠস্থ। বিদ্যাসাগরের লেখায় পাঠক একটু হলেও নাড়া খেল। সীতাকে গর্ভবতী অবস্থায় দূর করে দিয়েছিলেন রাম। গর্ভবতী শকুন্তলাকে আশ্রয়ভিক্ষা করতে দেখে উপহাস করেছিলেন দুষ্যন্ত।
দুর্বলকে রক্ষা করার দায় ছিল রাজার। যে রাজা সবলের অপরাধে দুর্বলকে নিপীড়ন করে, সে হেয়। আর যে রাজা নিজে সহজ সরল আশ্রমবালিকাকে নিয়ে যৌনতার খেলা খেলে তাকে ভুলে যেতে চায়, সে রাজা হলেও আসলে শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের কলমে রামায়ণী কথা আরো বড় রকম বাঁক নিল। সেখানে ইন্দ্রজিৎ দেশপ্রেমিক মহানায়ক, লক্ষ্মণ কুচক্রী অনুপ্রবেশকারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কর্ণকুন্তী সংবাদে কর্ণের অত্যুচ্চ মহত্ত্বপরায়ণ ছবি আঁকলেন। গান্ধারীর আবেদনেও অন্য মাত্রা আনলেন। এ সবই রামায়ণ মহাভারত থেকে নেওয়া চরিত্রগুলির নবনির্মাণ।
কিন্তু এই নির্মাণে রইল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবজনিত মূল্যবোধের স্পর্শ। মনে রাখা দরকার উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আগে কোনো গভর্নর জেনারেল একসাথে সতীদাহ, কন্যাভ্রূণ হত্যা, নরবলি, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা আর মেডিক্যাল কলেজের ভাবনা বাস্তবায়িত করে উঠতে পারেন নি। তিনিই পশ্চাৎপদ চূড়ামণি হিন্দু রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহস করলেন। রামমোহন বিদ্যাসাগরকে এক এক পা অগ্রসর হতে গিয়ে হিন্দু সমাজপতিদের গোঁড়ামির ভয়ঙ্কর আঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে।
কোম্পানির শীর্ষ পর্যায়ের নেতৃত্বের কার্যকরী সমর্থন থাকায় গোঁড়াদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া গেল। কোম্পানি প্রশাসন সদর্থক ও গঠনমূলক ভূমিকা নিতেই সুফল ফলতে লাগল। যুগের দাবিকে বাস্তবায়িত করা সহজ হল। তাই সমাজকে পরিশুদ্ধ করতে শাসকের তরফে শুদ্ধ ও সদর্থক ভূমিকা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতার সূত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতাবিন্যাস, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা, ও ন্যায়বিচার, যা ছিল যুগের দাবি, তাকে কবিতায় চিত্রায়িত করার চেষ্টা নিয়ে লিখতে চাইছি।
১
সামান্য ক্ষতি
নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক রাজশাসন বলতে ঠিক কি বোঝায়, “সামান্য ক্ষতি” কবিতায় তা নিয়ে ইঙ্গিত দেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ২৫ আশ্বিন তিনি কবিতাটি লিখেছেন। কাশীরাজের রাণী করুণা সখীদলবল সমভিব্যাহারে বরুণা নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেই স্নানের সময় যাতে রাণী ও তাঁর সঙ্গিনীদের আব্রু ও সম্ভ্রম কোনোভাবেই না বিপন্ন হয়, সেজন্য বরুণা নদীতীরবাসী নাগরিকদের সকাল বেলার জন্য এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র থাকতে বলা হয়েছিল। একজন রাণীর আব্রু রক্ষা র দায় তাঁর পরিচারিকাদের। কিন্তু সেজন্য সাধারণ মানুষকে নিজের নিজের কুটির ছেড়ে দূরে সরে থাকতে হল। প্রজাদের এইটুকু বিড়ম্বনায় ফেলেই রাণী করুণা সন্তুষ্ট থাকতে চাইলেন না।
স্নানের পর তিনি গা হাত পা সেঁকবেন বলে আগুন চাইলেন। কাঠকুটো যোগাড়ের চাইতে একটা কুটিরে আগুন লাগানো সুবিবেচনার পরিচয় মনে হল রাণীর। কুটিরে আগুন লাগানোর প্রস্তাবের বিপক্ষে একটি পরিচারিকা বক্তব্য রেখেছিল। কিন্তু তার যুক্তিপূর্ণ মানবিক আবেদন রক্ষিত হয় নি। বরং তাকে রাণী কটু মন্তব্যে বিঁধেছিলেন।
যাইহোক, একটি কুটিরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলে খানিকটা সময় পরে “গোটা গ্রামখানি লেহিয়া লইল প্রলয়লোলুপ রসনা”।
গৃহহারা বিপন্ন প্রজারা রাজসকাশে গিয়ে এহেন কুকর্মের বিরুদ্ধে সুবিচার চেয়েছিল।
রাণী স্নানলীলা সেরে ফিরলে সর্বসমক্ষে তাঁকে ডাকিয়ে আগুন লাগানোর কৈফিয়ত তলব করেছিলেন রাজা। রাজা জানতে চেয়েছিলেন, এরকম ব্যবহার তিনি করলেন কেন। দম্ভ ভরে রাণী বলেছিলেন, গরিবের প্রাণের ও সম্পত্তির কোনো মূল্য আছে বলেই মনে করেন না তিনি। অহমিকায় স্ফীত হয়ে রাণী আরো বললেন, রাজমহিষীর প্রমোদের পক্ষে এই গ্রাম ধ্বংসের মূল্য যৎসামান্য। রাণীর এই প্রগলভতায় রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দণ্ড দিলেন জীর্ণ ছিন্ন বসন পরে ঘরে ঘরে ঘুরে ভিক্ষা করে রাণীকে এই ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করে দিতে হবে। সময়সীমা দিলেন একবৎসর। রাজপরিবারের সদস্য বা ক্ষমতাবৃত্তে থাকা মানুষজনের সঙ্গে নিম্নকোটির জনগণের আদর্শ সম্পর্কবিন্যাসটি কি, তা স্পষ্ট করেন কবি। আজকের পৃথিবীতে উন্নয়নের নাম করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও সংখ্যালঘুকে উচ্ছেদ একটা বাস্তব ঘটনা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইনের চোখে সকলের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে এবং দরিদ্র মানুষের সম্পত্তি রক্ষা, ও বিপর্যয় মোকাবিলায় ত্রাণ দেওয়া রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে নির্দেশ করে। কথা ও কাহিনীর নানা কবিতায় এইভাবে রাষ্ট্রনীতি ও জনপ্রশাসনের ভারসাম্যমূলক পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরতে থাকেন।