রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প
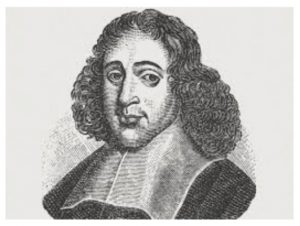
প্রবীণ বয়সে সত্তর পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব ইচ্ছে গেল বিজ্ঞান বিষয়ক বই লিখবেন। বিজ্ঞান নিয়ে প্রথাগত পড়াশুনা তো করেন নি। অথচ জগদীশচন্দ্র বসুর মতো আন্তর্জাতিক মাপের পদার্থবিজ্ঞানীর সঙ্গে খুব হৃদ্যতা ছিল। তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। নোবেল পুরস্কার পাবার খবর এলে শান্তিনিকেতনে বসু তাঁর সম্মানসভায় সভামুখ্য হয়েছিলেন। তাছাড়া কলকাতার রাজাবাজারে বসুর বাড়িতে নিবেদিতা তিনি আর বসু মিলে কত আড্ডা মেরেছেন। কাছের মানুষ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। তিনিও গোড়ায় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। পরে রাশিবিজ্ঞানে আগ্রহ গেল প্রশান্তর। প্রশান্ত তাঁর লেখাগুলি গুছিয়ে তুলতে বৈজ্ঞানিক পন্থা নিয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে বই লেখাটা একটু শক্ত। তাই দায়িত্ব দিলেন অধ্যাপক প্রমথ সেনগুপ্তকে। বুঝিয়েও দিলেন ঠিক কী জিনিস তিনি চাইছেন। প্রমথ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র। ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ অসাধারণ গবেষণা করে আইনস্টাইনের কাছের মানুষ হয়েছেন। গণিতবিদ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কবির ভাল সম্পর্ক। তিনি কবিকে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ানোর আয়োজন করেছিলেন। তবু বিজ্ঞানের বই লেখার দায়িত্ব দিলেন প্রমথকেই। তারপর সেই খসড়া বই নিয়ে আরো কষা মাজা করে বিশ্বপরিচয়। প্রুফ যিনি দেখলেন, তিনিও বিজ্ঞানের মানুষ। রাজশেখর বসু। কবি চেয়েছিলেন আদরের সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্ব পরিচয় একটু দেখে শুনে দেবেন। সে আর হল না। সত্যেন্দ্রনাথ গভীরভাবে গবেষণায় নিমগ্ন। তবুও কবি তাঁকেই বিশ্বপরিচয় উৎসর্গ করলেন। বিশ্ব পরিচয়ের খসড়া প্রমথ তৈরি করে দেবার পর তিনি সেটা তন্ন তন্ন করে পড়ে বুঝে ভাষাকে গড়ে তুলেছিলেন। চটপট এডিশন হল বইটির। এডিশন তৈরির সময়েও আরো পড়াশুনা করে নিলেন। এইসব সময়ে আর সাহিত্যের বই বিশেষ পড়তে চাইতেন না। বিজ্ঞান বিষয়ক ভাল বইতে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। মহাকাশ বিজ্ঞান আর পরমাণু বিজ্ঞান বিশেষ করে। বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহের ছাপ পড়ে গেল অনেকগুলো কবিতায়। আর সে গল্পে। গ্যেটে ছিলেন নিজস্ব ক্ষমতায় সাহিত্যিক এবং বিজ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানপিপাসু সাহিত্যিক।
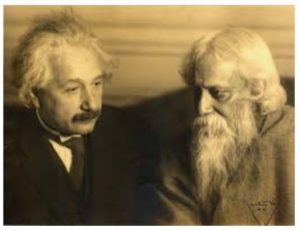
রবীন্দ্রনাথ নৈবেদ্যের কবিতায় লিখেছিলেন:
‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়–
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করে নি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা–
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।”
(কাব্যগ্রন্থ: নৈবেদ্য, প্রকাশ : বঙ্গাব্দ ১৩০৮, আষাঢ়।)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী নাটকে মহৎ উদ্দেশ্যে মুক্তিসংগ্রামীর আত্মবলিদানের কথা আছে। এই রক্তকরবী নাটক যে সময় গড়ে উঠছে, সেই সময়ে আমেরিকার সোশ্যালিস্ট ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার ( ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ – ২৫ নভেম্বর ১৯৬৮) এর কাছ থেকে কিছু বই উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ০৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন সিনক্লেয়ারের দি ব্রাস চেক গ্রন্থটি তিনি পড়েছেন। বলা দরকার, বহু গ্রন্থের রচয়িতা আপটন সিনক্লেয়ারের এই বইটি ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এই বইতে আমেরিকার মেনস্ট্রিম সাংবাদিকতার ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি তুলে ধরেছিলেন। আমেরিকায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জিনিসটা আসলে যে কী, তার মুখোশ খুলতে তিনি কড়া চাবুক ব্যবহার করেছিলেন। সিনক্লেয়ার নিজেই বলেছেন আমার দি ব্রাস চেক আমার লেখাগুলির মধ্যে মোস্ট ইমপরট্যান্ট আর মোস্ট ডেনজারাস। লক্ষ করি যে সিনক্লেয়ার তাঁর “দি ব্রাস চেক” বইতে আমেরিকান মেনস্ট্রিম সাংবাদিকদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তুলোধোনা করার বছর চারেক পর সেদেশে সাংবাদিকদের “কোড অফ এথিকস” প্রণীত হয়।
১৯২৩ এর ওই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সিনক্লেয়ারকে লিখেছিলেন: the ideas which you inculcated in this particular book immediately made a bond of sympathy. For years I have thought over these things, this especial phase of our modern civilization and only a few weeks ago I have myself finished a drama on the same subject. It will be published shortly in
English and I shall hope to have the pleasure of sending you a copy.
১৯৪৩ সালে সিনক্লেয়ার পুলিৎজার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।
রক্তকরবী নাটকের সঙ্গে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ জড়িয়ে রয়েছে। তিনি আমেরিকা থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন: “ছবিটা ভাল করে দেখ্ – কেরোসিন তেলের অন্ধকূপ – এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠচে ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরদের এই দশা – এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সূর্যের আলো এদের মানস চক্ষে পৌঁছায় না। বলি রাজা পাতালপুরীর রাজা – তার বল হরণ করেছিলেন বামন অবতার। বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেচে। যারা এতকাল ছোট হয়ে ছিল, তারাই বড়র ধন হরণ করবার জন্যে হাত বাড়িয়েচে – বড় ভয়ে কম্পান্বিত, চারদিকে দুর্গপ্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুলচে – কিন্তু দৈত্যভায়ার পাপের ধন আর টিঁকবে না।”
রক্তকরবী নাটকটি যখন শিলঙে লেখা চলছে, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন লেনার্ড কে এলমহার্স্ট। রাণু অধিকারীও ছিলেন। রক্তকরবী নাটকের যে জায়গাগুলিতে বিশেষ ভাবে দেখাতে চাইছি সেগুলি হল:
সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।
“নন্দিনী।
পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে?”
সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।……
….
নেপথ্যে।
সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত। …..
….
নেপথ্যে।
সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।…….
১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ১২ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর ১৯২৬) বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে রক্তকরবী প্রকাশ করেন জগদানন্দ রায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনেক আগে সম্পূর্ণ নাটকটি মুদ্রিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩১ সংখ্যায়। বাংলা বইটি প্রকাশের আগেই ১৯২৪ সালে বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি পত্রিকার ভলিউম ২ নং ২ সংখ্যায় নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং পরে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে যায়। নাটকটি গড়ে ওঠার সময় ০৯ জুন ১৯২৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথের কলমে পাওয়া যায় :
“জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।” এই অংশটি পূরবী কাব্যগ্রন্থে সংকলিত “শিলঙের চিঠি” কবিতায় রয়েছে।
শিলঙে নাটকটি লেখার পর রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনা গিয়েছিলেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন লেনার্ড কে এলমহার্স্ট। আর্জেন্টিনায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ এলমহার্স্টকে রক্তকরবী নাটকের সারবস্তু বুঝিয়ে বলেন। আলাপের সময়টা ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর ডিসেম্বর। কবির গুণমুগ্ধ এলমহার্স্ট রবীন্দ্রকৃত সে আলাপচারিতার লিখিত রূপ Red Oleanders: An Interpretation নামে প্রকাশ করেন। দীর্ঘ রচনাটির এক জায়গায় কবি বলছেন:
Into a loveless world, a world where men have ceased ever to be civil, a world of “foreign investment”, comes Nandini, the embodiment of that light that is beauty and love. She represents the highest truth in the human world, in the nature of man, a truth for which all down the ages, the great have lived, suffered and even died. She too is willing to suffer torture, a death, a mental crucifixion. In losing her lover and her own life she loses her all to save all, the truth of love, for humanity.
মানুষের সর্বপ্রকার মুক্তির সূত্রে আমরা ইংরেজ কবি জন মিল্টন ( ০৯ ডিসেম্বর ১৬০৮ – ০৮ নভেম্বর ১৬৭৪) কে স্মরণ করতে পারি। তিনি প্যারাডাইস লস্ট (১৬৬৭) নামে এপিক লেখার জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তাঁর আরো একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল অ্যারিওপ্যাগিটিকা ( প্রকাশ ২৩ নভেম্বর ১৬৪৪)। মাত্র ত্রিশ পৃষ্ঠার অ্যারিওপ্যাগিটিকা ধ্রুপদী ওজস্বী গদ্যরীতিতে লেখা একটি বিতর্ক মূলক অভিভাষণ। এটি সমসময়ের ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের কাছে পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে যে কোনো নিষেধাজ্ঞা ও কণ্ঠরোধ প্রত্যাহারের দাবিপত্র বিশেষ। কিন্তু অ্যারিওপ্যাগিটিকা সমসাময়িকতা ও স্থানিকতার গণ্ডী ডিঙিয়ে সর্বদেশের সর্বকালের মুক্ত মানবাত্মার বাণী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রকাশের পর একশো বছর অবধি সেভাবে গুরুত্ব না পেলেও পরবর্তীকালে বিদগ্ধ মানুষেরা অ্যারিওপ্যাগিটিকার তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হন। প্রকাশের তিনশো বছরের প্রাক্কালে অ্যারিওপ্যাগিটিকা মুক্তিকামী মানুষের নয়নের মণি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অ্যারিওপ্যাগিটিকার মহত্ত্ব বিষয়ে সচেতন ছিলেন। শেষ জীবনে লেখা সে গল্পে তিনি এই অসামান্য পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন।
মিল্টনের জীবৎকালেই বেঁচে ছিলেন দুই উল্লেখযোগ্য গুণী মানুষ। একজন হলেন ফরাসি চিন্তাবিদ রেনে দেকার্তে ( ৩১ মার্চ ১৫৯৬ – ১১ ফেব্রুয়ারি ১৬৫০) এবং আরেকজন ছিলেন ডাচ চিন্তাবিদ বারুখ স্পিনোজা ( ২৪ নভেম্বর ১৬৩২ – ২১ ফেব্রুয়ারি ১৬৭৭)। রেনে দেকার্তেকে সভ্য মানুষ আধুনিক দর্শনভাবনার অন্যতম পথিকৃৎ ও প্রতিষ্ঠাতা বলে জানেন। ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি রুলস ফর দি ডাইরেকশন অফ মাইন্ড নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এর পরে ১৬৩০ – ৩১ এ দি সার্চ ফর ট্রুথ, ১৬৩০ – ১৬৩৩ এ দ্য ওয়ার্ল্ড, ১৬৩৭ এ ডিসকোরস অফ মেথড, ১৬৪১ সালে মেডিটেশনস, ১৬৪৪ সালে প্রিন্সিপলস অফ ফিলজফি, এবং ১৬৪৯ সালে প্যাশনস অফ দি সোল ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।
রেনে দেকার্তে তাঁর ডিসকোরস অফ মেথড বইতে বলেছিলেন, আমি চিন্তা করতে পারি, এতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, আমি আছি। আই থিঙ্ক, দেয়ারফোর আই অ্যাম। লাতিন ভাষায় তাঁর কথাটা ছিল, কজিতো এরগো সাম। তিনি আরো বলেছিলেন, যেহেতু আমরা মানুষেরা সীমাবদ্ধ, সে কারণে আমরা অনন্ত কী তা বুঝতে পারি না। তবুও যে আমরা অসীম ঈশ্বরের ধারণা করতে পারি, তার কারণ হল, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে সেই ধারণাশক্তিটি জুগিয়ে দিয়েছেন। এই শক্তিটি তিনি জুগিয়ে দিয়েছেন বলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। দেকার্তে আরো বলেছিলেন, আমরা কখনোই বস্তু জগৎকে নিজস্ব ক্ষমতায় জেনে উঠতে পারি না।
ওঁর চিন্তাপদ্ধতি আরিস্ততলের অভিজ্ঞতাবাদের থেকে অন্যরকম। এক অর্থে যুক্তিবাদী ও বলা হয়। দেকার্তের ভাবনা পদ্ধতিকে কার্তেসীয় চিন্তাপদ্ধতি বলে।
বারুখ স্পিনোজা আবার প্রকৃতিকেই ঈশ্বর বললেন।
১৬৬০ সালে স্পিনোজা লিখলেন এ শর্ট ট্রিটিজ অন গড ম্যান অ্যাণ্ড হিজ ওয়েল বিয়িং। ১৬৬২ তে অধ দি ইমপ্রুভমেন্ট অফ দি আণ্ডারস্ট্যান্ডিং, ১৬৬৩ সালে দি প্রিনসিপলস অফ কার্তেসিয়ান ফিলজফি, ১৬৭০ সালে এ থিওলজিক্যাল পলিটিক্যাল ট্রিটিজ, আর ১৬৭৭ এ দি এথিকস নামে বই লিখলেন।
স্পিনোজা হিব্রু বাইবেলের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। সমসময়ে তাঁর তোলা প্রশ্ন সমাজকে তোলপাড় করে দিল। তিনি দৈবী বিষয়ের প্রকৃতি নিয়েও বিতর্কিত মতপোষণ করতেন। ইহুদি ধর্মনেতাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁরা স্পিনোজার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলেন। স্পিনোজাকে মাত্র তেইশ বছর বয়সেই সমাজচ্যুত করা হল। কেউ তাঁকে পছন্দ করত না। কেউ সম্পর্কটুকু রাখত না। এমনকি তাঁর পৈতৃক পরিবার পর্যন্ত তাঁকে দূর করে দিয়েছিল। শেষমেশ স্পিনোজার বইগুলি ক্যাথলিক চার্চ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল।
যদিও কোথাও, কোনো রচনাতেই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করেন নি, বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানান নি, তবুও সমসাময়িক লোকজন স্পিনোজাকে নাস্তিক বলত।
অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও মেধাবী ব্যক্তি হয়েও তিনি অতি সামান্য লোকের মতো দিনযাপন করতেন। পেশা হিসাবে কাচের লেন্স ঘসার কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখে স্বাধীনভাবে চিন্তা ভাবনা করতেন। সমসময়ের গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতির্বিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অণুবীক্ষণ ও দুরবিনের লেন্স ও তার ডিজাইন নিয়ে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হত। স্পিনোজা অনেক দূর অবধি দেখার উপযুক্ত দুরবিনের কথা ভাবতেন। তিনি কখনোই উপহার ও সম্মান গ্রহণে রাজি হতেন না। সম্মানিত করার যে কোনো প্রস্তাবকে তিনি পাশ কাটিয়ে যেতেন। নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার প্রস্তাবও তিনি অক্লেশে বর্জন করতেন। স্পিনোজার উচ্চতর জ্ঞানচর্চার সামর্থ্য দেখে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দর্শনের বিশিষ্ট অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ করতে চায়। স্পিনোজা এ প্রস্তাবটিও নাকচ করে দেন। তিনি বলতেন, এইসব বড় জায়গায় যোগাযোগ রাখলে তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।
এক দুর্মর আশাবাদের কবি পার্সি বিশি শেলি (০৪.০৮.১৭৯২ – ০৮.০৭. ১৮২২)। তিনি বলেন, “হে বাতাস, শীত যদি আসেই, তাহলে কি বসন্ত আসতে আর দেরি থাকে?” আবার বলেন, “আমাদের সবচেয়ে বিষণ্ণতার চিন্তাগুলোই মধুরতম গান হয়ে ওঠে।” কবিতাকে তিনি “বিদ্যুতের তরবারি” বলে মনে করেন। কবিতা যেন সেই নাঙ্গা তলোয়ার, যা এ জগতে সমস্ত অন্যায়, বঞ্চনা আর অসাম্যকে খান খান করে দেবে। আর বলেন, “কবিরাই এ জগতের বিধান রচনা করেন। অস্বীকার করেও তাঁদের এড়ানো যায় না।”
জীবৎকাল ত্রিশ বছর পেরোয় নি শেলির। কিন্তু গোটা জীবন ধরেই তিনি বিদ্রোহের কথাই বলে গেলেন। ভয়ঙ্করভাবে স্থিতাবস্থার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন শেলি। রাজা রাজড়াকে মোটেই পাত্তা দিতে চাইতেন না। যেন বলতে চাইতেন, ‘আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ’। জাঁ জাক রুশোর বৈপ্লবিক ভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। শেলি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। শেলি দেখেছিলেন তাঁর সময়ে তাঁর স্বদেশ ইংল্যাণ্ডে মিশরের ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের স্ট্যাচুর একটি খণ্ড আনা হয়েছিল। ফ্যারাওয়ের এই ভগ্ন মূর্তিটি দেখে শেলির মনে হয়েছিল পৃথিবীর বড় বড় শাসকেরা ওইরকম। ঠিক যেমন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন, ‘রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি/ শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি’, তেমনি করে ‘ওজিম্যানডিয়াস’ কবিতায় শেলি লক্ষ করেন মহাকালের সম্মার্জনীর ধাক্কায় এক সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত ফ্যারাও ভয়ে মুহ্যমান। তিনি আরো লক্ষ করেন, ধর্ম আর স্বার্থপরতা যেন দুই সহোদরা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও লক্ষ করেন, যারাই মানুষকে পায়ের নিচে রাখতে চেয়েছে, তারা ধর্মমোহকে অস্ত্র করেছে।
কৈশোর পুরোপুরি শেষ হবার আগেই নাস্তিক্যবাদে দৃপ্ত হয়ে উঠেছিলেন শেলি। ১৮১১ সালে, বয়স তখন ঊনিশ পেরোয় নি, তখনই শেলি একটি বই লেখেন, দি নেসেসিটি অফ এথেইজম বা নাস্তিক্যবাদের প্রয়োজনীয়তা। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ অথবা ১৪ তারিখ এটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হবার পর, শেলি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊনিশ বছর বয়সের ছাত্রটি বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপকদের কাছে পুস্তিকাটি পাঠান। অক্সফোর্ড কর্তৃপক্ষ শেলির এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ভীষণ ভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে কলেজ থেকে বিতাড়িত করেন। শেলি ঘোষিতভাবেই নাস্তিক ছিলেন। তিনি বলতেন, ধর্ম সামাজিক শোষণ শাসনকে দীর্ঘায়িত করে। ওই যে তিনি পুরোহিততন্ত্র, খ্রীস্টানী ভাবধারা আর ধর্মকে আক্রমণ করেছিলেন, তার জন্য ১৮২১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অবশ্য এরপর বেশিদিন বাঁচেননি শেলি। ১৮২২ এ প্রয়াণ। আমরা মহাকবি শেলিকে গভীর শ্রদ্ধায় আজ স্মরণ করব, কেননা, ২১০ বছর আগে এমন একটা ২৫ মার্চ শেলিকে পুস্তিকা লিখে নাস্তিক্যবাদ প্রচারের অভিযোগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করা হয়।
আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের “প্রশ্ন” কবিতায় ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন যারা পরিবেশ দূষণ করছে, সংস্কৃতিকে আক্রমণ করছে, বিচার ব্যবস্থাকে প্রহসনে পর্যবসিত করছে, তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করছে, অশেষ ক্ষমাশীল তিনি তাদেরকেও ক্ষমা করেছেন কি না।
কিন্তু কবিতাটি আগাপাশতলা খুঁটিয়ে পড়লে বেশ বোঝা যায় কবি চান না, ভগবান ওদের ক্ষমা করুন। অথচ চালু অর্থে যারা ভক্ত, তারা জানেন ঈশ্বরের সকল কাজ মানুষের প্রশ্নের অতীত। এই চালু অভ্যাসটাকে আঘাত করেই কবি প্রশ্ন করছেন, তুমি কি বেসেছ ভাল? ভাবখানা যেন এই, তুমি যদি বেসেও থাকো, সে কাজটা ভালো করো নি। ঈশ্বরের দৈবী মাহাত্ম্যটাকেই প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন কবি, আর বললেন মানুষী যুক্তিবিচারের কাছে কৈফিয়ত দেবার দায় স্বয়ং ঈশ্বর পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন না। “ধর্মমোহ” কবিতায় কবি এমন কি নাস্তিকের গুণগান পর্যন্ত করেছেন।
আবার শেলির কথায় ফিরি। মহাকবি পি বি শেলি’র কবিতা আবার প্রকাশকেরা ছাপাতেই সাহস করতেন না। কেননা, তাঁরা আশঙ্কা করতেন শেলির লেখায় ঈশ্বরের মহানুভবতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে ও রাষ্ট্রের সর্বাত্মক কর্তৃত্বকে প্রশ্নের সামনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।
প্রকাশকদের আশঙ্কাকে অমূলক বলে লাভ নেই। কেননা, শেলি, ১৮১১ সালে বছর ঊনিশের কৈশোর ছাড়ানো সদ্যোতরুণটি, লিখেছেন দি নেসেসিটি অফ এথেইজ়ম। ১৮১২ তে লিখেছেন ডিক্লারেশন অফ রাইটস, ১৮১৫ তে লিখেছেন অন এ ফিউচার স্টেট। রাষ্ট্র ও তার বিচারব্যবস্থা প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের যৌক্তিকতা ন্যায়গ্রাহ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলে ধরেন শেলি। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে শেলি কি চোখে দেখতেন, তা তাঁর এই কবিতায় প্রতিভাত :
ENGLAND IN 1819
An old, mad, blind, despised, and dying king,–
Princes, the dregs of their dull race, who flow
Through public scorn, mud from a muddy spring,–
Rulers who neither see, nor feel, nor know,
But leech-like to their fainting country cling,
Till they drop, blind in blood, without a blow,–
A people starved and stabbed in the untilled field,–
An army which liberticide and prey
Makes as a two-edged sword to all who wield,–
Golden and sanguine laws which tempt and slay;
Religion Christless, Godless, a book sealed,–
A Senate—Time’s worst statute unrepealed,–
Are graves from which a glorious Phantom may
Burst to illumine our tempestuous day.
কবিতা লিখে শেলি বিশ্বসেরা। ১৮১৯ এ লিখেছেন ওড টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড, ১৮২০ তে যথাক্রমে প্রমিথিউস আনবাউণ্ড, টু এ স্কাই লার্ক, আর দি ক্লাউড।
তাঁর কবিতা প্রভাবিত করেছিল মহান দার্শনিকদের। কার্ল মার্ক্স, বার্ট্রান্ড রাসেল, মহাত্মা গান্ধী যাঁদের অন্যতম। লেখকদের মধ্যে বিশ্ববরেণ্য লিও টলস্টয়, বার্নার্ড শ, অস্কার ওয়াইল্ড এর রচনায় শেলির ভাবনার স্পষ্ট ছাপ আছে।
শেলি তাঁর গদ্য রচনায় জগৎ জীবন, রাষ্ট্রের একতিয়ার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখায় প্লেটো, ফ্রান্সিস বেকন, জাঁ জাক রুশো ও নেপোলিয়নের কথা এসেছে। তীব্র রোমান্টিক এই কবি আশাবাদীও। তিনি বলেন If winter comes, can spring be far behind? এক আলোকময় জগতে উত্তরণের কথা বলেন শেলি, যার চাবিকাঠি রয়েছে মুক্তিপিপাসু মানুষের হাতে।
অসাধারণ মানুষ ছিলেন রম্যাঁ রলাঁ ( ২৯ জানুয়ারি ১৮৬৬ – ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৪)। এই ফরাসি নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক তাঁর সমুচ্চ আদর্শবাদ এবং সত্যের প্রতি সুগভীর আগ্রহ ও ভালবাসার জন্য ১৯১৫ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। সে সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ১৯১৪ সালের ২৯ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। শেষ হল ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর তারিখে। আর ১৯১৯ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে রম্যাঁ রলাঁ বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বের শুভচিন্তক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত করে তুলতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিশ্বশান্তির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে আহ্বান জানান।
এই সময়েই ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ তারিখে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা ঘটানো হল।
এই সময় সদ্য শেষ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজ জয়ী পক্ষে। এর মধ্যেই রাশিয়ার বুকে শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের ঐক্যে বিপ্লব হয়েছে ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ তথা লেনিনের নেতৃত্বে। তার প্রভাবে দেশে দেশে মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছে। গলা তুলছে শাসন শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে।
১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই থেকে ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর অবধি, চার বছর তিন মাস দুই সপ্তাহ জুড়ে চলা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ টের পেয়ে গেছে ভারতে মানুষ আরো বেশি বেশি করে জাগছে। আর তাই যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেই ১৯১৫ সালে ভারতে ব্রিটিশ আনল ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট। আনল কঠোর দমননীতি। যুদ্ধ শেষে ১৯১৯ সালে ওই ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টকে আরো কড়া করে চুঁইয়ে নতুন বোতলে এল অ্যানার্কিক্যাল অ্যাণ্ড রেভলিউশনারি ক্রাইমস অ্যাক্ট, ১৯১৯। এই আইনকে লোকে চিনল রাউলাট অ্যাক্ট হিসেবে। কেননা, এই আইন আনার আগে নিয়ম মান্য করে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল, যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন সিডনি রাউলাট। কী বলা হল এই অ্যানার্কিক্যাল অ্যাণ্ড রেভলিউশনারি ক্রাইমস অ্যাক্ট তথা রাউলাট অ্যাক্টে?
এই আইন কোনো কারণ না দেখিয়ে যে কোনো ভারতীয় ব্যক্তিকে অ্যারেস্ট করার আইনি একতিয়ার দিল পুলিশকে।
১৯১৯ সালের মার্চ মাসের আঠারো তারিখে দিল্লির ইমপিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এ আইনটি পাশ হয়ে গেল। পুলিশ এই আইনের বলে যাকে খুশি, যখন খুশি, কোনো কারণ না দেখিয়ে, বিনা বিচারে আটক করার সুযোগ পেয়ে গেল।
সভ্য সমাজ এ ধরনের আইনকে বলে ড্রাকোনিয়ান অ্যাক্ট। দানবিক আইন। কালা কানুন। ইংরেজের ভালমানুষি আসলে ঠিক কি, এই আইন চালু করে তারা তা টের পাইয়ে দিল। এহেন দানবিক আইনের বিরুদ্ধে গলা তুললেন মোহনদাস কর্মচন্দ গান্ধি, পেশায় যিনি ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনি এই আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। এই আইন চালু করার প্রতিবাদে ব্রিটিশ রাজকে ধিক্কার দিয়ে একুশে মার্চ, ১৯১৯ তারিখে দিল্লির ইমপিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মহম্মদ আলি জিন্নাহ্।
জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা দিকে দিকে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে নেমে পড়লেন। পঞ্জাবের মাটিতে ঝড় তুলতে চাইলেন চিকিৎসক রাজনৈতিক নেতা ডাক্তার সত্যপাল ( ১১.০৫.১৮৮৫ – ১৮.০৪. ১৯৫৪) এবং পঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা ব্যারিস্টার সৈফুদ্দিন কিচলু ( ১৫.০১.১৮৮৮ – ০৯.১০.১৯৬৩)।
পঞ্জাবি জনমনে ডাক্তার সত্যপাল ও ব্যারিস্টার সৈফুদ্দিন কিচলুর প্রভাবের কথা ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচররা জানত। ১৯১৯ এর মার্চের মাঝামাঝি থেকেই ওই দুই নেতার গতিবিধির উপর নজরদারি করছিল সিআইডি। আর তাক করছিলেন স্যর মাইকেল ও’ ডায়ার, আইরিশ আইসিএস, পঞ্জাব প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ( ১৯১৩ – ১৯১৯) পদে ক্ষমতাসীন প্রশাসক।
এপ্রিল মাসের দশ তারিখে ডাক্তার সত্যপাল আর ব্যারিস্টার সৈফুদ্দিন কিচলুর উপর ফরমান জারি করা হল যে তাঁদেরকে ডেপুটি কমিশনার মাইলস আরভিং সাহেবের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করতে হবে। ওইখানেই দুই নেতাকে আটক করে পঞ্জাব সরকার ধরমশালায় অন্তরীণ করে রাখলেন।
দুই জনপ্রিয় নেতার উপর এই অন্যায় আটকের বিরুদ্ধে পঞ্জাবি জনতা প্রতিবাদে গর্জে উঠল। শান্তিপূর্ণ পথে, অহিংস জনতা বৈশাখী মেলা উপলক্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ ময়দানে প্রতিবাদ সভায় জড়ো হল। প্রশাসন নজর রাখছিলেন। জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে আটকের বিরুদ্ধে জনতার শান্তিপূর্ণ সমাবেশকেও তাঁরা বাঁকা চোখে দেখলেন। জনতার নিরস্ত্র জোটবদ্ধতাকে ঔদ্ধত্য জ্ঞান করলেন মাইকেল ও’ডায়ার। সবক শেখানোর দরকার অনুভব করে অস্ত্রের ভাষায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যর মাইকেল ও’ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাবেশকে রুখতে অকল্পনীয় সাঁজোয়া ব্যবস্থা নিলেন। পঞ্চাশ ট্রুপ সেনা নামল। নাইনথ গুর্খা রাইফেলস এর গুর্খা ফার্স্ট ব্যাটালিয়নের পঁচিশজন গুর্খা সৈন্য, পঁচিশ জন পাঠান আর বালুচ সৈন্য, ৫৪ নং শিখ ও ৫৯ নং সিন্ধ রাইফেলস নামল বৈশাখী মেলা সমাবেশ রুখতে। প্রতিটি সেনানীর হাতে থ্রি নট থ্রি লী এনফিল্ড রাইফেল। চলল গুলি। যতক্ষণ না সঙ্গে আনা গুলিগোলা ফুরায়, গুলি বর্ষণ করার আদেশ হল। যে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে, তাকেও গুলি করতে হবে। যে মাটিতে পড়ে গিয়েছে, গুলিতে বিঁধতে হবে তাকেও। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন আরেক ডায়ার, কর্ণেল রেজিনাল্ড এডওয়ার্ড হ্যারি ডায়ার ( ০৯.১০.১৮৬৪ – ২৩.০৭.১৯২৩)। টেম্পোরারি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার।
আজ থেকে একশত দুই বৎসর আগে, ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র জনতার উপর যে নিষ্ঠুর আক্রমণ করেছিল ব্রিটিশ প্রশাসন, তার মূল কুশলী ও পরিকল্পনাকার ছিলেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যর মাইকেল ও’ডায়ার, আর যাঁর পরিচালনায় হত্যাকাণ্ডটি পরিচালিত হল, তিনি আরেক ডায়ার, কর্ণেল রেজিনাল্ড এডওয়ার্ড হ্যারি ডায়ার। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি দুজনেই ১৮৬৪ সালের জাতক।
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। সরকারপক্ষ খুব স্বাভাবিকভাবেই মৃত ও আহতের সংখ্যা স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকাশ করেন না। জালিয়ানওয়ালাবাগের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা ঘটেনি। তুলনায় অনেক বেশি নিরপেক্ষ হিসাব পাওয়া যায় ব্রিটিশ সার্জেন ডাঃ স্মিথের বর্ণনায়। তিনি বলেন মৃত ও সাংঘাতিক ভাবে আহতদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮০০ এর মতো।
জালিয়ানওয়ালাবাগ কাণ্ডে দেশে বিদেশে ধিক্কারের ঢেউ ওঠে। ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ব্রিটিশ শাসকের এহেন নখ দাঁত আস্ফালন আগে দেখেননি। তাঁরা কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। এমনকি আগুনখেকো নেতারাও গর্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাইশ মে তারিখে তিনি ঘটনাটি জানতে পেরে পরিচিত রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সমবেত প্রতিবাদের জন্য আবেদন করে ব্যর্থ হলে, একত্রিশ মে, ১৯১৯ তারিখে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে খোলা চিঠি পেশ করেন।
এই ১৯১৯ সালেই ২৪ জুন তারিখে রম্যাঁ রলাঁর আহ্বানের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখলেন:
When my mind was steeped in the gloom of the thought that the lesson of last war has been lost … Your letter came and cheered me up with the message of hope.
The truths that save us have always been uttered by the few and rejected by the many and have triumphed through their failures. It is enough for me to know that the higher conscience of Europe has been able to assert itself in the voice of one of her choicest spirits through the ugly clamours of passionate politics, and I gladly hasten to accept your invitation to join the ranks of those free souls who in Europe have conceived the project of a Declaration of Independence of the Spirit.
একটা অসাধারণ সম্পর্কে জড়ালেন দুজন অসাধারণ মানুষ। দুজনেই সাহিত্যে নোবেলজয়ী। পর পর নোবেল পেয়েছেন দুজনে। ১৯১৩ তে রবীন্দ্রনাথ আর ১৯১৫ তে রম্যাঁ রলাঁ। মাঝখানে ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার বিতরণ স্থগিত রাখা হয়েছিল।
১৯১৯ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চলবে এই সম্পর্ক। ৪৬টি চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের আদানপ্রদান হবে ওঁদের মধ্যে। এর আগেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনীষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রলাঁ। ১৯১৬ সাল। অল্পকিছু দিন আগেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রলাঁ। রবীন্দ্রনাথ তখন জাপানে। জুন ১৯১৬ তে টোকিওর ইমপিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতীয়তাবাদ নিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। আর সুদূর ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে বসে রলাঁ তাঁর বক্তব্য গভীর আগ্রহে নোট করছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা সম্বন্ধে রলাঁ তাঁর নোটবুকে লিখলেন: “turning point in the history of mankind” । রবীন্দ্রনাথকে রলাঁর মনে হল “burning flame of joy, which is always shrouded in a fog of melancholy in the West”.
রলাঁ ১৮৯৮ তে মরিস শোয়ার্জ এর সাথে মিলে লিখেছিলেন দি উলভস। ১৯৩২ সালে এই নাটকটি নিউ ইয়র্কে ঊনত্রিশবার মঞ্চাভিনীত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে রলাঁ লিখেছিলেন দি ট্রিয়াম্ফ অফ রীজন। ১৮৯৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম মহানায়ক জর্জেস দাঁতো-কে নিয়ে নাটক লিখেছিলেন। ১৯০২ তে ১৪ জুলাই বাস্তিল দিবস লিখেছেন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রবন্ধ লিখলেন দি পিপলস্ থিয়েটার। ১৯০৪ থেকে ১৯১২, এই সময়কাল ধরে লিখলেন জঁ ক্রিস্তফ। দশটি খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছিল উপন্যাসটি। সংগীত, কলাবিদ্যা, সাহিত্য, নারীবাদ, মিলিটারিজম, আরো নানা সামাজিক বিষয়ে নিজের বিপুল ভাবনাচিন্তা এই উপন্যাসে পেশ করেছিলেন তিনি। ১৯১১ থেকে ১৯১৩ র মধ্যে ইংরেজি ভাষায় জঁ ক্রিস্তফ এর অনুবাদ হয়। অনুবাদ করেছেন ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার গিলবার্ট কাননান ( ১৮৮৪ – ১৯৫৫)।
ইংরেজি অনুবাদে বিপুল সংখ্যক সাহিত্যানুরাগীর কাছে পৌঁছে যায় জঁ ক্রিস্তফ। এর দশটি খণ্ডের আলাদা আলাদা নাম রয়েছে। ১৯০৪ সালে লেখা হয়েছিল ডন, মর্নিং, এবং ইয়ুথ নামে তিনটি খণ্ড। ১৯০৫ এ লিখলেন রিভল্ট। ১৯০৮ এ দি মার্কেটপ্লেস, আঁতোয়ানেৎ, ও দি হাউস, ১৯১০ এ লাভ অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডশিপ, ১৯১১ তে দি বার্নিং বুশ, এবং শেষ খণ্ড দি নিউ ডন বেরিয়েছিল ১৯১২ সালে। জঁ ক্রিস্তফ রলাঁকে সাহিত্যমার্গে বিপুল পরিচিতি এনে দেয়। প্রথম কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ হতেই ফেমিনা পত্রিকার তরফে ১৯০৫ সালে পেয়েছিলেন প্রিক্স ফেমিনা পুরস্কার। ১৯১৩ তে ফরাসি সাহিত্য আকাদেমি থেকে পেয়েছেন গ্র্যাণ্ড প্রাইজ।


















