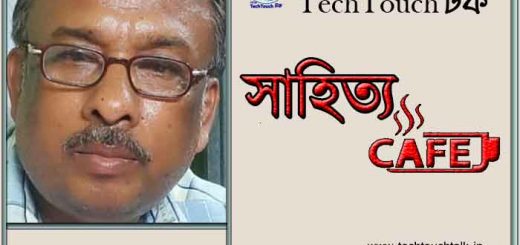ক্যাফে ধারাবাহিকে মৃদুল শ্রীমানী (পর্ব – ১৫)

অ্যাটমের গহন কথা

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জেমস জোসেফ টমসন তাঁর সহযোগী জন এস টাউনসেন্ড এবং এইচ এ উইলসনের সঙ্গে ক্যাথোড রশ্মি নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে লক্ষ্য করলেন, ক্যাথোড রশ্মি যেন তরঙ্গ নয়, তা যেন একটা অদ্ভুত ধরনের কণা। ক্যাথোড রশ্মির এই কণাস্রোতকে টমসন নজর করে তার কণার আধান এবং ভর নির্ধারণ করলেন। আর বললেন, এই কণাগুলি সবচাইতে ছোট আয়ন হাইড্রোজেনের হাজার ভাগের একভাগ।
টমসন আরো দেখালেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যা নির্গত হয়, এবং উত্তপ্ত বস্তু থেকে যা নির্গত হয়, এবং আলোকিত বস্তুর থেকে যা নির্গত হয়, তা প্রকৃতপক্ষে একই অভিন্ন জিনিস। তিনি এই কণাগুলির নাম দিলেন করপাসল। কিন্তু তাঁর দেওয়া ওই নাম টিঁকল না। বিজ্ঞানীগণ জি এফ ফিটজেরাল্ড, জে লারমর, এবং এইচ এ লোরেঞ্জ এই কণার নাম রাখলেন ইলেকট্রন। আবিষ্কারক টমসনের দেওয়া নাম করপাসলের বদলে এই ইলেকট্রন নামটাই বিজ্ঞানী সমাজে গৃহীত হল। ১৮৯৩ তে টমসন ইলেকট্রনের আধান এবং ভরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন। পরে, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট মিলিকান এবং হারভে ফ্লেচার আরো সূক্ষ্ম ভাবে ইলেকট্রনের আধান নির্ধারণ করেন।
গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নিয়ে গবেষণার স্বীকৃতি তে জে জে টমসন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে টমসনের সাথে ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করেছিলেন।
এর আগে লর্ড কেলভিন পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একভাবে ভেবেছিলেন। জে জে টমসন কেলভিনের ওই ধারণাটাকেই সকলের কাছে সুপরিচিত করেছিলেন। পরমাণুর গঠনের এই ধারণা প্লাম পুডিং মডেল হিসাবে বিখ্যাত ছিল। মনে করা হত যে, পুডিংয়ের দলার উপরে প্লাম ফল যেভাবে সাজানো থাকে, তেমনভাবে যেন পরমাণুর কেন্দ্রকের গায়ে ছোট ছোট ইলেকট্রন লেপ্টে আছে।
আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এই ধারণাটাকে বদলে দিতে চেয়ে বললেন, পরমাণুর কেন্দ্রে একটি অতি ক্ষুদ্র এলাকায় ধনাত্মক আধান নিয়ে অত্যন্ত ঘন অবস্থায় নিউক্লিয়াস রয়েছে, আর তার খানিকটা দূরে থেকে ইলেকট্রনগুলি সেই নিউক্লিয়াসকে পরিক্রমা করে চলেছে। যেভাবে সৌরমণ্ডলে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি প্রদক্ষিণ করে, রাদারফোর্ড পরমাণুর জন্য তেমন একটা মডেল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে খাড়া করলেন।
অত্যন্ত পাতলা সোনার পাতের উপর আলফা কণা দিয়ে আঘাত করে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং হান্স গিগার লক্ষ্য করেছিলেন, বেশিরভাগ আলফা কণা সোনার পাত ভেদ করে অক্লেশে চলে যায়, আর অল্পসংখ্যক আলফা কণা সামান্য এদিকে ওদিকে ঠিকরে যায়। আর অতীব অল্প সংখ্যক কণা ঠিকরে গিয়ে উৎসের দিকে ফিরে আসে। এথেকে রাদারফোর্ড ও গিগার ধারণা করলেন যে পরমাণুর অভ্যন্তরে বেশিরভাগ জায়গা একেবারেই ফাঁকা, এবং মাঝখানে অত্যল্প একটি পরিসরে অত্যন্ত ঘন অবস্থায় ধনাত্মক আধান নিয়ে কেন্দ্রক রয়েছে। এই কেন্দ্রককে ঘিরে অনেকখানি দূর দিয়ে ইলেকট্রন ঘুরছে।
প্লাম পুডিং মডেলকে সরিয়ে রাদারফোর্ডের মডেল পদার্থবিজ্ঞান জগতে জায়গা পেয়ে গেল। কিন্তু রাদারফোর্ডের মডেল খুব অল্পদিনের জন্যই টিঁকে ছিল। কেননা ডেনিশ পদার্থবিজ্ঞানী নিলস বোর পরমাণুর গঠনের ভিন্নতর ধারণা দিলেন।
রাদারফোর্ড ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পদার্থের ভাঙন বিষয়ে গবেষণার জন্য রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। রাদারফোর্ডের ছাত্র ছিলেন নিলস হেনরিক ডেভিড বোর। তিনি ধাতুর ইলেকট্রন তত্ত্ব নিয়ে পিএইচডি করেছিলেন। বোর ১৯১১র সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডে গিয়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে গিয়ে জেমস জোসেফ টমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং ক্যাথোড রশ্মি নিয়েও কিছুটা গবেষণা করেছিলেন। পরে তিনি আর্নেস্ট রাদারফোর্ডের ডাকে ম্যাঞ্চেস্টারের ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তিনি রাদারফোর্ডের পরমাণুর গঠন সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের সংযোগ ঘটিয়ে পরমাণুর বোর মডেল তৈরি করলেন।