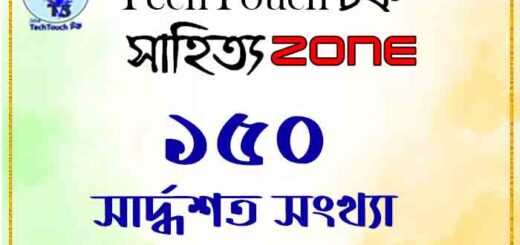রবিবারে রবি-বার – এ মৃদুল শ্রীমানী

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প
৪ ‘জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়’
জীবনের শেষ বৎসরটিতে, ১৯৪১ সালে, ১৮ জানুয়ারি তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ঐকতান’ কবিতায় লিখেছিলেন “কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,/ কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,/ যে আছে মাটির কাছাকাছি,/ সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।”
নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি/ আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি–/ এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,/ রয়ে গেছে ফাঁক।”
নিজের অর্থনৈতিক শ্রেণিগত অবস্থানটি নিরপেক্ষভাবে লক্ষ্য করে সততার সঙ্গে বলেছেন: ” …সম্মানের চিরনির্বাসনে/ সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।/ মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;/ ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।/…তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা–/ আমার সুরের অপূর্ণতা।/ আমার কবিতা, জানি আমি,/ গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।”
কী রকম কবিতা চাইছেন রবীন্দ্রনাথ? “মূক যারা দুঃখে সুখে,/ নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,/ ওগো গুণী,/ কাছে থেকে দূর যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।”
অনেকদিন আগে ১৪০০ সাল কবিতায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে ২ ফাল্গুন ( খৃস্টাব্দ ১৮৯৬ ) তারিখে লিখেছিলেন, “কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহলভরে,/ .. এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি / তোমাদের ঘরে!/ আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন /পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।”
আর পঁয়তাল্লিশ বছর কবিজীবন অতিক্রম করার মুহূর্তে বললেন, “এসো কবি অখ্যাতজনের/ নির্বাক মনের/ মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার;/ …প্রাণহীন… শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি / রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।”
এই ১৯৪১ সালেরই ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) তারিখে লিখছেন:
ওই মহামানব আসে ।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ।।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক–
এল মহাজন্মের লগ্ন ।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন ।
উদয়শিখরে জাগে ‘মাভৈঃ মাভৈঃ’
নবজীবনের আশ্বাসে ।
‘জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়’
মন্দ্রি-উঠিল মহাকাশে।।
আটচল্লিশ বছর আগে ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থের “এবার ফিরাও মোরে” কবিতায় লিখেছিলেন, “বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা– সমুখেতে কষ্টের সংসার/ বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।… এ দৈন্য-মাঝারে, কবি, একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।।” স্বর্গ হতে কে আনবে সেই শুশ্রূষা? ওই একই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:
“শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন–
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস
অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণনেত্রে– অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্যপ্রতিমা। …”
মানুষের মুক্তি কিভাবে তা ভাবতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের কথাই ভাবেন। মানুষের বাইরে কোনো ঈশ্বরের কথা ভাবেন না। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ২৭ আষাঢ় লিখেছিলেন
‘ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন ‘পরে
বাঁধা সবার কাছে’
বাংলা ২১ আশ্বিন, ১৩১২, ১৯০৫ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন:
বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান–
তুমি কি এমন শক্তিমান!
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান–
তোমাদের এমনি অভিমান ॥
চিরদিন টানবে পিছে,
চিরদিন রাখবে নীচে–
এত বল নাই রে তোমার,
সবে না সেই টান ॥
এই বিধি এবং বাঁধন বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাভাবিক নিয়মের কথাই ভেবেছেন।
বাংলা ২৭ আষাঢ়, ১৩১৭ সনে, ১৯১০ খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন,
সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর।
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে–
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দরবিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥
এই গানে আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ , আমার মধ্যে তোমার শোভা, তোমার আলো আমার মাঝে পায় কায়া, এইসব ভাবনারীতির দিকে বিশেষ করে নজর রাখতে চাই।
বাংলা ১৭ আশ্বিন, ১৩২১; ৪ অক্টোবর, ১৯১৪ খৃস্টাব্দে লিখলেন:
তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি গানের সুরে ॥
যেমনি নয়ন মেলি যেন মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে গানের সুরে ॥
সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয়মাঝে বেড়ায় ঘুরে গানের সুরে ॥
এই গানের মধ্যে মহাজাগতিক সুর, আকাশের আনন্দবাণী মাটির পৃথিবীতে তরু তৃণ হয়ে মাথা তোলে, মানবিক হৃদয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।
আচার্য শংকর বলেছিলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। তার অনেকদিন আগে প্লেটো বলেছিলেন, এই জগৎ ঈশ্বরের ছায়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টতঃই তুমির সঙ্গে আমির সম্পর্ককে অন্যভাবে দেখলেন। ২৮ আষাঢ়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দে ১৯১০ খৃস্টাব্দে বললেন, তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছ নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।
১৬ ভাদ্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন,
এই-যে তোমার প্রেম,ওগো হৃদয়হরণ,…..
প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ॥
এসব লেখার অনেক বছর পরে, ১৯২৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথমবারের জন্য আলাপ হল অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের।
আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, বিশ্বজগৎ ব্যক্তিনিরপেক্ষ। অর্থাৎ, মানুষ থাকুক বা না থাকুক, বিশ্ব নিজের গুণাবলী সমেত নিজের নিয়মে চলে। মানুষী বিবেচনার উপর বিশ্বনিয়ম নির্ভর করে না। আইনস্টাইন স্পিনোজার ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন।
ঈশ্বর না মানুষ, মৃত্যুর উপান্তে পৌঁছে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ কাকে গুরুত্ব দিলেন, সেই কথা ভাবতে গিয়ে বারুখ স্পিনোজার কথা আমাদের ভাবতেই হবে। বারুখ স্পিনোজা ( ২৪ নভেম্বর ১৬৩২ — ২১ ফেব্রুয়ারি ১৬৭৭) নামে ডাচ ভদ্রলোকের জাত জন্মের শিকড় ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখা যাবে তিনি পর্তুগিজ সেফারডিক ইহুদি। তিনি চশমার কাচ ঘসে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অত্যন্ত সাধারণ শ্রমিকের জীবন। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আহ্বান পেয়েও সেসব জাগায় চেয়ার অলঙ্কৃত করতে যান নি। কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠানের কাছে মাথা নত করতে চান নি। স্পিনোজা বলতেন, freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. আর ফ্রি বলতে স্পিনোজা বুঝতেন, I call him free who is led solely by reason.
জীবনের যথার্থ পুণ্যকর্ম বলতে স্পিনোজা বুঝতেন, True virtue is life under the direction of reason. জোরদার ভাবে বলতেন, He alone is free who lives with free consent under the entire guidance of reason.
যুক্তির সপক্ষে তীব্রভাবে বলতে বলতে বারুখ স্পিনোজা বলে বসলেন, God and the world is same thing, আর বলে বোঝাতে চাইলেন, God is not the creator of the world. তাঁর এইসব ধারণা ও প্রকাশভঙ্গি কোনোটাই ইহুদি বা খ্রিস্টান, কোনো ধর্মমতের সঙ্গেই খাপ খেত না। তার উপর তিনি বললেন, Most people parade their own ideas as God’s words, mainly to compel others to think like them under religious pretexts. আরো বললেন, The holy word of God is in everyone’s lips, but we see almost every one presenting their own versions of God’s word. তাঁর এসব কথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের খুব চটিয়ে দিল। তাঁকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করে পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা হল। তাঁর বোন এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্পিনোজা বোনের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আইনি পথে লড়ে জয় ছিনিয়ে আনেন, এবং জয়ী হবার পর, নিজের ভাগের পৈতৃক সম্পত্তি আবার বোনকেই দান করেন। এমনই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র তিনি। বিরোধী গোষ্ঠী ছোরা নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্পিনোজা প্রাণে বেঁচে গেলেও পোশাক আশাক ছিঁড়ে খুঁড়ে গিয়েছিল। ওই ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকেই তিনি ঘুরতেন। হেসে বলতেন, এই হল আমার প্রতি সমাজের উপহার।
পৌষ, ১৩৩৮, বা ডিসেম্বর জানুয়ারি ১৯৩১ – ১৯৩২ সালে ওই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিশেষ কাব্যগ্রন্থের ‘প্রশ্ন’ কবিতায় লিখলেন:
‘তারা বলে গেল “ক্ষমা করো সবে’, বলে গেল “ভালোবাসো–
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো’।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে’, তখন তাঁর মনে বারুখ স্পিনোজার কথা মোটেও উঁকি দেয় নি, একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না।
স্পিনোজার মতবাদে আস্থা রাখতেন যে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, সেই মহাবিজ্ঞানীর সঙ্গে মহাকবির তিন তিনটি বার সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৩০ -১৯৩১ সময়কালে, দুইবার জার্মানিতে এবং শেষবারের মতো নিউ ইয়র্কে।
বারুখ স্পিনোজা পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের নিয়মকেই ঈশ্বর বলে ভাবতেন। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণযোগ্য ওই নিয়মের বাইরে অন্য কোনো বিশ্বমন ও কোনো বিশ্বপিতার অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতেন না।
আইনস্টাইনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩১ বৈশাখ, মে, ১৯২৬ খৃস্টাব্দে লিখেছেন ‘ধর্মমোহ’ নামে কবিতাটি। সেখানে লিখেছেন,
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।
লিখেছেন,
অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকার বিড়ম্বনা
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা। —
লিখেছেন,
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।
শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আস্থা রেখেছেন মানুষে। মানুষের জ্ঞানচর্চায়, মানুষের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা গবেষণায়। ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের ‘চিররূপের বাণী’ কবিতায় মৃত্যুকে অবধারিত জেনে তবু মানুষী সাধনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে এগিয়ে চলা, মৃত্যুর যত ক্ষতিকে অতিক্রম করার চেষ্টা। ১৯৪১ সালে ঐকতান কবিতায় এল ‘কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,/ কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন’, কেমন কবিতা চাই, তা নিয়ে আর কোনো দ্বিধাথরথর ভাব নেই, কিছুমাত্র দোলাচল নেই। সমাজের সবচাইতে প্রগতিশীল অংশ কে, সমাজের কোন্ অংশের সঙ্গে একাত্মতা বাঞ্ছনীয়, তা নিয়ে সব সন্দেহ ঘুচে গিয়েছে। বলছেন, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, তারপর নিজেই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, সে কখনো করে না বঞ্চনা। সত্যকে অর্জন করছেন, বলছেন, সত্যেরে সে পায়, আপন আলোকে-ধৌত অন্তরে অন্তরে। ওই ১৯৪১ সালেই লিখেছেন: ‘ওই মহামানব আসে’। জীবনের শেষ কবিতাতেও বলেন, অনায়াসে ছলনা সহ্য করে, তাকে মানুষী পরাক্রমে অতিক্রম করে, শান্তির অধিকার অর্জন করার কথা।