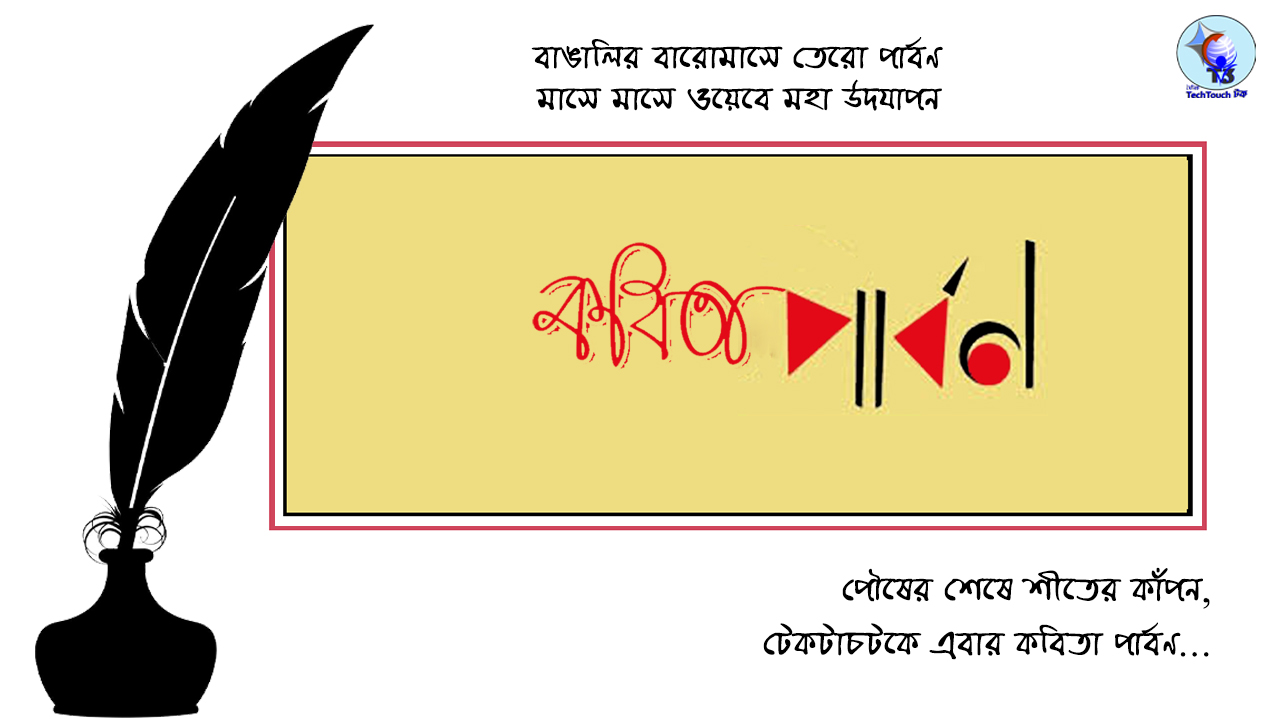।। ত্রিতাপহারিণী ২০২০।। T3 শারদ সংখ্যায় অংশু ভট্টাচার্য

বাজারের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের বাজার
মানবসভ্যতার কয়েকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলা যায় আগুন, চাকা, মোটর (গাড়ি নয়, তড়িৎচুম্বকীয়) কম্পিউটারের ভাষা এসকিউএল বা স্ট্রাকচার্ড কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি। এদের মধ্যে অন্যতম সেরা হল বাজার বা মার্কেট। কয়েক হাজার বছর ধরে, সারা পৃথিবী জুড়ে সামাজিক জীবন যাত্রার ধ্রুব সত্য বলে যদি কিছু থাকে, তা হল এই বাজার। তাত্বিকেরা বলেন, বাজারের মত এমন আর্থসামাজিক আবিষ্কার আর দুটি নেই।
কোন বাজারের কথা বলছি আমরা? সবজি আনাজ মাছ-মাংসের লেক মার্কেট, না জামা কাপড়ের গড়িয়াহাট হাতিবাগান, নাকি পড়ার বাইরের বইয়ের বিশাল জগত কলেজ স্ট্রিট? নাকি অনলাইনের অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট? আসলে এর সবগুলিই এবং আরো অনেক বেশি এবং বিস্তৃত এই বাজার।
বাজার বলতে স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে একটি জায়গার কথা মনে আসে, যেখানে প্রচুর জনসমাগম হয়। কেউ ক্রেতা তো কেউ বিক্রেতা। এবং অনেক পণ্য থাকে, সেগুলোর লেনদেন এই বাজারের প্রধান কাজ। একটি মাধ্যম থাকে লেনদেনের, বর্তমান বিশ্বে যা একমেবাদ্বিতীয়ম টাকা।
তত্ত্বগত ভাবেও এই সংজ্ঞাটি একেবারেই ঠিক। যত বেশি ক্রেতা ও বিক্রেতা আসবেন, তত তাড়াতাড়ি অনেক পণ্য লেনদেন হয়ে যাবে। সেটাই বাজারের সার্থকতা। এবং আরো একপ্রস্থ পণ্য বাজারে চলে আসবে, আবার আরেক দল ক্রেতা এবং বিক্রেতা। আরও সফল সেই বাজার। এই চক্র ঘুরতেই থাকে।
যত তাড়াতাড়ি এই চক্র ঘুরবে এবং যত বেশি লোক এই লেনদেনে অংশগ্রহণ করবেন, তত বেশি করে সফল সেই বাজার। আবার আমাদের সাধারন অভিজ্ঞতাতেও এরকমটাই দেখা যায়। যে বাজারে লোক বেশি, আমাদের ধারণা সেখানে সর্বোত্তম জিনিসটি পাওয়া যাবে, এবং সবচেয়ে সঠিক দামে। তাই সবাই সুযোগ পেলেই জামাকাপ্ড় কিনতে গড়িয়াহাট বা হাতিবাগান ছোটেন। আজকাল অনলাইনে, সেখানে যখন প্রভূত ছাড় দেওয়া হয়।
কিন্তু এই লেনদেন টা কি করে সম্ভব হয়? এত পণ্য এত বিক্রেতা; তার মধ্যে থেকে একজন ক্রেতা কিভাবে বেছে নেন? এখানে একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের সিদ্ধান্তে কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে পণ্যের মূল্য বা জিনিসের দাম। সচেতন বা অচেতন ভাবে। ক্রেতার হিসেবে দাম বেশি না কম, ট্যাঁকসই হচ্ছে কিনা, ক্রেতা সেই দামে সঠিক পছন্দের পণ্যটি পাচ্ছেন কিনা – সেটাই একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়। শেষমেশ আর কোন তেমন মাপকাঠি না থাকায়, দামের ওপর নির্ভর করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।
অথচ আমরা জানি কোন যে কোন পণ্যেরই আরো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এবং একজন ক্রেতার পছন্দ সেই বৈশিষ্ট্গুলির ওপরেও নির্ভর করে। তাহলে কোন লেনদেনের সিদ্ধান্ত শুধুই পণ্যের মুল্যমানের ওপর নির্ভর করে নেওয়া হয় কেন?
অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এর অনেকগুলো কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমটা হচ্ছে যে অনেক বৈশিষ্ট্য থাকলেও বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে সেগুলোকে তুলনা করা কঠিন। যেমন ধরা যাক কেউ একজন একটি টি-শার্ট কিনতে চান। কোন টি-শার্টের রং পছন্দ তো তার কাপড় পছন্দ নয়। আবার কোনটার কাপড় পছন্দ তো ডিজাইন মানানসই নয়। এর পরেও আছে অন্য কিছু ব্যবহারিক বিষয়, যেমন কবে তৈরি হয়ে আসবে, তার নিশ্চয়তা ইত্যাদি।
সাধারণ ক্রেতা এত সমস্ত বিষয়ের চক্করে না গিয়ে, সরাসরি যে পণ্যটির দাম তার পছন্দ অনুযায়ী সঠিক মনে হয়, সেই পণ্যটি তুলে নেন। এটাতো গেল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবহারিক সুবিধার কথা।
এর বাইরেও অনেকগুলো বিষয় আছে। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো ক্রেতার কাছে কি সমস্ত তথ্য আদৌ আছে? মানে এই যে দেখলাম টি-শার্টের কাপড় রং ডিজাইন ইত্যাদি, সেগুলো বোঝা তো আপাতভাবে সহজ।
সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের তথ্য সহজভাবে উপলব্ধ নয়। যেমন একটি কম্পিউটার কিনতে গিয়ে ওপর ওপর কতগুলো স্পেসিফিকেশন হয়ত জানা যাবে। কিন্তু কোন দেশে তৈরি হয়েছে, কানেকটরে সোনা ব্যবহার করা হয়েছে না তামা, প্লাস্টিকের বডি নাকি নাকি ধাতব; চট করে কিছুই জানা যায় না।
আবার সকাল বেলায় সবজি বাজার করতে গিয়েও এক ই দশা। মানে এই যে আলুটা সিঙ্গুর থেকে এসেছে নাকি বাঁকুড়া, রুই মাছটা লোকাল না দক্ষিণ দেশের; এই সমস্ত চট করে বোঝা সম্ভব নয়। সাধারণ ক্রেতা কি করেন, এই অবস্থায় দাম দেখেই তার গুণগতমান ঠিক করে নেন। মানে লোকাল রুই মাছের দাম একটু বেশি হবে দক্ষিণ দেশের তুলনায়, বা সিঙ্গুরের আলু ভালো হবে তাই দাম কিঞ্চিত বেশি, এইসব ভেবে নেন। অনেকে তো জ্যোতি বা চন্দ্রমুখী তফাৎ করতে পারেন না আমার মত। দোকানদার যেটির দাম কম বলবেন সেটিই জ্যোতি।
এইভাবে, একজন ক্রেতা কোন পণ্যের সমস্ত জানা-অজানা তথ্য কে একমাত্র এই মূল্যের মাপকাঠিতে নিয়ে আসেন, ও ক্রয় পর্ব সমাধা করেন। এর অনেক সুবিধাও কিন্তু আছে। ক্রেতা বা বিক্রেতাকে হাজার রকম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, চট করে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।
একটু টেকনিক্যাল ভাষায় বললে, এই দাম নির্ভর ব্যবস্থায় অনেকগুলো পছন্দের মাত্রা শেষ পর্যন্ত একমাত্রিক একটি মাপকাঠিতে, মানে পণ্যের মূল্যে এসে উপনীত হয়। যেকোনো পণ্যের লেনদেন নির্ধারণ করতে পারি এই একমাত্রিক মূল্যের মাধ্যমে। মানে বাজারের লেনদেনের সিদ্ধান্তের একমাত্র বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পণ্যের মূল্য।
কিন্তু এই যে সরলীকরণ, একটি বহুমাত্রিক পছন্দের বিষয় শেষমেশ একমাত্রিক পণ্যমূল্য এসে দাঁড়ালো, এটা কি ঠিক? বা এটা কি সবসময়ই গ্রহণযোগ্য? অর্থনীতিবিদরা বলেন যে অন্যান্য তথ্যের অপ্রতুলতা বাজারের একটা খুব জরুরি অক্ষমতা কে তুলে ধরে। আবার তথ্য থাকলেও, সেই তথ্যকে বিশ্লেষন করে, তার থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আরও কঠিন। তাই যুগ যুগ ধরে মানুষ এই সহজ রাস্তা বেছে নিয়েছে, যেখানে শুধুই দামের ওপর নির্ভর করে বাজারে লেনদেন সম্পূর্ণ হয়।
এটা ঠিক যে আগের যুগের বাজারে কোন পণ্য সম্বন্ধে বেশি তথ্য পাওয়া কঠিন ছিল। যদিও বা কিছু তথ্য পাওয়া যায়, সেই তথ্য একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা বিশ্লেষণ কিভাবে করবেন, বা তার থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসবেন, সেটাও খুব জটিল ব্যাপার ছিল। বস্তার গায়ে যদি না লেখা থাকে আলু টা কোথা থেকে আসছে বা টি-শার্টে যদি স্টিকার সাঁটানো না থাকে কিভাবে ধোওয়া বা ইস্ত্রি করতে হবে, ক্রেতার পক্ষে সেই পণ্যটি সম্বন্ধে কোন তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। যুগ যুগ ধরে বাজার এই তথ্যের অপ্রতুলতা বা তথ্য ব্যবহারের অক্ষমতা নিয়ে বেঁচে থেকেছে।
কিন্তু এবার যদি আমরা একটু বর্তমান সময়ের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে এই একমাত্রিক মূল্যমান এর বাইরেও, অনেকগুলো বিষয় আজকের বাজারে নিয়মিত ব্যবহার হচ্ছে কোন একটা লেনদেনের সিদ্ধান্তের জন্য। যেমন যদি দেখি অনলাইন বাজার, অ্যামাজনের একটি পণ্যের পাতা, যেখানে পণ্যের পাশে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হবে ভাবে নিশ্চয়ই থাকে তার দাম। কিন্তু আরো অনেকগুলো বিষয় তার সাথে উল্লিখিত থাকে। যেমন পণ্যটির স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন সাইজ রং, কোথায় তৈরি হয়েছে ইত্যাদি।
আবার আরো থাকে, অন্যান্য ক্রেতারা কিভাবে এই পণ্যটি কে ব্যবহার করে তার সম্বন্ধে গুনগান গেয়েছেন, কি কি সুবিধে অসুবিধে আছে ইত্যাদি হাজারো রকম মতামত। ক্রেতা চাইলে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চেয়ে থাকেন, এই সমস্ত তথ্যে অন্তত চোখ বুলিয়ে নিতে। আবার এই তথ্য বিশ্লেষণ করে তার থেকে একটি সহজ সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়, পণ্যের রেটিং দিয়ে। পাঁচের মধ্যে কত নম্বর একজন ক্রেতা দিয়েছেন সব দিক খতিয়ে দেখে। আবার সমস্ত ক্রেতা মিলে গড়ে পণ্যটিকে কত রেটিং দিয়েছেন। এই রেটিং আজকের একজন ক্রেতার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যদি দাম ঠিকঠাক হয়, তাহলেও অনেক ক্রেতাই পণ্যটি কিনবেন না যদি এই রেটিং তার কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়।
আবার বিক্রেতার কাছেও এই সমস্ত তথ্য জরুরি। একে তো যদি অনেক ক্রেতা তাঁর পন্যের নিন্দা করেন বা পাঁচের মধ্যে এক বা দুই নম্বর দেন, তাহলে তার পণ্য কেনার লোক ক্রমাগত কমে যাবে। আবার ক্রেতাদের এই সব মতামত থেকে তিনি বুঝে নিতে পারবেন যে চাহিদা কোন দিকে, সেই মত পণ্যের রূপ বা গুণ বদলে ফেলবেন। বাজারে টিঁকে থাকতে গেলে এটা একজন বিক্রেতার মূলমন্ত্র।
সব মিলিয়ে, আধুনিক বাজারে তথ্য জোগাড় করা আর খুব একটা মুশকিল নয়। আবার তার অনেক রকম বিশ্লেষণও সহজেই সম্ভব হচ্ছে। তো বলা যায় আজকের বাজার এই সীমিত তথ্যের অক্ষমতা কে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে অনেকটাই। পুরনো বাজারের সাথে আধুনিক বাজারের একটা বিরাট ফারাক হয়ে গিয়েছে এই তথ্যের জোগান ও ব্যবহার। তাই আমরা বলতেই পারি, আজকের নতুন বাজার হল তথ্যবহুল বাজার। প্রযুক্তি পরিভাষায় বলা যায় তথ্য সুলভ মার্কেট প্লেস।
আমি আপনি রোজ এই তথ্যবহুল বাজারে ছুটছি, ক্রয় বিক্রয় করছি, জ্ঞানত বা অজান্তে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করছি। এমনকি, এই তথ্যের জোগান ও দিচ্ছি আমরাই। আমরা কি পছন্দ করছি না করছি, কোন সময়ে বাজারে আসছহি, কোন জিনিস উল্টেপাল্টে দেখছি মানে পণ্যের পাতায় ঘরাফেরা করছি কিন্তু কিনছি না, কোনটা নেব নেব করেও নিচ্ছি না মানে, কিভাবে পাওনা মেটাচ্ছি, সবই আসলে তথ্যের ছোট ছোট বিন্দু জমা করছি। সেই বিন্দুবৎ তথ্য এভাবেই তথ্য মহাসাগর হয়ে উঠছে। আর বাজারও হয়ে উঠছে আসলে তথ্যের সীমাহীন ভাণ্ডার।
ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায় এইরকম একটি তথ্য; যে উবর হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্যাক্সি সংস্থা, কিন্তু তার একটাও নিজের ট্যাক্সি নেই। বা এয়ারবিএনবি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেল ব্যবসা, যার নিজস্ব একটিও হোটেল নেই, ইত্যাদি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই কথাগুলির আসলে তেমন কোন সারবত্তা নেই। উবর কখনো ট্যাক্সি সংস্থা হবে বলে বাজারে আসেনি বা এয়ারবিএনবি কখনো কোন হোটেল খোলার স্বপ্ন দেখেনি। এরা প্রত্যেকেই আসলে হয়ে উঠতে চেয়েছে একটি বৃহৎ বাজার, নির্দিষ্ট একটি বা দুটি পণ্য বা পরিষেবার এর জন্য, হাজারও বিষয়ে না গিয়ে। কেবলমাত্র ট্যাক্সি বা কেবলমাত্র হোটেল রুম ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য এই সংস্থাগুলোর জন্ম।
আসলে বিশেষ যে কাজটি এরা করেছেন, তা হল এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করা; যেখানে অনেক ক্রেতা আসতে পারবেন তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা নিয়ে, আবার অনেক বিক্রেতা সেখানে নিয়ে আসবেন তাদের নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা। ক্রেতার সাথে সঠিক বিক্রেতার সমন্বয় ঘটানোই এদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এবং সবচেয়ে কম সময়ে, সবচেয়ে কম খরচে।
এই সমন্বয় সাধনের জন্য এর সাথে সাথে আরো যা যা এরা আনছেন, তাহল অনেক তথ্য। যদি কেউ ট্যাক্সি বুক করতে চান, তাহলে কি মাপের কি ব্র্যান্ডের গাড়ি, এসি আছে কি নেই, সারথিকে অন্যান্য যাত্রীরা কেমন পছন্দ করেছেন, ফলে আমার ক্ষেত্রে এই সারথি সুবিধাজনক হবে কি ইত্যাদি তথ্য। আবার অন্যদিকে সারথির কাছে এটা জানা জরুরী যে ক্রেতা কোথায় যাবেন, সওয়ারি কজন আছেন, আরো কারো সাথে শেয়ার করতে ইচ্ছুক কিনা ইত্যাদি। এবার যাত্রী যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তার সবচেয়ে কাছের যে ট্যাক্সি যিনি কিনা একই দিকে যেতে ইচ্ছুক, তার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে উবর। এইখানেই উবরের বিশেষত্ব, যে এই বাজারে পরিষেবার দামের বাইরেও আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ক্রেতা ও বিক্রেতার বিষয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, এবং সেইমত লেনদেন এর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে।
তাই এদের কে ট্যাক্সি বা হোটেল ব্যাবসা না বলে বরং বলি ট্যাক্সি বা হোটেলের বাজার বা মার্কেট প্লেস, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই লেনদেন এর সিদ্ধান্ত নেন একাধিক তথ্যের ভিত্তিতে।
এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই নিশ্চিন্ত যে তার কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে । বাজারও বুঝতে পারছে যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা সুলভ সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেই একটি লেনদেনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। সেখানে ভুল হবার বা পরে হাত কামড়ানোর সুযোগ কম। এইভাবে বাজারে অনেক বেশি সার্থক লেনদেন হচ্ছে। যত বেশি সার্থক লেনদেন হচ্ছে, সেই বাজারের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ততই বেশি হচ্ছে এবং আরো বেশি মানুষ সেই বাজারে অংশগ্রহণ করছেন। এইভাবেই এক একটি উবর বা এয়ারবিএনবি বা জোম্যাটো বা স্যুইগি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর মার্কেট প্লেস হয়ে উঠছে। এরা তৈরি করে যাচ্ছেন এক একটি তথ্যবহুল বাজার, যেখানে লেনদেনের সাথে যুক্ত হাজারো তথ্য দিনকে দিন তৈরি ও ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।
এর পরবর্তী ধাপে ব্যাপারটা আরও মজার। কয়েকবার ট্যাক্সি বুক করে চড়লে বা হোটেলে ঘর বুক করে রাত্রি কাটালে, আপনার সমস্ত তথ্য এই গুগল বা উবর বা এয়ারবিএনবি কাছে রয়ে যাচ্ছে। পরে যখন আপনি আবারো ট্যাক্সি বুক করতে চাইবেন, তখন উবর আপনাকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী ট্যাক্সি ঠিক করে দেবে। তার জানা আছে যে আপনি বড় গাড়ি নেবেন না ছোট গাড়ি, এসি চাই কি চাই না, শেয়ার করবেন কি করবেন না ইত্যাদি। আপনি মাথা না ঘামালেও আপনার হয়ে মাথা ঘামিয়ে যাবে এই উবর বা এয়ারবিএনবি।
আবার সব বাজারই সরাসরি লেনদেনের বাজার নয়। মানে সেখানে টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়া হবেই এমন কোনো ব্যাপার নেই। যেমন ধরে নিই গান শোনার অ্যাপ, গানা বা স্পটিফাই ইত্যাদি বা ভিডিও দেখার অ্যাপ ইউটিউব। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতা সেই অর্থে বলা যাবে না, বলতে হবে যারা গান বা সংগীত ভিডিও আপলোড করছেন আর যারা সেগুলো শুনছেন বা দেখছেন। সেখানেও প্রতিনিয়ত শ্রোতা-দর্শকের তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে উনি কোন ধরনের গান বা ভিডিও পছন্দ করেন, দিনের বা সপ্তাহের কোন সময় কোন ধরনের বিষয়বস্তু দেখতে ভালোবাসেন। সেইভাবে তাঁর সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হয় যারা তার পছন্দের বিষয়বস্তু পোস্ট করছেন। বিশ্লেষণ করা হয় এই সংযোগের ফলাফল। এইখানে কেউই ক্রেতা-বিক্রেতা নয়। একজন দর্শক বা শ্রোতা, আরেকজন সঙ্গীত বা ভিডিও সংগ্রাহক। যদিও এদের দুজনের দেওয়া নেওয়ার মাঝখানে চলে আসেন বিজ্ঞাপনদাতারা। আর এই গানা স্পটিফাই ইউটিউব এর মত সংস্থাগুলো রোজগার করে বিজ্ঞাপনদাতাদের থেকে। খানিকটা রোজগার সংগ্রাহকরাও করে থাকেন। এই সংস্থা গুলকে আমরা বরং বলি প্ল্যাটফর্ম।
এইভাবে যে বাজার বা প্ল্যাটফর্ম টা তৈরি হলো, সেখানে কিন্তু ব্যাবহারকারিদের দুটো দল। আবার একটি সম্পূর্ণ আলাদা দল বিজ্ঞাপনদাতাদের। সাধারনভাবে এদের বলা যাক প্ল্যাটফর্ম বা বাজারের ব্যবহারকারী বিভিন্ন দল। প্রচলিত বাজারের অর্থে তাই এই নবীন বাজারকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু দিনের পর দিন এই বাজার বা প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে। আবার এখানেও রয়েছে তথ্যের সহজলভ্যতা ও তার বিশ্লেষণ ও ব্যবহার। এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ সাধন করে দেওয়া হচ্ছে এই বাজারগুলিতে সেই তথ্যের মাধ্যমেই।
এইভাবে সবচেয়ে ভাল ড্রাইভার, রেস্টুরেন্ট, গায়িকা বা সিনেমার সাথে ব্যবহারকারীর মিলন ঘটিয়ে দেবে আধুনিক এই বাজার। সোজা বাংলায় হয়ত বলা যায় সঠিক ঘটকালি করিয়ে দেওয়া। ইংরিজিতে ম্যাচমেকিং। এমনকি প্রযুক্তির ভাষায় একে ম্যাচমেকিংই বলা হয়ে থাকে। মনে করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো বাজার হচ্ছে বিবাহের ঘটকালির বা ম্যাচমেকিং এর। সেই অর্থে, আধুনিক এই বাজার ও ঘটক মিলন করায় গ্রহীতা ও তার চাহিদার পণ্য বা পরিষেবার।
এই যে নতুন যুগের বাজার, সেটা ক্রেতা ও বিক্রেতার সরাসরি ব্যবসায়িক লেনদেনেরই হোক, বা অনেকগুলো ব্যবহারকারী দলের নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান – এদের সকলের মধ্যেই একটি সবল যোগসুত্র, তা হল তথ্য, তথ্য এবং আরো তথ্য। তথ্য সংগ্রহ ও জমা রাখা, তার ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ; এই সমস্ত কিছুর মাধ্যমে এই বাজারগুলো ক্রমশ আরো সফল হয়ে ওঠে।
এই বাজারগুলিতে যেকোনো লেনদেন খুব তাড়াতাড়ি করা যায়- পণ্য বা সার্ভিস খুঁজে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয় না বা ক্রেতা খুঁজে বার করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না। তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই করে, এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে, সেখানে ক্রেতা বিক্রেতা, দর্শক শ্রোতা সংগ্রাহক এদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়া হয় খুব সহজেই।
এবং ক্রেতা-বিক্রেতা দিনের শেষে উভয়ই সন্তুষ্ট থাকেন, কারণ এই প্রচুর সংখ্যক লোকের মার্কেটে তাঁর লেনদেন সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অনলাইন ও ডিজিটাল হওয়ার ফলে এই বাজার গুলো এতই সহজলভ্য, এবং প্রায় সারা বিশ্বের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। আবার খোলাও থাকে ২৪*৭।
একথা বলাই যায় যে আগামী দিনে এই ধরনের বাজার আরো বেশি করে উঠে আসবে এবং প্রতিনিয়ত আমরা তাদের সাথে দেওয়া-নেওয়া করব। আজকের দিনে পুরনো ধাঁচের যে কটা বাজার আছে, তারাও এই পথেই হাঁটবে সন্দেহ নেই। এই বাজারগুলিকে তাই বলা যায় সত্তিকারের ভবিষ্যতের বাজার।
যদিও এটা বোঝা জরুরী যে শুধু তথ্য জোগাড় বা সাধারণ বিশ্লেষণ করলেই হবে না। সেটা দিয়ে প্রথম কয়েকবার হয়তো ব্যবহারকারীদের খুশি করা যাবে। কিন্তু লম্বা সময়ের জন্য তাদের ধরে রাখতে হলে আরো গভীর, আরও নিয়মিত বিশ্লেষণে যেতে হবে। এর একটা বড় কারণ, পণ্যের বৈশিষ্ট্য যেমন পাল্টে যাচ্ছে পাল্টে যাওয়া চাহিদা ও সময়ের সাথে, তেমনি নতুন নতুন পণ্য বাজারে আসছে। তো কোন পুরনো তথ্য বিশ্লেষণ করে যেভাবে আগে একজন ক্রেতা কে আন্দাজ করা গিয়েছিল, তার পছন্দ-অপছন্দের লিস্ট তৈরি করা গেছিল, সেটা বোধ হয় আর চলবে না। এরমধ্যে ক্রেতা অনেকগুলো সিনেমা দেখে ফেলেছেন, নতুন বই পড়ে ফেলেছেন, নতুন নতুন জিনিস কিনে ফেলেছেন। তার রুচি আর পছন্দ হয়ত বদলে গেছে। সেটা জানতে গেলে তথ্যের বিশ্লেষণ আবার নতুনভাবে করতে হবে, নতুন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। এবং এই নতুন তথ্য, তার বিশ্লেষণ, তার থেকে নতুন করে ধারনা তৈরি করা; এবং এই চক্র ক্রমাগত চালাতে থাকা- আধুনিক বাজারের আর একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য। ক্রেতাকে জানা তার কখনোই ফুরোয় না।
এই নতুন তথ্য জোগাড়, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারকারীদের সম্বন্ধে নতুন করে ধারনা তৈরি করা, অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় জ্ঞানের অভিযোজন। নিত্যনতুন তথ্যের সাহায্যে, নিত্য নতুন পদ্ধতিতে নতুন চোখে ক্রেতাকে আন্দাজ করার ক্রমাগত চেষ্টা, সেটাই এই নবীন বাজারগুলিকে আমাদের জানা বা প্রচলিত বাজার গুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে রেখেছে।
বাজারের এই ক্রেতাকে জানার যে দুর্দমনীয় ইচ্ছে, তার ফলশ্রুতিতে প্রায় প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারী সম্বন্ধে একটি বিশেষ জ্ঞান তৈরি হয়, প্রায় ব্যাক্তিগত স্তরে গিয়ে একজনের সম্বন্ধে ধারনা তৈরি করা হয়। প্রত্যেক জনের পছন্দ অপছন্দ রুচি ইত্যাদি নিয়ে এক সুবিশাল জ্ঞান ভান্ডার তৈরি হয়ে যাচ্ছে নিয়মিত এই বাজার গুলোর কাছে।
শুনতে যতটা সহজ কাজটা তার থেকে অনেক বেশি কঠিন। এত শত সহস্র বিক্রেতা, এত অর্বুদ নির্বুদ ক্রেতা; প্রত্যেকের একটা তথ্য ভান্ডার তৈরি করা, আবার তার থেকে একজন ব্যক্তির স্তরে গিয়ে কোন জ্ঞান তৈরি করা, এ এক বিরাট কাজ। অবশ্যই প্রযুক্তি ও তথ্যবিজ্ঞান বিরাট ভূমিকা পালন করে। যদিও আজকে আমরা সে আলোচনায় যাব না।
এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের আরও যে বাজার বা মার্কেটপ্লেস বা প্লাটফর্ম আসতে চলেছে, তারা এই তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ, ব্যক্তিগত স্তরে জ্ঞান তৈরি করা ইত্যাদি আরো অনেক গভীরে গিয়ে করবে। আমরা চোখের দেখায় যা দেখতে পাই তার থেকে অনেক বেশি তথ্য এই প্ল্যাটফর্ম গুলোর কাছে জমা হছে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে তৈরি হয়েছে প্রযুক্তি, যা কোটি কোটি তথ্যবিন্দুকে খুব তাড়াতাড়ি বিশ্লেষণ করে দিতে পারে। তথ্যবিজ্ঞানের নিত্যনতুন যে প্রয়োগ প্রক্রিয়া আসছে, সেগুলো আরো তাড়াতাড়ি আরও অনেক বেশি জ্ঞান উন্মোচন করতে পারে এই তথ্যের থেকে।
এইভাবে বাজারের প্রচলিত ধারণা গুলি ভেঙে যাচ্ছে বা গেছে। শুধু ক্রেতা-বিক্রেতা- ব্যবহারকারিদের এক ভার্চুয়াল বা ফিজিক্যাল ছাদের তলায় নিয়ে আসা নয়, তাদের মধ্যে সঠিক ও সফল যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া এবং পরস্পরকে অন্যের রুচি পছন্দ সম্বন্ধে অবহিত করা, যাতে করে একটি তথ্যনির্ভর লেনদেনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে, এই সবকিছুই আধুনিক বাজারের দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।
প্রচলিত অর্থে বাজারের সাফল্য ধরা হয় তার গভীরতা অর্থাৎ কতজন ক্রেতা-বিক্রেতা আছেন এবং তার দক্ষতা মানে কতগুলি লেনদেন সম্পন্ন হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এর সাথে ভবিষ্যতের বাজারে যোগ হবে আরেকটি নির্ণায়ক, যাকে বলা যেতে পারে খুঁজে পাওয়ার সুব্যবস্থা। যেখানে একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা বা দর্শক বা শ্রোতা চোখের পলক পড়ার আগেই তার উদ্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা বা ক্রেতাকে খুঁজে পেয়ে যাবেন। আগামীর একটি বাজার সফল হবে তখনি, যখন সেটি এই সবগুলি গুণসম্পন্ন হতে পারবে।
ভবিষ্যতের বাজার তাই কিভাবে আরো নিত্য নতুন তথ্য দিয়ে, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে, ব্যাবহারকারিদের মধ্যে যোগাযোগ আরো সহজে, আরও তাড়াতাড়ি এবং আরো গভীরভাবে করা যায় সেদিকেই নজর দেবে। ভবিষ্যতের বাজারের সাফল্য নির্ভর করবে শুধু যে কতজন ক্রেতা-বিক্রেতা আছেন তার ওপরে নয়; কিন্তু কত সহজে একজন ক্রেতা তার পছন্দের পণ্য খুঁজে পাচ্ছেন বা একজন বিক্রেতা কত সহজে একজন সঠিক ক্রেতাকে খুঁজে পাচ্ছেন, যার সাথে তৎক্ষণাৎ লেনদেন সম্পন্ন হতে পারে। এই চটজলদি খুঁজে পাওয়ার সাফল্যই আগামির বাজারের সার্থকতার নির্ণায়ক হবে।
কোন একটি বাজারের নিজের টিকে থাকার জন্যও এই চটজলদি ক্রেতা বা বিক্রেতা বা সঠিক পণ্য খুজে পাওয়ার ব্যাবস্থা রাখা খুব জরুরি। বাজার গুলির নিজেদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকবে। যেহেতু অনলাইন, একজন ক্রেতা বিক্রেতা খুব সহজেই অন্য একটি বাজারে চলে যেতে পারেন, তাড়াতাড়ি আরও ভাল লেনদেনের সন্ধানে। কে বলতে পারে যে তিনি একই সাথে পাশাপাশি দুটো বাজারের অ্যাপ খুলে রেখে দেখছেন না যে কোথায় তার লেনদেনের পার্টনারকে পাওয়া যায়। তাই প্রত্যেকটি বাজারই চাইবে কিভাবে আরো বেশি দক্ষ হয়ে ওঠা যায়। এই বাজারের মধ্যেকার পারস্পরিক প্রতিযোগিতা সাধারণ ক্রেতা বিক্রেতা কে আরো বেশি লেনদেনের, আরও ভাল ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ এনে দেবে সন্দেহ নেই।