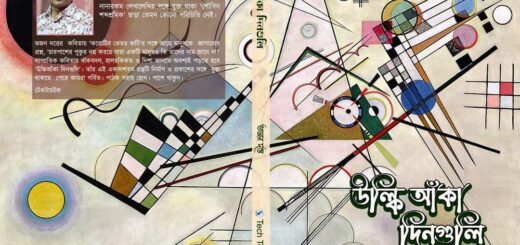রেডবুক
একপাক্ষিক মতাদর্শী মানুষের জীবনে বই পড়ার যে আসলে কতোখানি প্রভাব তা আমি প্রথম জানতে পারি ‘নকশালপন্থী ছাত্রদের’ মনস্তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করবার সময় (সাধারণ নকশালপন্থী বিপ্লবী নয় কিন্তু)। শ্রী চারু মজুমদার তাঁর ছাত্রজীবনে নিজের প্রাণপ্রিয় ঝোলাটিতে কী কী বই নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এখনও অবধি তার কোনো হিসাব না পেলেও এটুকু আমি জেনেছি যে পাঁচের দশকে অতিবামপন্থী (বা উগ্র সাম্যবাদে বিশ্বাসী) ছাত্রদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশেই চৈনিক বিপ্লবী নেতা মিস্টার মাও-সে-তুঙ লিখিত ‘বিপ্লবের লাল বই’ (রেড বুক) ছাড়া অন্য কোনো বই পড়া একেবারে ‘নিষিদ্ধ’ ছিলো। আপাতদৃষ্টিতে কু-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হ’লেও আসলে এর কারণ হ’চ্ছে এই যে মার্ক্সীয় বা মাওপন্থী উভয়প্রকার সাম্যবাদই একটি বিষয়কে প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা ক’রতো আর তা হ’লো বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত সন্দেহ নিরসন বা বিপ্লবের শত্রুরূপী ‘সংশয়বাদ’। তারা বিশ্বাস ক’রতো যে কেবলমাত্র নেতাকে প্রতি পদক্ষেপে প্রশ্ন করাই নয়, বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী কোনো সাধারণ মানুষ যদি ক্রমাগতঃ বিভিন্ন উৎস থেকে নিজেকেও সমষ্টিগত স্বার্থে নিবৃত্ত করার খোরাক জোগাতে থাকে তা হ’লে দীর্ঘমেয়াদি মহৎ উদ্দেশ্য তো কোনোদিন সাধিতই হবেনা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সমস্ত বিচার ক’রেই এগোনো যেহেতু তারুণ্যের ধর্ম, তাই ঊর্ধ্বতন অভিজ্ঞ নেতৃত্বেরই দায় তাদেরকে এই তথাকথিত সঠিক পথের দিকে নিয়ে আসা (অনুগামীর তারুণ্যই আবার সে প্রক্রিয়াকেও সহজতর করে)। সে সময় বহুসংখ্যক মেধাবী ছাত্রকে প্রতিনিয়তঃ বুঝিয়ে যাওয়া হ’য়েছে যে শিক্ষা থেকে শুরু ক’রে প্রচলিত সমস্ত ব্যবস্থাই আসলে ‘পরজীবী সংস্কৃতির’ ফসল। কোনোভাবে তাতে ন্যূনতম বিশ্বাস স্থাপনও বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।
এখন প্রশ্ন হ’চ্ছে ঠিক কীসের প্রেক্ষিতে জনৈক দার্শনিক নিজস্ব স্বৈরাচার-বিরোধী তত্ত্বে অন্ধ অনুসরণকে স্থান ক’রে দিলেন? যদি শেষ পর্যন্ত নিজস্ব মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না’ই থাকে সেক্ষেত্রে বৈষম্যের অপনোদন আদৌ কীভাবে সম্ভব? এ নিয়ে হাজারও বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এর একমাত্র উত্তর হ’চ্ছে এই যে সারা পৃথিবীতে শ্রমজীবী ও অত্যাচারিত মানুষের সংখ্যাধিক্য থাকলেও যেহেতু তাদের কেউই আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়নি, তাই তারা ‘ক্ষণিকের জন্য’ নিজস্ব অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো বিষয়েই বিচার করার ক্ষমতা রাখেনা। কাম্য ক্ষমতা তারা তখনই হাতে পাবে যখন তারা রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে অধিকার ক’রবে (যা কিনা তত্ত্বানুযায়ী বলপূর্বক ব্যতীত অসম্ভব) এবং নিজস্ব সভ্যতার সঠিক তত্ত্ব তারা নিজেরাই রচনা ক’রবে পরবর্তী প্রজন্মকে আদর্শ উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে, সে শিক্ষাও হবে আপামর পৃথিবীর জন্য। ঠিক এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে যে সমস্ত তত্ত্ব, দর্শন, মনস্কতার প্রকাশ মুষ্টিমেয় ক্ষমতাধর মানুষকে বইয়ের মাধ্যমে ছ’ড়িয়ে দেওয়া হ’চ্ছে তা কেবল পরজীবী সংস্কৃতির ফসল। সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরে ঠাঁই পাওয়ার লোভে নিজস্ব মেধাকে যে এহেন শিক্ষায় শিক্ষিত হ’তে ব্যবহার ক’রবে, ক’রেছে বা ক’রতে চ’লেছে তাকে বলপূর্বক নিবৃত্ত করাও বিপ্লবের অঙ্গ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তাজমহলের নির্মাতা হিসাবে সম্রাট শাহজাহানের নাম সর্বত্র উল্লিখিত, কিন্তু সত্যি সত্যিই যেসব মানুষের পরিশ্রমে তাজমহল আজ পৃথিবীর বিস্ময় তাদের নাম কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়না। এদিকে সেসব নিয়ে আজ যদি কেউ তদন্তে উৎসাহও দেখায় তাকেও কিন্তু যেতে হবে সেই রাষ্ট্রের নির্ধারিত (বলা হয় সর্বজনসম্মত, কিন্তু সর্বজন যে আসলে কারা তা আমরা সকলেই জানি) ব্যয়বহুল উচ্চশিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই, যা অর্থনৈতিকভাবে বলশালী না হ’লে সম্ভব নয়। মুষ্টিমেয় পরজীবীর পাঠ্য বইয়ে মুষ্টিমেয় পরজীবী লিখিত মুষ্টিমেয় পরজীবীর ইতিহাস। শিক্ষার এই ব্যবস্থাও এমনই সুচারুরূপে সজ্জিত যে নিজস্ব মেধায় সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে উঠে আসা মানুষও ব্যক্তিগত পরিসর গুছিয়ে নিতে পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের মূলে ফিরে তাকায়না। ফলাফল কিন্তু চিরকাল একই থাকে।
এতোক্ষণ যে গৌরচন্দ্রিকা ক’রলাম তার মূল উদ্দেশ্যটুকু আশা ক’রি এইবারে স্পষ্ট হ’য়েছে। উদ্দেশ্য ছিলো দেখানো যে মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতেও সমাজের একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকেই বৈষম্য কেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জ’ড়িয়ে র’য়েছে আমাদের। ইতিহাস নয় দেখালাম, কিন্তু বাকি বিষয়গুলি? চিরাচরিত অর্থনীতিতে তো বেশ সুন্দরভাবে দেখানো হ’য়েছে যে চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল সম্পর্কযুক্ত এবং স্থান-কাল-পাত্রের বিচারে এই সম্পর্কের অভিমুখ পরিবর্তনশীল (কখনও সমানুপাতিক, কখনও ব্যস্তানুপাতিক)। কিন্তু প্রশ্ন হ’লো উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাবে কি কখনোই বিনিময় নিয়ন্ত্রিত হয়না? বাজারে একনায়কত্বের অজুহাতে বিনিময় মূল্যের স্বেচ্ছাচারী তারতম্য কি আমরা কখনও দেখিনি? উত্তর হ’চ্ছে, পাঠ্য অর্থনীতির অন্তর্গতঃ এই সমস্ত অসুবিধাই জ্ঞানপিপাসু মানুষের চোখের সামনে প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয় কিন্তু শিক্ষার্থীরা সেগুলি ভালোমতো মুখস্থ ক’রে, আরো কিছু সমমনস্ক মানুষের সামনে ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ অব্যবহার্য কিছু তাত্ত্বিক আলোচনা তুলে ধ’রে, একটি সনদ জোগাড় ক’রে, দিনের শেষে ঐ একই নৈতিকতার অংশীদার হ’য়ে অর্থনীতির চর্চায় ক্ষান্তি দেয় এবং অর্থনৈতিকভাবে বলশালী হ’য়ে তার পরবর্তী প্রজন্মটিকেও তৈরী করে নিজের মতোই গড্ডলিকা প্রবাহতে অংশগ্রহণ করবার জন্য। কিন্তু এসবের বাইরে যে আসল অর্থনীতি, তা দেখায় যে বাজারে যারা ‘যোগান নিয়ন্ত্রণ’ ক’রে প্রাপ্তির তারতম্য ঘটায় তারা হ’চ্ছে পরজীবীমনস্ক মধ্যপন্থী (ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এরাই মূলতঃ বুদ্ধি ও মেধার জোরে তথাকথিত উচ্চস্তরের বলপূর্বক অংশীদার), সাধারণ মানুষের পক্ষে তুলনায় এরা বরং কম ক্ষতিকর। আসল সর্বনাশের মূলে থাকে তারা, যারা স্ব-প্রয়োজনে বাজারের যোগান নয় ‘চাহিদা নিয়ন্ত্রণ’ করে। এরাও পরজীবী ঠিকই, কিন্তু এরা পূর্বোক্তের ন্যায় হঠাৎ ক’রে গ’জিয়ে ওঠা পরজীবী নয়, আসল লড়াই এদেরই বিরূদ্ধে, এদেরকে নির্মূল না ক’রলে মানুষের কোনো মুক্তি নেই এবং ভেবে দেখলে এদেরই বিরোধিতা ক’রতে আসলে ঘোষিত সাম্যবাদের উৎপত্তি হ’য়েছিলো। এদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি এতো অতিরিক্ত পরিমাণে বেশী যে অস্তিত্বরক্ষার দুশ্চিন্তা না থাকায় এরা বহুদিন যাবত কোনো কায়িক বা মানসিক শ্রমশক্তি ব্যয় না ক’রেও নিশ্চিন্তে অপরের অস্তিত্বসংকট ঘটানোর চিন্তা ক’রতে পারে। নৈতিক প্রেক্ষিতে ক্ষমতাশালী হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় রাজনীতিও এদের দাক্ষিণ্যেই নিজস্ব গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখে। অর্থনৈতিক পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় ‘পুঁজিবাদী’ বা ক্যাপিটালিস্ট।
পুঁজিবাদ বা পুঁজিবাদী সম্পর্কে জানতে হ’লে কিন্তু ‘পুঁজি’ সম্পর্কে প্রথমে বিশদে জানা দরকার। খুব সহজ ভাষায় মানুষের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক চাহিদা ৩টি স্তরে বিভক্ত, ১। অস্তিত্বরক্ষা (যে পরিমাণ ন্যূনতম ব্যয় সপরিবারে তার ভদ্রস্থ জীবনধারণ ও সুরক্ষিত থাকবার উপযোগী), ২। উন্নীতকরণ (অস্তিত্বরক্ষার পরে সঞ্চয়ের যে অংশটুকু স্বাভাবিকভাবেই তাকে তাৎক্ষণিক পরবর্তী উচ্চস্তরের অভিমুখে পরিচালিত করে), ৩। অতিরিক্ত (পূর্বোক্ত ঘটনাদ্বয় ঘ’টে যাওয়ার পরে যেটুকু সঞ্চয়কে অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ়তর হ’তে মানুষ পুনরায় বিনিয়োগ করবার ক্ষমতা রাখে)। ঠিক এই যে তৃতীয়াংশ, বিনিয়োগের ফলে এই অংশই ক্রমাগতঃ আয়তনে বাড়তে বাড়তে অতিরিক্ত থেকে ‘মাত্রাতিরিক্ত’ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় এবং মাত্রাতিরিক্তের একাংশই আবার অবস্থা উন্নীতকরণের পর্যায়ে ফিরে গিয়ে তাৎক্ষণিক উচ্চস্তরের অভিমুখে মানুষের যাত্রাকে ব্যক্তিগত ‘বিলাসব্যসনে’ রূপান্তরিত করে। এর বিপরীতে অপর যে নিয়মিত বিনিয়োগকৃত অংশটি বর্তমান তাকেই বলে ‘ব্যবসায়িক পুঁজি’। পুঁজির বংশানুক্রমিক ও কালানুক্রমিক ব্যবহারে মানুষের একাংশ ক্রমাগত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হ’তে থাকে আর অপর অংশটি হ’তে থাকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর। স্বাভাবিকভাবে চক্রাকারে এই ঘটনা ঘটবার একটি নির্দিষ্ট মাত্রা উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আছে ঠিকই, কিন্তু সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন কেবল পুঁজির আয়তন বৃদ্ধি ক’রতেই ব্যবসায়িক পক্ষ অপরের অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থও বিঘ্নিত করে। এইভাবে বিঘ্নিত করার কারণ এইই যে সেই মুহূর্তে তাদের কাছে অস্তিত্বরক্ষা আর পুঁজির বৃদ্ধি সমার্থক হ’য়ে দাঁড়ায়। তখন সে অর্থবলে কিছু প্রলোভন দেখিয়ে স্বয়ং রাষ্ট্রের মাধ্যমে সরাসরি বাজারের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ক’রতে থাকে আর রাষ্ট্র তার নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে হ’য়ে ওঠে ‘পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক রাষ্ট্র’ বা ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমিকাল কান্ট্রি। একথা ভুললে চ’লবেনা যে রাষ্ট্রনেতারাও কিন্তু দিনের শেষে সেই সাধারণ মানুষেরই প্রতিনিধি। দেশবাসী সমস্ত শ্রমজীবীদের কাছে এর ফল হয় অত্যন্ত ভয়ানক। তারা তখন পরজীবী সংস্কৃতির ফসল হিসাবে উৎপন্ন হ’য়ে জনৈক পরজীবীরই পুঁজির বৃদ্ধিতে নিজস্ব সমস্ত শ্রমশক্তি উগরে দিতে থাকে কেবল অস্তিত্বরক্ষার জন্য। বিশ্বাস ক’রুন আর না’ই ক’রুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেতনরূপে তাদের ঠিক সেই অর্থই দেওয়া হয় যাতে তারা ব্যক্তিগত চাহিদার প্রাথমিক স্তরটুকু কোনোভাবে পূরণ ক’রতে পারে মাত্র। বেতনের মাত্রাও নির্ধারিত হয় পুঁজির বৃদ্ধিতে জনৈকের অংশগ্রহণের নিরিখেই।
ঠিক এইবারে প্রশ্ন আসে শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে তার সেই প্রাপ্য এবং প্রাপ্তটুকুও ছিনিয়ে নেওয়ার। আগেই ব’লেছি নিজের পেট ভর্তি থাকলে অপরের পেটে লাথি মারার প্রবণতা মানুষের মজ্জাগত। চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করবার যে আগ্রাসী নীতি তার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হ’চ্ছে ক্রেতার স্বাভিমানে আঘাত। “যার নেই সে কিনতে পারবেনা” এই হ’চ্ছে পুঁজিবাদী মনস্কতার প্রকাশ, কিন্তু “যার নেই সে বাঁচতে পারবেনা” এটি হ’চ্ছে আদর্শ পুঁজিবাদের প্রকাশ। আসলে এই আগ্রাসনের একমাত্র কারণ হ’চ্ছে পুঁজিবাদীর নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে পূর্বোক্ত কৃত্রিম ভয় এবং মার্ক্সীয় অর্থনীতি ঠিক এই ঘটনাকেই একবাক্যে প্রকাশ ক’রেছে এই তত্ত্বে যে উদ্ভাবনীক্ষেত্রে প্রতিনিয়তঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন না ঘ’টিয়ে পুঁজিবাদী শ্রেণী বাজারের পাশাপাশি পৃথিবীতেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনা। এইখানে এসে চিরাচরিত অর্থনীতির আরেকটি বক্তব্যের খানিক অসারতাই প্রমাণিত হ’য়ে যায় যে সবসময় ক্রেতার স্বতঃস্ফূর্ত রুচিই কেবল বাজারের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করেনা, বহুক্ষেত্রে ক্রেতার নিজের রুচিও বিক্রেতার ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মনযোগ অর্থনীতি থেকে স’রে আসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর, সেখান থেকে স’রে আসে সামগ্রিক শিল্পক্ষেত্রের ওপর যে তাহ’লে কি সভ্যতার উন্নতিসাধনে এতোদিন পর্যন্ত যা যা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ’য়েছে সকলই কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ব্যবহারিক প্রেক্ষিতে মিথ্যে? উত্তর হ’চ্ছে তা যেমন সর্বক্ষেত্রে মিথ্যে নয়, তেমনই একেবারে নির্জলা সত্যিও নয়। এ কথা যেমন ঠিক যে গণমাধ্যম না থাকলে নিজস্ব ভাবনা ছ’ড়িয়ে দিতে আমি পারতামনা, তেমনই গণমাধ্যমের অভাবে কখনোই কোনো বলিষ্ঠ মতামত অজস্র মননে ছ’ড়িয়ে প’ড়তে বাধা পায়নি। এখনও কিন্তু কেবল ভারতবর্ষেই বহু ঘরে অন্তর্জাল দূরে থাক, বিদ্যুৎ সংযোগও পৌঁছোয়নি, বাকি পৃথিবীর হিসাব তো নয় বাদই দিলাম। দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের দূরভাষের ক্রেতাও কিন্তু দীর্ঘকাল ধ’রে তৈরী করা হ’য়েছে, নাহ’লে তা কখনোই এতো বিপুল সংখ্যায় বিক্রী হ’তোনা। ভোগবাদী মনস্কতাকে উৎসাহী দিতেই উদ্ভাবন করা হ’য়েছে ‘উপভোক্তার গর্ববোধ’ বা প্রাইড অফ পজেশন বাক্যবন্ধটি। প্রযুক্তি নিজেকে সভ্যতার পক্ষে অপরিহার্য ব’লে তখনই দাবি ক’রতে পারে যখন সে আপামর পৃথিবীর প্রতিটি কোণায় পৌঁছোতে পেরেছে। সংখ্যায় সামান্য কিছু মানুষের কোনো অধিকার নেই নিজেদের সমগ্র মানবজাতির প্রতিভূ হিসাবে জনসমক্ষে ঘোষণা করার।
তো এখন আমরা ফিরে যাবো “উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে”, যেখানে আপামর মানবজাতি পশু শিকার ক’রে পুড়িয়ে খাওয়ার তুলনায় সামান্য উন্নত হ’য়েছে এবং খুঁজে পেয়েছে তার আদি ও অকৃত্রিম পেশা। ভূমিজ উর্বরতার ওপর নির্ভর ক’রে প্রথমে অসংগঠিতভাবে, তারপর নিজস্ব উদ্যোগে নির্দিষ্ট সীমানা বুঝে নিয়ে সে শুরু ক’রেছে সংগঠিত ‘কৃষিকাজ’। সেই সেদিন যে ‘কৃষিনির্ভরতা’ শুরু হ’য়েছিলো তারপর থেকেই পৃথিবীর সমস্ত সমৃদ্ধিশালী দেশ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ’রে ক’রে যাচ্ছিলো এই একই কাজ। কিছুদিন যেতে না যেতেই কৃষির পাশাপাশি তার নিজস্ব প্রয়োজনে গ’ড়ে উঠেছিলো শিল্প ও তৎসম্পর্কিত প্রযুক্তি। পারস্পরিক নির্ভরতায় আয়তনে দুই পক্ষই বর্ধিত হ’য়ে চ’লেছিলো নিজেদের মতো। সমস্যা তখনই শুরু হ’লো যখন পুঁজিবাদের পূর্বোক্ত সুবিধার্থে উন্নততর অর্থনীতির (প্রায় সমস্ত নৈতিকতারও) মাপকাঠি হিসাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা হ’লো ‘শিল্পনির্ভরতা’ এবং রাষ্ট্রের সমর্থনে পুঁজিবাদী পক্ষ কৃষির বদলে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ক’রলো শিল্পের ওপর। স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পক্ষেত্রের পরিবর্তে ‘প্রয়োজনীয়তাই উদ্ভাবনের জন্মদাত্রী’ বা নেসেসিটি ইজ দ্য মাদার অফ ইনভেনশন এই অজুহাতে কেবল পুঁজির বৃদ্ধিতে এতো বেশী সংখ্যক আরোপিত শিল্পক্ষেত্রের উদ্ভব হ’লো যে জঙ্গল ইত্যাদি শূন্যস্থান তো বটেই নূতনতর শিল্পের উদ্দেশ্যে সরাসরি কৃষিযোগ্য ক্ষেত্রও অধিগ্রহণ করা প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে লাগলো (যদিও একথা প্রমাণিত যে শিল্প কৃষির প্রধানতম সহযোগী মাত্র, পরিবর্ত নয়) এবং এর পাশাপাশি নদীমাতৃক অঞ্চলসমূহে জমির উর্বরতা নষ্ট হ’তে হ’তে সেখানকার সমগ্র কৃষিব্যবস্থাতেই সরাসরি প্রভাব ফেলতে শুরু ক’রলো, ফলে ফসলের উৎপাদন গেলো ক’মে। এদিকে শিল্পাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী নদীতে বর্জ্য, বাতাসে দূষণ, মাটি অক্ষম, তা সত্ত্বেও কেবল অস্তিত্ত্বরক্ষার্থে (শিল্পক্ষেত্রে অংশগ্রহণের যোগ্যতা না থাকায়) যারা কৃষিকাজে বাধ্য হ’লো তাদের ঐ একই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনতে হ’লো রাসায়নিক সার ও কীটনাশক, তাতে উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় আরো হ্রাস পেলো, কৃষকের অর্থাগমও একইসাথে অনেকাংশে বন্ধ হ’য়ে গেলো। অবশেষে ফলাফল যা দাঁড়ালো যে অন্যান্য প্রাণীর যোগ্য বাসস্থান নেই, মানুষের পেটে খাবার নেই, কৃষকের হাতে অর্থ নেই, আছে শুধু পুঁজিবাদী পরজীবীদের অজস্র কারখানা, তাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ ও রাষ্ট্রবল আর সেই কারখানা থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য। অর্থনৈতিক পরিভাষায় একের স্বার্থরক্ষার্থে বহুর স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবার এই অব্যবস্থা ‘বাস্তুতান্ত্রিক স্বৈরাচার’ বা ইকো ফ্যাসিজম্ নামে পরিচিত। এই ঘটনা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রবাসীকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতারণার পরিচায়ক। এই অবস্থা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনোই পথ নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকলে রাষ্ট্র এর অগ্রগতি অবশ্যই যেকোনো সময় রোধ ক’রতে সক্ষম।
কেরলের রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আলোচনা ক’রতে গেলে প্রথমেই যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ’য়ে দাঁড়ায় তা হ’লো উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নৈতিক মতবিরোধ। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণসংক্রান্ত বিষয়ে বারংবার কেন্দ্রীয় সরকারের শিরঃপীড়া হ’য়ে দাঁড়িয়েছে এই রাজ্যটি। সমস্যা হ’লো মানুষ যেকথা কখনোই বুঝতে চায়না যে পৃথিবীর কোনো দেশের, কোনো রাজ্যের, ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষসম্বলিত কোনো অঞ্চলের নাগরিকরা কখনও কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা তার সদস্যকে অন্ধ আনুগত্যের প্রভাবে জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচন করেনা, করে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি থেকে এমন কোনো রাজনৈতিক দল অথবা মানুষকে যারা স্বয়ং জনগণকেই সংসদীয় মঞ্চে উপস্থাপিত ক’রবে। কেরলে মানুষের অন্তর্গতঃ পরার্থপরতার পরিমাণ এতো বেশী যে মারণবীজাণুসংক্রান্ত বিপদে সর্বাগ্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক তারাই আক্রান্ত হ’য়েছে এবং অন্তর্গত স্বাস্থ্যব্যবস্থায় পূর্ণ বিশ্বাস (যা পারস্পরিক আস্থা ব্যতীত গ’ড়ে ওঠা সম্ভব নয়) রেখে সুস্থও হ’য়ে উঠেছে সবার আগে। ব্যক্তিগত ধর্মাচরণ ও পরিসরে তাদের সৌভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই অবহিত, কিন্তু অপরাপর প্রাণীদের প্রতি তাদের মনোভাব আমরা কতোটুকু জানি? একটি রাজ্য, যেখানে প্রায় সকল রাজ্যবাসীই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত এবং খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো সমস্ত প্রাথমিক চাহিদাই সরকারের উদ্যোগে প্রত্যেকের করায়ত্ত, গত সপ্তাহে কিন্তু সেখানেই অন্তর্জালে পঠনপাঠনের সুবিধা না পেয়ে অগ্নিসংযোগে আত্মহত্যা ক’রেছে এক ছাত্রী। শাসকের হাতে উদ্বৃত্ত যতোই থাকনা কেন এবং তার বন্টন যতোই সুচারুরূপে হোকনা কেন, একথা তো অনস্বীকার্য যে কৃষিপ্রধান একটি রাজ্যে রাজ্যবাসীর ব্যক্তিগত জমিতে উৎপাদন ও অর্থাগম দুইই বহুদিন বন্ধ ছিলো। কিছুক্ষেত্রে নৃশংসতার চূড়ান্ত হ’লেও সাধারণ মানুষ তার সর্বস্বটুকু যেকোনো মূল্যে বাঁচাতে চেষ্টা ক’রবেনা কি?
ঠিক এমতাবস্থাতেই গর্ভবতী হস্তিনীটি শস্যক্ষেতে প্রবেশ ক’রেছিলো। প্রশ্ন উঠতেই পারে যে সে যা’ই অপরাধ ক’রুক বা ক’রতে যাক, বিশ্বাসের সুযোগে খাদ্যের নামে মুখে বিস্ফোরক ছুঁড়ে দেওয়া কি নৃশংসতা নয়? নিঃসন্দেহে নৃশংসতা তাতে কোনো দ্বিমত নেই, কিন্তু একত্রে একথাও সত্য যে শেষ আশ্রয়টুকু রক্ষা ক’রতে মানুষ মানুষকে পর্যন্ত হত্যা ক’রতে পারে আর এ তো বন্য চতুষ্পদ। আসলে দিনের শেষে সহানুভূতিও তো একটি বিলাসিতার থেকে বেশী কিছু নয়। গরীব মানুষের নিজের ব’লতে ঐ পরিবারকে ভরণপোষণের স্বতঃস্ফূর্ত তাগিদটুকুই তো আছে। মার্ক্সীয় সাহিত্যে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশকেও ঠিক এইজন্যই স্থান দেওয়া হয়নি (এবং তা ক’রতে গিয়ে মার্ক্সবাদ মানুষের জীবন থেকে মনুষ্যত্বকেই একরকম বাদ দেওয়ার উপক্রম ক’রেছিলো)। শেষে এটুকুই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে যারা এহেন ঘৃণ্য কাজটি ক’রলো জমিটি কি আদৌ তাদেরই ছিলো? উত্তর যদি “হ্যাঁ” হয় তাহ’লে এ ব্যাপারে আমার আর কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু যদি উত্তর “না” হয়? যদিও রাজ্য সরকারের তদন্তের ফলাফলকে কোনো গুরুত্ব আমরা আপাততঃ দিচ্ছিনা, তারপরেও এ ব্যাপারে ব’লি অপরাধমূলক প্রবৃত্তিও সর্বদা ব্যক্তিগত অপ্রাপ্তি থেকেই আসে। মানসিকভাবে সুস্থ প্রকৃতির কোনো মানুষ অহেতুক হিংস্রতায় বিশ্বাস করেনা আর যদি তা করে তা হ’লে তাকে আক্ষরিক অর্থেই সুস্থ সমাজের উপযোগী বলা যায়না (প্রকৃত অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিসর এখানে নয়)। কেবলমাত্র একটি শ্রেণী, একটিই মাত্র শ্রেণী, যাদের বিলাসিতা আজকে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা পারলে সারা পৃথিবীর সীমানা উপেক্ষা ক’রে নিত্যনতুন পণ্যের ব্যবসা খুলে বসে (সাম্রাজ্যবাদী মনস্কতাও পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেখান থেকে মূলতঃ ‘বিশ্বায়ন’ বা গ্লোবালাইজেশনের ধারণার উৎপত্তি ঘ’টে সমস্ত দেশীয় শিল্পের সর্বনাশ ক’রেছে) সেই মুষ্টিমেয় মানুষের স্বার্থে পৃথিবীর সমস্ত সুস্থ নৈতিকতা নষ্ট হ’য়ে গেলো, বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হ’য়ে গেলো, হয়তো মানবজাতির ধ্বংসও ত্বরান্বিত হবে। শুনলে অবাক হবেন যে দুই-তিনমাসব্যাপী মৃত্যুমিছিলের পর ইতালিতে অজস্র মানুষ রাস্তায় অর্থ বর্জ্যের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে এই ব’লে যে কাছের মানুষরাই যখন র’ইলোনা তখন এসব রঙিন কাগজ দিয়ে আমাদের আর কী হবে? অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন জীবন পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের প্রাপ্য, প্রত্যেকটি প্রাণের স্বপ্ন। কেরলে এ মৃত্যু, এ নৃশংসতা, এসবের দায় রাজ্যবাসীর নয়, ভালোভাবে বাঁচতে চাওয়া আপামর পৃথিবীর মানুষের নয়, এ দায় পুরোপুরি অর্থলিপ্সু সেই নরপিশাচদেরও নয়, দোষ নিয়ন্ত্রণের, দোষ সুবিধার হার বাড়ানোর নামে পরনির্ভরতার, এজন্য সমর্থক বা বিরোধী হিসাবে কোনো পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে শাসনব্যবস্থাকে দোষারোপ বা গৌরবান্বিত ক’রতে হয়না। আসল যুদ্ধ যাদের সঙ্গে তাদের কাছে অনুভূতির মূল্য খুব কম, প্রায় নেইই ব’লতে গেলে। কেবল প্রার্থনা ক’রি যে ফিরে আসুক, প্রাপ্য ন্যায়বিচারের ব্যবস্থাটুকু পুনরায় ফিরে আসুক। মনে রাখবেন বিশালাকায় যে ভোজনালয়টি থেকে পছন্দের খাবারটি আনিয়ে আস্বাদন ক’রতে ক’রতেই হাতিটির জন্য দুঃখ ক’রেছেন, সেখানেও একদিন প্রাণ ছিলো, সেখানেও একদিন সবুজ ছিলো। হাতি না হোক, গোরু চ’রতো সেখানে। তাদের ঘরহারা ক’রে দিয়ে এই যে রমরমিয়ে ব্যবসা, সেখানে কিন্তু এইভাবেই অপরাধের আমরাও অংশীদার। ঐ যে ব’ললাম পুঁজির বৃদ্ধিতেই কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি।
ধন্যবাদ।
(বিঃদ্রঃ হাতিটিও মরিয়া পুনরায় প্রমাণ করিয়াছে যে গণমাধ্যমে সমস্ত ঘটনাই একেকটি গড্ডলিকা প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ধন্যবাদ।)