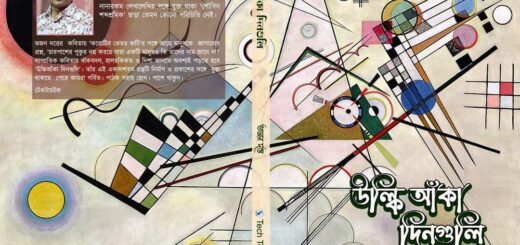–situsslotgacor–link(nagatoto168.com) – ফিরে দেখা পৌষমেলা ও নিরুদ্দেশের ঠিকানা

ঘরের খুব কাছে হলেও সব জায়গায় যাওয়া হয়ে ওঠেনা। ছোট বেলা থেকে শুনে আসা, জানা এবং পড়া যে শান্তিনিকেতন সেখানে যেতে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল কলেজের শেষ ধাপ পর্যন্ত। সেই তারুণ্যে তখন জড়িয়ে আছি বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে। নিজের গ্রাম থেকে সম্পাদনা করছি একটি পত্রিকা আর দুর্গাপুর থেকে যৌথভাবে সম্পাদনা করছি আর একটি। তার সঙ্গে দুর্গাপুর থেকে আর একটি বড় পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্বে আছি। নিয়মিত চলছে সাহিত্যের আড্ডা। সেই আড্ডা থেকেই ঠিক হল পৌষ মেলায় শান্তিনিকেতন যাওয়া হবে। শুধু মেলা দেখাই নয়, অন্য দুটো আকর্ষণ আছে। প্রথমত পত্রিকাগুলো বিক্রি করার চেষ্টা করা হবে, স্বপন ওর কবিতার বইও বিক্রি করবে। দ্বিতীয়ত, সেখানে কলকাতার কণ্ঠস্বর পত্রিকার স্টলে কবিতা পড়ার আমন্ত্রণ পাওয়া গেছে। পত্রিকা চালানোর সুবাদে ততদিনে বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হয়েছে। তাদেরও কেউ কেউ নিশ্চয় আসবে সেখানে। যোগাযোগ যা আছে সে তো চিঠিপত্রের মাধ্যমেই। কবিতা পাঠের আসরে গেলে হয়তো তাদের অনেকের সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হবে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, তখন মোবাইলের নামগন্ধ ছিলনা। সময়টা সত্তরের দশকের শেষ ভাগ।
সেবছর মেলা শুরু হওয়ার পরদিন আমরা চারজন, আমি, স্বপন (পাল), চিন্ময় (ঘোষ) আর মথুর (দাস) একসঙ্গে দুর্গাপুর থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছানোটাই জাগিয়ে তোলে এক বিস্ময় আর আনন্দ। কেবলই মনে হয় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা থেকে তাঁর দৃষ্টিতে দেখা বোলপুর আর ভুবনডাঙার মাঠকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করি। মিলিয়ে দেখতে চাই আগের দেখা অন্যান্য মেলার সঙ্গে পৌষমেলাকেও। আরও আগে কিরকম ছিল জানিনা, কিন্তু আমি যা দেখছি তাতে মেলার গ্রামীণ রূপ যতটা, তার চেয়ে শহুরে প্রভাবই বেশি। এটাই হয়তো ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। তারপর নতুন আগন্তুক হিসাবে জনস্রোত ঠেলে খুঁজতে খুঁজতে পৌঁছে গেলাম কণ্ঠস্বরের স্টলে।
একটা চিন্তা ছিল মেলার এত ভিড়ের মধ্যে শান্তিনিকেতনে থাকবো কোথায়। রাত্তিরে না থাকলে সন্ধ্যার বাজি উৎসব, বাউল গান, কবিগানের লড়াই, নানাধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কোনোটাই দেখা হবেনা। শেষ পর্যন্ত কলাভবনে ঠাঁই পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে শুধুমাত্র রাত্রিটুকুই থাকতে পারবো, তাই কাঁধের ছোট ব্যাগটি কাঁধে নিয়েই ঘুরতে হবে সারাদিন।
সেই প্রথম নিজের শহরের বাইরে অনেকের মাঝে কবিতা পাঠ। আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসেছিল তাদের কণ্ঠে তাদের কবিতা শোনার অভিজ্ঞতাও সেই প্রথম। তখন অনেকের সঙ্গেই বেশ অনেকদিনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, যদিও তা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। সেখানে তাদের সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হওয়ায় পরিচয়টা আরও ঘন হওয়ার সুযোগ হল তো বটেই। এই আনন্দে যখন মশগুল হয়ে আছি, সেই সময়, দুপুর নাগাদ, হঠাৎই কণ্ঠস্বরের স্টলে এলেন বিখ্যাত কবি, শিল্পী এবং চিত্র পরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী। পরনে সাদা ধুতি আর আর্দির পাঞ্জাবি, সাদা শাল। তাঁকে এরকম সামনে পেয়ে যাবো একদমই ভাবিনি। তাঁর কবিতা পড়েছি, তাঁর তৈরি ছবি ‘স্ত্রীর পত্র’ দেখেছি, কিন্তু এখানে তাঁর মতো শিল্পীর মুখোমুখি হবার সুযোগ হয়ে যাবে, এটা পৌষ মেলায় আসার আগে ভাবিনি। তাঁর কবিতা শুনলাম, কবিতা নিয়ে তাঁর আলোচনা শুনলাম। তারপর স্টলের পাশে একটি বেঞ্চিতে এসে বসলেন তিনি।
আমি সরাসরি তাঁর সামনে গিয়ে নিজের নাম বলে পরিচয় দিলাম। মনে পড়ে, এমন ভাবে নামটা বলেছিলাম যেন বলা মাত্রই চিনতে পারবেন। পরক্ষণেই অনুভব করলাম যে আমার মতো অর্বাচীনকে চেনার তাঁর তো কোন দায় নেই, সম্ভবও নয়। আমি সরাসরি বললাম, স্যার, একটা অনুরোধ ছিল। আমি আমার গ্রাম থেকে সুপ্রভাত নামে একটা পত্রিকা বের করি। পরের সংখ্যার জন্য একটা প্রচ্ছদ এঁকে দেবেন? এসব তখন একদম মাথায় আসেনি যে প্রথম দেখাতেই তাঁর মত একজন মানুষকে নগণ্য এক পত্রিকার জন্য প্রচ্ছদ এঁকে দিতে বলা যায় কিনা। আসলে ওইরকম বয়সে অতসব যুক্তির কথা মাথাতেই আসেনা। আমারও আসেনি। বরং এটাই মনে হয়েছিল যে নিজের সম্পাদিত পত্রিকার প্রচ্ছদ যদি পূর্ণেন্দু পত্রীর মতো একজন শিল্পীর আঁকা হয়, তা শুধু গৌরবের নয়, একটা চমকে দেওয়ার মতো কিছু হবে। তাই প্রথম সুযোগেই আলাপ আর অনুরোধ। আর তিনিও নির্দ্বিধায় বাড়িয়ে দিলেন হাত। আমি ব্যাগ থেকে একটা সাদা কাগজের প্যাড আর একটা স্কেচ পেন তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ মাত্র কয়েকটি স্ট্রোকে এঁকে দিলেন একটি বাউলের স্কেচ। কতটা মুগ্ধ আর কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম জানিনা। সেই স্কেচটি সযত্নে রাখা আছে আমার কাছে। ভেবেছিলাম পত্রিকার পরবর্তী কোনো সংখ্যায় সেটি প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করবো। কিন্তু দুঃখের কথা, সে সুযোগ আর হয়নি। লিটল ম্যাগাজিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার গল্প মোটামুটি সবারই জানা।
দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত আমাদের আর একটি পত্রিকা স্বমচিতা’র নামটিও তিনি এঁকে দিয়েছিলেন। তারপর আমাদের সঙ্গে শুরু হলো আলাপচারিতা। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। তাঁর আগামী ছবি মালঞ্চ, সেই ছবির প্রস্তুতিপর্ব নিয়েও তিনি অনেক কথা বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে।
পৌষমেলার একটা বড় আকর্ষণ বাজি উৎসব। পুজো বা দেওয়ালিতে যে বাজি পোড়ানো হয় সেটা অন্যরকম। কিন্তু বাজির উৎসব যে এরকম হতে পারে সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। না দেখলে ভাবতেও পারতামনা যে তা এত চমৎকার হতে পারে। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হলো সেই উৎসব। আগে থেকেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ব্যবস্থা করে রাখা থাকে। সেইমত বাজি ফুটতে থাকলো বিভিন্ন দিক থেকে। নানান শব্দ সৃষ্টি করতে করতে বিচিত্র সব আলোকমালায় মিলিয়ে যেতে থাকলো দূর আকাশে। বেচাকেনা খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে মেলাপ্রাঙ্গণের সমস্ত মানুষের দৃষ্টি তখন আকাশে। শেষ চমকটা তখনও বাকি ছিল। বিভিন্ন দিক থেকে বাজি ফাটতে ফাটতে একটার সঙ্গে আর একটা যোগ হয়ে নানান রঙ আর আকার আকৃতি তৈরি করতে করতে এক সময় আকাশের বুকে বাজির আলোয় আঁকা হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের মুখ। বিস্ময়ের চরম সীমা সেটা আমার কাছে। মনে হল, এই যে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এত মানুষের এই মিলনমেলা যেখানে সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, এইটিই পৌষমেলার সার্থকতা। বিশ্বভারতীর সার্থকতা। নিছক রংবেরঙের খেলা নয়, বাজি উৎসবের সৃষ্টিশীল কারিগরেরা সবার চোখের সামনে আলো দিয়ে আকাশে এঁকে দিলেন যে মুখ, তা আমাদের উত্তরাধিকার। সে এক বিশেষ আলো, আমাদের সংস্কৃতি আর জীবনবোধের। আমি এক নগণ্য মানুষ সেই মিলনমেলায় সেই মুহূর্তে শামিল হতে পেরে যেন নিজের অস্তিত্বকেই ছুঁতে পারলাম কিছুটা।
রাত্রে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল কলাভবনে। স্বপনই ব্যবস্থা করেছিল। ও ইচ্ছা করলেই ওর ভাইয়ের সঙ্গে হোস্টেলে থাকতে পারত। কিন্তু সবাই মিলে একসঙ্গে থাকাটাই ওর বেশি আনন্দের মনে হয়েছিল। কলাভবনে পৌঁছে দেখি একটা বড় হলে অনেক মানুষ। কেউ শুয়ে পড়েছেন, কেউ বসে অন্যদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। মেঝেতে খড় বিছানো, তার উপর শতরঞ্চি পাতা। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে হলের ভিতরে ঢুকে বেশ উষ্ণতায় স্বস্তি বোধ করলাম। খড়ের উপর পাতা শতরঞ্চিতে বসে আরও ভালো লাগলো। মনে হলো এত মানুষের জন্য এই ঠাণ্ডায় এর চেয়ে সহজ ব্যবস্থা আর হতে পারেনা।
একটা খালি জায়গা দেখে বসে পড়লাম। পাশাপাশি পাতা শতরঞ্চি সরে গিয়ে মাঝে মাঝেই খড় বেরিয়ে পড়েছে। সেরকমই একটা জায়গা পেলাম আমরা। কিছু করার নেই। এখানেই চারজনে গাদাগাদি করে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়া যাবে। বসেই দেখি একটু দূরে অভিজিৎ দা, দলবল নিয়ে আড্ডায় মেতে আছেন। অভিজিৎ ঘোষ, কলকাতার আর একটি পত্রিকা ‘সৈনিকের ডায়েরি’র সম্পাদক। ফোল্ডার আকারে বের হয় পত্রিকাটি প্রতি মাসে। দুহাজার কপি ছাপা হয় ভারত ও বাংলাদেশে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। যুগ্ম সম্পাদক নির্মল বসাক। অনেকদিন থেকেই পত্রিকায় লেখালেখির সূত্রে এই দুজনের সঙ্গে আলাপ এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমেও অনেক মত বিনিময় হয়েছে। আজও মেলায় অভিজিৎ দার সঙ্গে কথা হয়েছে, গল্প হয়েছে কিছু। নির্মল দা আসেনি। এখন আড্ডায় বসার আর একটা সুযোগ পাওয়া গেল। এটা সুযোগই কারণ অভিজিৎ দা এমন সব মজার মজার কথায় জমিয়ে রাখেন যে সহজেই আড্ডার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। ব্যক্তি হিসাবেও তিনি স্বনামধন্য। ১৯৭৫ এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত All India National Poets Congress এর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। Young Writers নামে একটি সংস্থারও দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি সম্পাদক হিসাবে। পরবর্তীকালে কত যে পদ অলংকৃত করেছেন আর কত কাজের সঙ্গে যে যুক্ত হয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবেনা। বলা বাহুল্য, সেই অভিজিৎ দার সঙ্গে আড্ডায় সেদিন ভোর হয়ে গেছিল।
প্রথমদিন পত্রিকার বিক্রিবাটা খুব একটা হয়নি। স্বপন তাও ওর কবিতার বই বেশ কয়েক কপি বিক্রি করতে পেরেছে। কিন্তু পত্রিকাগুলোর বিক্রি বেশি হয়নি। মেলার মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে সম্ভাব্য ক্রেতা মনে করে অনেককে এপ্রোচ করেছি। কাউকে দেখে হয়তো মনে হয়েছে উনি হয়তো শিক্ষক। ঝোলা ব্যাগ থেকে এক কপি পত্রিকা বের করে বলেছি – গ্রাম থেকে সদ্য প্রকাশিত পত্রিকা। দাম মাত্র এক টাকা। এক কপি নিন না! মুখ ফিরিয়ে চলে গেছেন। কাউকে আবার ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক কৃষক কিছুই না মনে করে বলেছি, একটা পত্রিকা নেবেন? নতুন নতুন কবিতা গল্প প্রবন্ধ সব আছে। দাম মাত্র এক টাকা। কেউ হাতে নিয়ে দেখেছেন। কেউ কেউ কিনেছেনও। দাম হয়তো এমন কিছু বেশি নয়। কিন্তু বেশি দামের জন্য লোকে পত্রিকা কেনেনা তা তো নয়। ওসব যেন কেনার বস্তু নয় এমন একটা মানসিকতা কাজ করে বোধ হয়।
তবে আমাদের মতো বেকার এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটাকার মূল্যও তো কিছু কম ছিলনা সেইসময়। এর পরেও আমরা কয়েক বছর ধরে মেলায় গেছি। আমরা সেখানে দু-তিন টাকার মধ্যে একবেলার খাওয়া সেরে নিতে চেষ্টা করতাম। একবার ভাবলাম, এত গরিবিয়ানা ভাল্লাগছেনা। একটু ভালো করে খাওয়া যাক। এক জায়গায় সেঁজুতি বলে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। সেখানে মিল সিস্টেমে নিরামিষ খাওয়ার খরচ পাঁচ টাকা। এটা আমরা কয়েকবার দেখেও এড়িয়ে গেছি। পাঁচ টাকা খরচ হয়ে যাবে একবার খেতে? সেটা তো বিলাসিতা! বেশিরভাগ হোটেলেই মিল সিস্টেম। যতটুকুই খাও, দাম দিতে হবে সেই পাঁচ টাকা। পাইস সিস্টেম হোটেল পেলে সুবিধা হতো। কিন্তু সেরকম তো চোখে পড়েনি। এই বিভিন্ন সিস্টেমের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা তখনো খুব ভালো করে জানতামনা। বাইরের হোটেলে তো খেতে হতোনা! একবার নিজের জেলা বাঁকুড়া শহরে গেছিলাম হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়ার পর। সেই প্রথম বাঁকুড়া যাওয়া। সেখানে হোটেলে খেতে হয়েছিল দুপুরবেলা। সেখানেই প্রথম দেখেছিলাম হোটেলে ‘পাইস সিস্টেম’ কথাটা লেখা। পরে বুঝেছিলাম মানেটা। পৌষমেলায় সেবার বন্ধুরা মিলে ঠিক করেছিলাম যে রাত্রে সেঁজুতিতেই খাবো। খেয়ে খুব তৃপ্তি হয়েছিল সবার। সেই প্রথম ওই সময়ের পাঁচ টাকাকে খুব তুচ্ছ মনে হয়েছিল।
যাই হোক, পরদিন মেলাতে দুপুর অব্দি কাটিয়ে আমরা দুর্গাপুর ফিরে যাবো এরকমই ঠিক ছিল। দুপুরে খাওয়ার পর আমরা একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। স্বপন হয়তো নিজের কবিতার বই বিক্রি করছে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে। মথুর হয় ওর সঙ্গে আছে নাহয় একা একাই ঘুরছে মেলায় এদিক সেদিক। নতুন নতুন কবিতার লাইন গড়ে রাখছে মনের মধ্যে। ও সবকিছু খুব ভালো মনে রাখতে পারে। কবিতার লাইন একবার মাথায় এলে অনেকদিন পরে হলেও সেটা লিখে ফেলতে পারে। আমি চিন্ময়কে খুঁজে পেলাম। দুজনে অপেক্ষা করছি স্বপন ও মথুরের জন্য। সবাই একসঙ্গে হলেই বাসে উঠবো।
কিন্তু ওদের দেখা পাচ্ছিনা। হয়তো ফিরতে যে হবে সেই কথাটাই ওদের মনে নেই। কিম্বা সময়টা লক্ষ্য করেনি। দুর্গাপুরের এক একটা বাস ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা আসছেনা। এভাবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি যখন, তখন হঠাৎই চিন্ময়ের মাথায় বোধ হয় একটা কিছু বুদ্ধি এসেছিল। বললো, তারাশংকর, চল, কোথাও পালিয়ে যাবি?
পালিয়ে যাবো?
মানে হারিয়ে যাবি? ওদের যখন খুঁজে পাচ্ছিনা, একরকম ধর আমরা হারিয়েই গেছি। একটু ভালো করেই হারিয়ে যাই, বললো চিন্ময়।
আমি বললাম, কিরকম?
বললো, চল, কোথাও চলে যাই। অন্য কোনো দিকে।
কিন্তু আমরা তো দুর্গাপুর ফিরবো।
সে আজ না হয় কাল ফিরবো।
চল তাহলে।
ব্যাস। একেবারে পরিকল্পনার বাইরে কোথাও চলে যাওয়া ঠিক হয়ে গেল। একটা বয়স বোধ হয় থাকে যখন কোথাও বিনা নোটিসে চলে যাওয়া বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার একটা ইচ্ছে কখনও কখনও মনের মধ্যে জেগে ওঠে। তখন সেই বয়সে ওদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খুঁজে না পেয়ে হয়তো আমাদেরও তাই হয়েছিল। আসলে ঠিক সেই অর্থে হারিয়ে যাওয়া নয়। হঠাৎ ইচ্ছা হলো তাই অন্য কোথাও চলে যাওয়া, কিন্তু বন্ধুদের যেহেতু কিছু জানা নেই এ ব্যাপারে তাই তাদের কাছে ব্যাপারটা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার মতই।
কিন্তু যাদের পথ চেয়ে এতক্ষণ বসে ছিলাম, কেবলই মনে হচ্ছিল এই বুঝি এসে গেল ওরা, সেই চিন্তাটা পাল্টে গেল। ওদেরকে না পেয়ে ঠিক যখন আমরা অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়া ঠিক করলাম, তখন কেবল মনে হচ্ছিল পাছে ওরা এখুনি এসে পড়ে! মন চাইছিল ওদের সঙ্গে যেন এখন দেখা না হয়ে যায়। এসব ভাবতে ভাবতে চিন্ময় একটা এগিয়ে আসা বাস কে দেখিয়ে বললো, চল, এটায় উঠে পড়ি। এ তো রামপুরহাটের বাস? আমরা কি রামপুরহাট যাবো? উঠে পড় তো, যেখানে হোক যাওয়া যাবে।
উঠে পড়লাম রামপুরহাটের বাসে। আমার মনে হল অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা। চিন্ময় হয়তো একটা জায়গা তাৎক্ষণিক ভাবে ভেবেই রেখেছিল, নাহলে রামপুরহাটের বাসে উঠবে কেন।
রামপুরহাটেও সেই আমার প্রথম যাওয়া। সন্ধ্যার পর সেখানে পৌঁছে সেখান থেকে আবার একটা বাস ধরে কোন এক গ্রাম। গ্রামের নামটাও এখন মনে নেই। ঘড়িতে এমন কিছু বেশি না বাজলেও গ্রামজীবনে শীতকালের রাত সাড়ে আটটা বেশ নিঝুম হয়ে যায়। পৌঁছলাম চিন্ময়ের আত্মীয়ের বাড়িতে। বলা বাহুল্য, তাঁরাও কেউ জানতেন না আমাদের আসার কথা। কিন্তু তবুও রাত্রিবেলা আত্মীয়ের সঙ্গে এক অচেনা অতিথিকে আসতে দেখে এত অবাক আর আনন্দিত হয়েছিলেন যে আমিই অবাক হয়ে গেছিলাম। বোঝা গেল চিন্ময়ও বহুদিন যায়নি সেখানে। চিঠিপত্রও লেখেনি। সে নিয়ে ওকে বেশ কিছু অনুযোগ শুনতে হলো। যে উষ্ণ অভ্যর্থনা আর আদর পেয়েছিলাম ওই বাড়ির মানুষগুলির কাছে, অল্পসময়ের মধ্যে আমিও ওদের আত্মীয় হয়ে উঠেছিলাম, অদ্ভুত আনন্দে কাটিয়েছিলাম একদিনের বদলে দুটো দিন, তা মনে থাকবে চিরকাল। এরকম বেশি পাইনি জীবনে।
আসলে সময়টাই এরকম ছিল। কিছু না জানিয়েও চলে যাওয়া যেত যেকোনো আত্মীয়ের বাড়িতে, যেকোনো সময়। সাধারণ মানুষের বাড়িতে ফোন ছিলনা তখন। গ্রামের দিকে তো কথাই নেই। আসা যাওয়া অথবা চিঠিপত্র ছাড়া অন্য কোনো যোগাযোগ ছিলনা। তাই অসময়ের হঠাৎ আগন্তুকও অতিথির সাদর অভ্যর্থনা পেত। আর দূরে কোথাও গিয়ে ফিরতে দেরি হলেও বাড়িতে অতটা চিন্তা করতনা। বাড়িতে জানতো বন্ধুদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় গেছি, একদিনের জায়গায় দুদিন হতেই পারে। আমার বরং চিন্তা হচ্ছিল স্বপন আর মথুরের জন্য। ওরা নিশ্চয় খোঁজাখুঁজি করবে আমাদের, না পেয়ে একটু চিন্তাও করবে। শেষে হয়ত ভাববে আমরা যে যার বাড়ি ফিরে গেছি। হয়েওছিল তাই। সেটা আমরা পরে ওদের মুখেই শুনেছিলাম। আসলে উদ্বেগ ব্যাপারটা কমই ছিল তখন। মনে রাখতে হবে, সময়টা সত্তরের দশকের শেষ ভাগ। মোবাইল- বিহীন সেই যুগে কাউকে সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ত দিতে হবে আমি কোথায়, বা কেউ আমার খোঁজ নেবে সেই সম্ভাবনা ছিলনা। যোগাযোগের তেমন মাধ্যম ছিলনা বলে হয়ত যোগাযোগ করে খবর দেওয়ার বা নেওয়ার কোন দায়ও ছিলনা কারও। ফলে এই খবর না পাওয়াটাই ছিল সে সময়কার একটা বাধ্যবাধকতা। সেকারণে উদ্বেগও কম। মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে মোবাইল। প্রতিটি মুহূর্ত থাকতে হয় নজরদারির মধ্যে। এখন খুব মুশকিল হারিয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। তাহলে মোবাইল ফোন হয় ফেলে দিতে হবে বা নষ্ট করে দিতে হবে, নাহয় বন্ধ রাখতে হবে। তাতেও অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে পরে। ভাগ্যিস এসব ছিলনা তখন, তাই মেলার জনসমুদ্রে একবার নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে সেখান থেকে আবার একদিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পেরেছিলাম।
কিন্তু সব আনন্দ তো আর নির্ভেজাল হয়না। তাৎক্ষণিক আবেগে যা করে ফেলা যায়, কখনও কখনও তার জন্য বিড়ম্বনাতেও পড়তে হতে পারে, সেই শিক্ষাটাও হাতেনাতে পেয়েছিলাম সেই ‘নিরুদ্দেশ’ যাত্রায়। সেদিন রাত্রে ওখানে পৌঁছানোর আগেই পকেট হাতড়ে বুঝে গেছিলাম আমাদের দুজনের কাছে যা আছে তাতে দুর্গাপুর ফিরে যাওয়ার বাস-ভাড়া হবেনা। শান্তিনিকেতনে বাসে ওঠার আগে এসব ভাবনায় আসেনি। দুর্গাপুর ফিরে গেলে কোন সমস্যা হতোনা। স্বপন মথুর সঙ্গে এলেও সমস্যা হতোনা, কারণ ওদের দুজনের পকেটেই একটু বেশি টাকা পয়সা থাকে। তাছাড়া স্বপন ওর কবিতার বই বেশ কিছু বিক্রি করতে পেরেছে। তাই ওর কাছে টাকা আছে। কিন্তু আমার আর চিন্ময়ের পকেট প্রায় ফাঁকা। তাই আনন্দ উত্তেজনার পাশাপাশি ফেরার ভাড়ার টাকা কোথায় পাই সেই চিন্তাই বেশি করে ভিতরে ভিতরে বেজে চলেছে।
পরদিন সকালে দুজনে পরামর্শ করে ঠিক হল কয়েকটি পত্রিকা বিক্রি করতে পারলে ভাড়ার টাকাটা উঠে আসতে পারে। সেইমত অমলকে আমাদের পত্রিকার কয়েকটি কপি দিয়ে বললাম যদি কিছু বিক্রি করে দিতে পারে। অমল চিন্ময়ের দূর সম্পর্কের ভাই, আমারও বন্ধু হয়ে গেছিল। ও নিয়ে গেছিল কয়েকটি কপি, কিন্তু গ্রামের হাটে কে পত্রিকা কিনবে? বলা বাহুল্য, একটিও বিক্রি হয়নি।
সেটাই আমাদের বিড়ম্বনাকে বাড়িয়ে দিল বহুগুণ। মুখ ফুটে কাউকে বলতেও পারছিনা যে আমাদের কাছে বাসে ভাড়া দেওয়ার মতো টাকা নেই। আবার দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর দুর্গাপুর ফিরে যাবো এটাও ঘোষণা করে দিয়েছি। সেই অবস্থা থেকে সেদিনের মত কিছুটা রিলিফ দিলেন গৃহকর্ত্রী, সম্পর্কে দিদিমা। তিনি বললেন, আজ কিছুতেই যাওয়া হবেনা, কাল সকালে যেও।
সেদিনের মতো মান বাঁচলো, কিন্তু সমস্যার তো সুরাহা হলোনা। সেই চিন্তাটা থেকেই গেল। শত আদর আপ্যায়ন আড্ডা আর আন্তরিকতার আবহেও ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তির কাঁটা ফুটে উঠছিল মাঝেমাঝেই। নিরুদ্দেশ হতে গিয়ে এ কী বিড়ম্বনা!
পরদিন সকালে রওনা দেওয়ার আগে আমাদের দুজনের মনেই হাজারো দ্বন্দ্ব। ওদের কাছে টাকা চাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। সেই নিয়ে আমরা দোটানার শেষ সীমায়। তখনই এলেন সেই দিদিমা। বললেন, তোমরা এলে খুব ভালো লাগলো। আবার এমনি করেই চলে এসো। তারপর দুটো দশ টাকার নোট চিন্ময়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আমার মেয়ের কাছে একবার যেও। দুর্গাপুরে তোমাদের কাছেই তো থাকে। ওকে এই টাকাটা দিয়ে দিও। বুঝলাম, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিরুদ্দেশ হতে পারলে শেষ পারানির কড়ি ঠিক জুটে যায়। কে যে কিভাবে কার মন পড়তে পারে, তার তল খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।