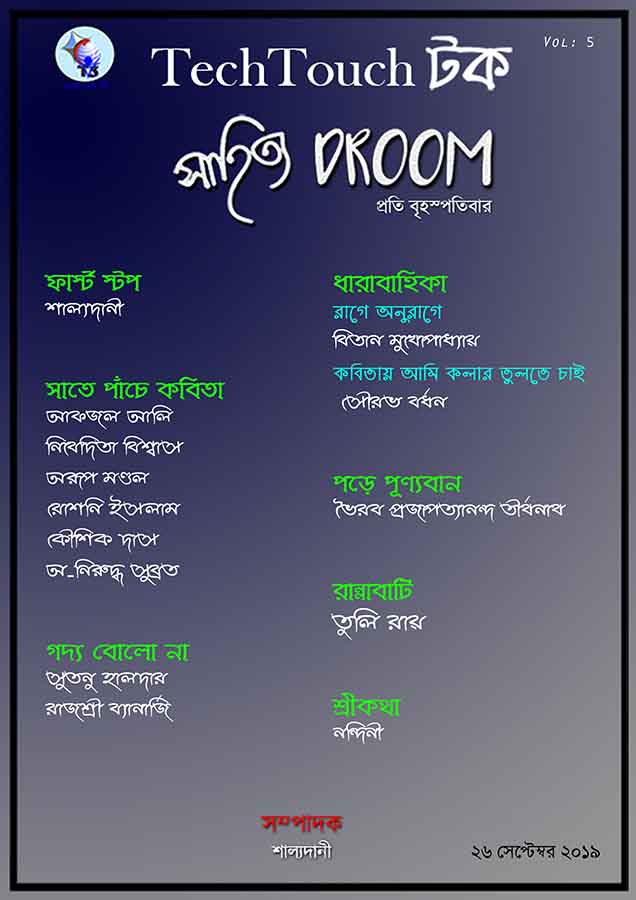–situsterpercayapesiarbet – না জানলেও ক্ষতি নেই সমরজিৎ চক্রবর্তী
না জানলেও ক্ষতি নেই
সলতে পাকানো
উত্তর ভারতে তখন বিজয় সিংহ আর বাংলায় আদিশূরের রাজত্ব। সেই সময় দেবাদিত্য দত্ত নামে এক ব্যক্তি কান্যকুব্জ থেকে আধুনিক মুর্শিদাবাদের কাছে মায়াপুরে চলে আসেন। মায়াপুর থেকে তিনি বাংলার সেই সময়কার রাজধানী সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের কাছে দত্তবাটী নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত করে বসবাস শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিনায়ক দত্ত বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জীবনযাপন করেন। এরপর এই বংশে পাঁচ পুরুষে কোন যোগ্যতম ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেনি। রাজা বল্লাল সেনের আমলে এই বংশে মাধব দত্ত নামে এক স্বনামখ্যাত পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। বিষয় সম্পত্তিও অনেক করেছিলেন, কিন্তু রাজা বল্লাল সেনের বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র মহেশ, সে’ও আত্মরক্ষা করতে না পারেনি কিন্তু তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী কোনরকমে পালিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তাঁর পুত্রের নাম উবরু। কিছু করতে না পারলেও পুত্র কন্যা মিলিয়ে ন’টি সন্তান রেখে যান। এই সন্তানদের মধ্যে এক জনের নাম কবি দত্ত। ভাগ্যদেবীর বদ্যানতায় দেবাদিত্যের বংশমর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সময়ে বাংলার সিংহাসনে লক্ষ্মণ সেন। কবি দত্ত পৈতৃক বাসভূমিতে ফিরে এসে বিষয় বৈভব অর্জন করে প্রতিষ্ঠিত হন। হিন্দু রাজত্বে রাজ-সরকারের থেকে প্রথম সেই সময়কার মহাসম্মানসূচক “খাঁ” উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি কোন মুসলমানি উপাধি নয়। মুসলমান প্রভাব তখনো এদেশে শুরু হয়নি। ‘দত্তবাটীর খাঁ’ এই নামেই বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেন কবি দত্ত। তাঁর ছয় পুত্রের মধ্যে ঈশ্বর দত্তই সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন এবং পিতামহ ও কুলপতি কবি দত্তের মতন তিনিও আটটি পুত্র ও নয়টি কন্যা রেখে পরলোকে গমন করেন। পুত্রদের মধ্যে কিশু (কেশব) ও বিষু (বিষ্ণু) যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেন।
দিনাজপুর রাজবংশ
ঈশ্বর দত্তের পুত্র বিষু (বিষ্ণু) সেই সময়কার মুসলমান নবাব সরকারের উচ্চ রাজপদ পেয়ে প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করেন দিনাজপুর জেলায়। ১৫০০ শতকের শেষভাগ, বাংলার রাজধানী তখন রাজমহল, নবাব সরকারের ‘কানুনগো’ পদ পেয়ে প্রবল প্রতাবান্বিত হয়ে উঠেন বিষ্ণু। একমাত্র পুত্র শ্রীমন্ত অকালে মারা গেলে ভীষণভাবে ভেঙে পড়েন বিষ্ণু। সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জামাতা হরিরাম ঘোষকে দান করে দেন। হরিরামের দুই পুত্র। প্রথম পুত্র শুকদেব ১৬৪৪ সালে পিতৃসম্পত্তির অধিকার লাভ করেন। পত্তন হল দিনাজপুর রাজবংশের। ১৬৬৩ সালে বাংলার শাসনকর্তা শাহেনসা সুজার কাছ থেকে এক সনন্দে রাজা উপাধি পান। ১৬৭৭ সালে দিনাজপুরে নিজ নামে বিশাল এক সরোবর খনন করান শুকদেব। যারজন্য তিনি এখনো স্মরণীয় হয়ে আছেন।
শুকদেব রাজত্ব করেন ১৬৮১ সাল পর্যন্ত। তাঁর প্রথম পুত্র রামদেব তাঁর জীবদ্দশাতে পরলোকে যাত্রা করলে মধ্যম পুত্র জয়দেব রাজ্যাধিকার লাভ করেন। কিন্তু তিনি অল্পদিনের মধ্যে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলে কনিষ্ঠ পুত্র প্রাণনাথ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। প্রাণনাথের কোন পুত্র না থাকায় রামনাথ নামে একজনকে দত্তক নেন। রামনাথ জমিদারি অনেকটাই বিস্তৃত করেছিলেন। সরকারকে বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন। বহু সৎকাজের জন্য তিনি মহারাজা উপাধি লাভ করেছিলেন। এরপরেই আসেন মহারাজা তারকনাথ। তাঁর পুণ্যপ্রাণা পতিব্রতা সহধর্মিণী মহারাণী শ্যামমোহিনী নিরাপত্তার জন্য যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তিনিই দেশে বিদেশে দিনাজপুর রাজবংশের নাম উজ্জ্বল তারার মতন আলোকিত করেন।
পাটুলি রাজবংশ
ঈশ্বর দত্তের প্রথম পুত্রের নাম কেশব, এ কথা আমরা আগেই জেনে গেছি। কেশবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বারকানাথ পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করে দেখলেন, মুকসুদাবাদের (মুর্শিদাবাদ) নবাবের অত্যাচারে হিন্দুরা জর্জরিত, ভীত, স্ত্রস্ত। নবারের এই অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আশায় দ্বারকানাথ চলে এলেন গঙ্গার পশ্চিম পারে, বর্ধমান (অধুনা পূর্ব বর্ধমান) জেলার কাটোয়া মহকুমার পাটুলি গ্রামে। সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে সুখে শান্তিতে বসবাস শুরু করেন। দ্বারকানাথের সেই সুরম্য অট্টালিকা এখন গঙ্গা-গর্ভে। তাঁর পৌত্র সহস্রাক্ষ খুব ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। ১৫৭৩ সালে সম্রাট আকবরের এক সনন্দের প্রভাবে তিনি নদীয়া জেলার ফৈজুল্লাপুর পরগণার জমিদার হন। সেই সময়ে জমিদারেরা নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে ফৌজদারি ও দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমার বিচার করতে পারতেন। রাখতে পারতেন সৈন্যসামন্ত। বাসস্থান নির্মাণ করার জন্য অট্টালিকার চারপাশে খনন করতেন গভীর গড় খাত।
সহস্রাক্ষের পুত্র উদয় ছিলেন প্রতিভাশালী ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন এক জমিদার। রায় উপাধি পেয়েছিলেন সম্রাট আকবরের কাছ থেকে। উদয় সম্পর্কে হেজেস তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, “Early in ye morning we passed by a village called Sreenagar and by 5 o’clock this afternoon (October, 1682) we got as far as Rewee, a small village belonging to Woodoy Roy, a Jamindar that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hughly. It is reported by ye country people that he pays more than twenty lacks Rupees per annum to ye King , rent for what he possesses and that about two years since he presented above a lack of rupees to ye Mogoul and his favourite, to divert his intention of hunting and hawking in his country for fear of his tenants being ruined and plundered by the Emperors lawless andunruly followers. This is a fine pleasant situation, full of great shady trees, most of them tamarinds, well stored with peacocks and spotted deer like our fellow deer. We saw two of them near the river side on our first landing.”
উদয়ের চার পুত্র। এঁদের মধ্যে জয়ানন্দ অন্যান্য সকলের নিরাপত্তার জন্য সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য না পেলেও সম্রাট শাহাজানের বিশেষ আস্থাভাজন হতে সমর্থ হয়েছিলেন। শাজাহান সিংহাসন লাভ করেই তাঁকে ‘মজুমদার’ উপাধি দেন। সেকালে মজুমদার যেমন তেমন উপাধি ছিল না। ছিল একটি সরকারের জমানবিশ। বাংলায় সেই সময় মাত্র তিনজন মজুমদার ছিলেন। সরকার সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের মজুমদার ছিলেন ভবানন্দ। সেই কারণে তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে খ্যাত। দ্বিতীয় সাবর্ণ চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত এবং জয়ানন্দ। আর এর সমর্থন পাওয়া যায় ১৯০১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে। “For their valuable services jagirs and titles were conferred by the Emperor on the three men concered Bhabananda, Laksmikanta and Jayananda, all of whome were taken, into the services of the State as Majumdars.”
জয়ানন্দ মজুমদার “কোর এক্তিয়ারপুর পরগণা” জায়গির স্বরূপ পেয়েছিলেন। বাংলার তৎকালীন নবাব কাশিম খাঁ জুয়ানী শাহাজানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জয়ানন্দকে ‘কানুনগো’ নিযুক্ত করেন। কানুনগো-র নিদিষ্ট কোন বেতন ছিল না, রুসম বা কমিশনই ছিল তাঁদের বেতন। জমির নিরিখ ধার্য করাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করেন জয়ানন্দ।
রাজা রাঘব চৌধুরী
জয়ানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘব রাজ্যাধিকারী হয়ে সম্রাট শাজাহানের কাছ থেকে ১৬৪৯ সালে ‘চৌধুরী’ এবং ১৬৫০ সালে ‘মজুমদার’ উপাধি লাভ করেন। রাঘব ছিলেন প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী। দিল্লীর সম্রাট তাঁকে প্রচুর নিস্কর জমি ছাড়াও দিয়েছিলেন আরো একুশটি পরগণার স্বত্ব। পরগণাগুলি হল, আর্যা, হালদহ, মামদানীপুর, পাজনৌর, বোরো, সাহাপুর, জাহানাবাদ, সায়েস্তা নগর, সাহানগর, রায়পুর, কোতোয়ালি, পাউনন, খোসালপুর, মইয়াট,বক্সাবন্দর (হুগলী), হাবেলি শহর, পাইকান, মজফরপুর, হাতীকান্দা, সেলিমপুর, আমিদাবাদ ও জঙ্গিপুর। শুধুমাত্র আর্যা পরগণা থেকেই বছরে তাঁর দু’লক্ষ টাকার বেশী আয় হতো। সরকারি রাজস্ব দিয়ে হাতে যা থাকত তাই সুপ্রচুর। আর এই সকল পরগণার অধিকাংশই সরকার সপ্তগ্রামেরের অন্তর্গত বলে সুব্যবস্থার জন্য হুগলীর কাছাকাছি বাস করার মনস্থ করেন। সপ্তগ্রামের উত্তর-পূর্বে ভাগীরথীর তীরে বাঁশবন পরিস্কার করে বংশবাটী তথা বাঁশবেড়িয়ার ভিত্তিস্থাপন করে বসবাস শুরু করলেন। বছরের বেশীভাগ সময় এখানে থেকে জমিদারির কাজ দেখাশোনা করতেন কেবল পুজোর সময় যেতেন পৈতৃক বাসভূমি পাটুলিতে। পাটুলি সম্পর্কে মগধরাজ বৈজলের সভাপন্ডিত কবিরাম তাঁর “দিগ্বিজয়-প্রকাশ” গ্রন্থে লিখেছেনঃ
“গঙ্গাযমুর্নেয়ারমধ্যে পাটলিগ্রামবাসিনাম্।
কায়াস্থানাং শাসনঞ্চ বর্ততে অধুনা নৃপ।।
রামেশ্বর রাজা মহাশয়
রাঘব রায়চৌধুরীর দুই পুত্র। রামেশ্বর ও বাসুদেব। পিতার মৃত্যুর পর দু’ভাইয়ের মধ্যে বিপুল সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ার ফলে জ্যেষ্ঠত্বের সম্মান স্বরূপ তৎকালীন নিয়মানুসারে রামেশ্বর সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) এবং বাসুদেব এক তৃতীয়াংশ পান। রামেশ্বর পাটুলি বাসভূমি ত্যাগকরে পাকাপাকিভাবে চলে এলেন বাঁশবেড়িয়ায়। বস্তুত তাঁর আমল থেকেই বংশবাটী রাজবংশের নাম সমুজ্জ্বলভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর বাসুদেব থেকে শুরু হয় শেওড়াফুলি রাজবংশ। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও কায়স্থ পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আসেন রামেশ্বর। পল্লী ভাগ করে তাদের উপযুক্ত ভাবে থাকার ব্যবস্থাও করে দেন। সঙ্গে এসেছিল কয়েকটি মুসলিম পরিবারও। তারা রাজবাড়ির দারোয়ানী ও জমাদারের কাজের জন্য বহাল হয়।
বারাণসী থেকে আগত ন্যায় সংখ্যাদি দর্শন ও সাহিত্যলঙ্কারে পারদর্শী বহু ব্রাহ্মণ নিজ নিজ অধীত বিদ্যার অধ্যাপনার জন্য রামেশ্বরের সাহায্যে ৬০টি চতুস্পাঠী স্থাপন করেন। এঁদের মধ্যে রামশরণ তর্কবাগীশ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর বংশধরেরা বহুদিন পর্যন্ত এই কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে বিশৃঙ্খলার কারণে সুযোগ পেলেই জমিদারেরা রাজস্ব পাঠাত না। রামেশ্বর এই সব অবাধ্য জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জমিদারি হস্তগত করে সম্রাটকে রীতিমত রাজস্ব পাঠিয়ে দিতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব হিন্দু বিদ্বেষী হলেও গুণের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করতেন না। ১৬৭৩ সালে তিনি রামেশ্বরকে পাঞ্জাপার্চা খেলাত সহ ‘রাজা মহাশয়’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সম্মান ব্যক্তিগত ছিল না। ছিল পুরুষাক্রমিক। সেকারণে রামেশ্বরের বংশধরেরা এই উপাধি ব্যবহার করতেন। সেই উপাধি সনন্দ-এর ইংরাজী অনুবাদঃ
SANAD
TO RAJA RAMSWAR RAI MAHASAY
Paragana Araha of Satgaon
( Govermment of Satgon)
As you have promoted the great interest of Government in getting possession pf Perganas and making assessment thereof and as you have performed with care whatever services were entrusted to you, you are entitled to reward. The Khelat of Panja Percha (five cloths i.e. dresses of honour) and the title of “Raja Mahasay” are therefore given to you in recognition thereof, to be inherited by the eldest Children of your family, Generation after Generation, without being objected to by any one. To Safar 1090 Hijar.
মিঃ এ.জি. বাওয়ার তাঁর “হিস্ট্রি অব্ বাঁশবেড়িয়া রাজ” গ্রন্থে লিখেছেনঃ “We know of no family in India enjoying the title of “Rajah Mahasaya” except Bansberia Raj.”
উপাধির এই সনন্দ-এ দিল্লীর সম্রাট সা গাজি আলমগীরের শীলমোহর ও পাঞ্জা স্বাক্ষর আছে। আসল সনন্দ-টি পারস্য ভাষায় লেখা। বাংলার প্রাচীন রাজবংশের গৌরব স্মারক হিসেবে আসল সনন্দ-টি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে “ডকুমেন্ট গ্যালারী”-তে ১৯১৯ সালে ১ সেপ্টেম্বর প্রথম সংরক্ষণ করা হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের হেনরি বেভারেজ একজন পারস্যভাষাবিদ। উপরি লিখিত অনুবাদ ১৯০২ সালে ৫ ফেব্রুয়ারি এশিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও লেঃ গভর্ণর স্যার জন উডবার্ন (এম.এ) কে.সি.আই মহোদয়ের অনুমতি অনুসারে প্রকাশ করেন। ১০৯০ হিজরিতে আর একটি সনন্দ-এর মাধ্যমে রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয়কে বসবাসের জন্য ৪০১ বিঘা নিস্কর জমি এবং নিম্নের বারোটি পরগণার জমিদারির স্বত্ব দেওয়া হয়ঃ
১) কলিকাতা ২) ধাড়ষা ৩) আমিরপুর ৪) বালন্দা (মেদিনীপুর) ৫) খালোড় (হাওড়া জেলার বাগনানের কাছে) ৬) মানকুর (হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণ নদের তীরে) ৭) সুলতানপুর ৮) হাতিয়াগড় ৯) মেদমোল্লা ১০) কুজপুর ১১) কাউনিয়া ১২) মাগুরা।
বর্গী হাঙ্গামা শুরু হয় এদেশে। রাজা রামেশ্বর বর্গী হাঙ্গামা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য এক মাইল পরিধির গড়খাত খনন করেন রাজবাড়ির চারিদিকে। এই কারণে রাজবাড়ির নাম হয় ‘গড়বাড়ি’ একটা সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দুর্গও নির্মাণ করেন গড়বাড়ির মধ্যে। সৈন্যরা রণসাজে সজ্জিত হয়ে অবস্থান করত দুর্গে। বর্গীরা ত্রিবেণীর কাছে এসে হাজির হলেই রাজবাড়ির লোকেরা গড়বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন।
শেওড়াফুলি রাজবংশ
রামেশ্বর রায় পাটুলি থেকে বাঁশবেড়িয়ায় চলে এলেও বাসুদেব রায় পাটুলিতেই থেকে জমিদারি পরিচালনা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে সেই সময়কার নিয়মানুযায়ী সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা হয় আনা বা আনি হিসেবে। ‘দশ আনি’, ‘নয় আনি’, ‘সাত আনি’ ও ‘ছয় আনি’। ‘দশ আনি’ পুত্র মনোহর রায় ও তাঁর পরিবার পাটুলিতেই থাকতেন। ধার্মিক মনোহর রায় ছিলেন বদান্যতায় ও পরদুঃখকাতরতায় উদার মানুষ। কলকাতা থেকে শুরু করে সমগ্র গ্রাম বাংলা, বারাণসী, দিল্লী ও হরিদ্বার মিলিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৫২টি দেবদেবীর মূর্তি স্থাপন করে অমর হয়ে আছেন। এক ব্রাহ্মণকে ঋণদায় থেকে মুক্ত করার জন্য বাংলার নবাব তাঁকে বংশ পরম্পরায় ব্যবহার করার জন্য ‘সুদ্রামণি’ উপাধি দান করেন। সুদীর্ঘকাল এই পরিবার সেই উপাধি মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছিলেন।
শেওড়াফুলি-কে তখন জনপদকে বলা হতো সাড়া পুলী। জমিদারীর কাজ পরিচালনা করার জন্য একটি কাছারী প্রতিষ্ঠা করেন শেওড়াফুলিতে। ১১৪১ সনে ১৫ জ্যৈষ্ঠ (১৭৩৪ সালে মে মাসের শেষে) তিনি এই কাছারী বাড়িতে শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলার দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার পুজোর জন্য বর্তমান শ্রীরামপুরে বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করে দেন। আজকের যে শ্রীরামপুর আদালত, পোস্টাফিস তা সবই ওই দেবোত্তর সম্পত্তির অংশে অবস্থান করছে। মাহেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা পরিচালনার জন্য মনোহর রায় জগন্নাথপুর নামে একটি গ্রামকে দেবোত্তর করে দেন। আর এই কারণে স্নানযাত্রার সময় শেওড়াফুলি রাজাদের অনুমতি ছাড়া আজও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান আরাম্ভ হয় না।
পিতা বাসুদেব রায়ের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখতে মনোহর বাসুদেবপুর নামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে একটি মন্দিরে নির্মাণ করে স্থাপন করেন পিতার প্রস্তরমূর্তি। নিত্য সেবা ও পুজোর জন্য দান করেন একশো কুড়ি বিঘা জমি। এ ছাড়াও পিতামহ রাঘবেন্দ্র রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে রাঘবেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেন বৈদ্যবাটীতে। গুপ্তিপাড়ায় নির্মাণ করেন শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। তাঁর মৃত্যুর পর ‘মনোহরাষ্টক’ রচনা করেন শুকদেব সিংহ। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, প্রত্যেক দিনই মনোহর ভূমি দান করতেন। আর এই রকম ভূমি দানের ফলে শেষ জীবনে তিনি দেখতে পেলেন রাজ্যের সব গ্রামের অর্ধেক জমিই তাঁর নিস্কর দান। ১১৫০ সনে তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন রাজচন্দ্র রায়।
১৭৫৫ সালে দিনেমাররা বাংলায় প্রথম বাণিজ্য করতে আসে। ফরাসীদের সাহায্যে ১৭৫৫-৫৬ সালে নবাবের অনুমতিতে রাজা মনোহর রায়ের কাছ থেকে আকনা ও পেয়ারপুর গ্রাম পেয়ে শ্রীরামপুরে বসবাস শুরু করেন। ১৭৫৯ সালে তাঁর পুত্র রাজচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে বার্ষিক ১৬০১ টাকা খাজনায় ৬০ (ষাট) বিঘে জমি নিয়ে দিনেমাররা কুঠি (ফেড্রিকনগর) নির্মাণ করে ব্যবসা শুরু করে।
রাজচন্দ্র রায় পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অনেক দেব-দেবীর মন্দির স্থাপন করেন। দিনেমার অধ্যুষিত ফেড্রিকনগরে ‘শ্রীরামসীতা’ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শ্রীপুর, মোহনপুর ও গোপীনাথপুর (তিন শত বিঘে) জমি দেবোত্তর করে দেন। শ্রীরামসীতার জন্যই গঙ্গার তীরস্থ তিনটে গ্রাম পরিচিত হয়ে ওঠে শ্রীরামপুর নামে। কলকাতায় চিৎপুর রোডে শ্রীশ্রীচিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং মায়ের সেবার জন্য দান করেন বহু জমি। বাংলার দেওয়ানী ভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নেওয়ার পর সম্রাট দ্বিতীয় শাজাহানের শীলমোহর দেওয়া এবং হেস্টিংসের স্বাক্ষর দেওয়া একটি সনন্দ পান ১৭৭৮ সালে ১০ ডিসেম্বরে। এই সনন্দে প্রভাবে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতন রাজস্ব আদায় করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। রাজচন্দ্রের পর রাজা হন পুত্র আনন্দচন্দ্র। তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনিও পিতার মতন মাঝেমাঝে শেওড়াফুলি কাছারী বাড়ি এসে থাকতেন। কাছারী বাড়ি রাজবাড়িতে পরিনত হয় আনন্দচন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্রের আমলে।
শ্রীশ্রীনিস্তারিণী কালী
রাজা হরিশচন্দ্র শেওড়াফুলিতে শ্রীশ্রীনিস্তারিণীদেবীর মন্দির নির্মাণ করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ১২৩৪ সনে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। ধার্মিক, সত্যপরায়ণ হরিশচন্দ্রের দেবী কালিকার এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে লুকিয়ে আছে বেদনাবিদুর এক মর্মস্পর্শী ঘটনা। ভাগ্যদোষে তিনি স্ত্রী-হত্যা জনিত পাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। হরিশচন্দ্র তিনটি বিবাহ করেছিলেন। তিন পত্নীই ছিলেন কলহপ্রিয়া। এক দিকে যেমন নির্দয় তেমন পরশ্রীকাতর ও মুখরা। একদিন এই কলহ এতদূর গড়ায় যে হরিশচন্দ্র নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেননা। ক্রোধাসক্ত হয়ে কোষমুক্ত তরবারী নিয়ে ভয় দেখাতে যান। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাণীরা আঘাত পান এবং বড় রাণী সর্বমঙ্গলা দেবী সেই আঘাতে মারা যান। স্থিরবুদ্ধি রাজা স্ত্রীহত্যাজনিত পাপে অনুশোচনায় কাতর হয়ে প্রাণত্যাগ করার বাসনা নিয়ে একাকী অশ্বারোহণে বেরিয়ে পড়লেন। রাতের অন্ধকারে দুর্ভেদ্য এক গভীর অরণ্যে বিশাল এক বৃক্ষের তলে বিমর্ষ মনে আশ্রয় নিলেন। অস্নাত অভুক্ত পরিশ্রান্ত রাজা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন যে, স্ত্রীহত্যাজনিত মহাপাপ করলেও এ পাপ তাঁর ইচ্ছাকৃত নয় উপরন্তু তিনি গভীর অনুতপ্ত। তাই তিনি যদি গঙ্গার তীরে দক্ষিণাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজোয় রত থেকে সেখানে বাস করেন, অবশ্যই পাপমুক্ত হবেন। তিনি আরো শুনলেন যে, যে পাথরটির উপর তিনি শয়ন করে আছেন সেই পাথরটি থেকেই দেবী-বিগ্রহ নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর রাজা হরিশচন্দ্র দেখলেন, তিনি সত্যিই একটি কালো পাথরের উপর শয়ন করে আছেন। রাজা শেওড়াফুলি কাছারী বাড়ি ফিরে কর্মচারীদের সেই দুর্গম জঙ্গলের হদিশ দিয়ে পাথরটি আনতে বললেন। কথিত আছে, কয়েকদিনের মধ্যেই এক ভাস্কর উপযাচক হয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তাকে মাকালী স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছেন।
পাথরখন্ড থেকে দেবী-বিগ্রহ নির্মাণের পর গঙ্গার দিকে মুখকরে নির্মিত হয় মন্দির। পঞ্চমুন্ডিবেদীর উপর তামার তৈরী বিশাল আকারের পদ্মাসনে দেবী সংস্থাপিতা হলেন। দেওয়ালে মিনার সুদৃশ্য কারুকার্যে শোভিত। রাজা হরিশচন্দ্র দেবীর চরণ বন্দনা করে নাম রাখলেন শ্রীশ্রীনিস্তারিণী। মন্দির নির্মাণ, মূর্তি গঠন ও স্থাপন করতে সেই সময় দশ হাজার টাকার বেশী। মন্দিরের স্থাপত্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কিছু নেই। সাধারণ একচূড়া মাঝারি আকৃতির মন্দির।
শ্রীশ্রীনিস্তারিণী মন্দিরের বামদিকে দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির। শ্বেতপাথরের শিববিগ্রহটি খুব সুন্দর। সামনে নাট মন্দির ও বলিদানের স্থান। চারপাশে বিস্তৃত ফাঁকা জায়গা। নিস্তারিণী মন্দিরের ডানদিকের দেওয়ালে সংস্কৃত ভাষায় দেবীর নাম, প্রতিষ্ঠাতার নাম ও স্থাপনকাল একটি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ আছে –
“স্বীয়ে রাজ্যে ভূজঙ্গশ্রুতিশিখরি ধরা গণ্যমানে শকাব্দে।
কালীপদোভিলাষী স্মরহরমহিষী মন্দিরং তৎপ্রতিষ্ঠাং।।
চক্রে গঙ্গা সমীপে বিগতভল ভয়ঃ শ্রীহরিশচন্দ্র দত্তঃ।
সম্মতির্যস্য রামেশ্বর ইতি নৃপস্মেন্ত্রী-যত্নেন সার্ধং।।”
যদিও সময়ের সঙ্গে প্রস্তর ফলক থেকে বর্তমানে উদ্ধার করা খুব কষ্টকর। প্রস্তর ফলকে এবড়ো-খেবড়ো লেখা খুবই অস্পষ্ট এবং পাঠোদ্ধারে অযোগ্য। মন্দিরের মধ্যে আরও চারটি বিগ্রহ দেখা যায়, ১) কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বৃষবাহন ও দ্বিভুজা সুদৃশ্য ভৈরবমূর্তি, ২) বর-চক্র-গদা-অভয়ধারী তাম্রনির্মিত মহাবিষ্ণুমূর্তি, ৩) পিতল নির্মিত চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মীমূর্তি, ৪) পিতল নির্মিত দ্বিভুজা ও উপবিষ্টা অন্নপূর্ণামূর্তি, দেখতে অনেকটা মঙ্গলচন্ডীর মতন। বিগ্রহ পাটুলির বিভিন্ন মন্দির থেকে এনে রেখেছেন নির্মলচন্দ্র ঘোষ।
বাংলায় প্রসিদ্ধ কালীক্ষেত্রগুলির মধ্যে নিস্তারিণী কালীর ‘থান’ অন্যতম উল্লেখযোগ্য। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার পর পাটুলি থেকে রাজপরিবারের সকলে শেওড়াফুলি কাছারী বড়ি চলে আসেন। কাছারী বাড়ি হয়ে উঠে রাজবাড়ি।
নিস্তারিণী কালী নিয়ে অনেক কাহিনী কথিত আছে। রাণী রাসমণি গঙ্গার তীরে মা-ভবতারিণী মন্দির নির্মাণের জন্য স্থান অন্বেষণে নৌকা করে গঙ্গাবক্ষে বেরিয়েছেন। সেই সময় শেওড়াফুলির কাছে গঙ্গাঘাটে মা-নিস্তারিণী কিশোরী কন্যার বেশে তাঁকে পথ দেখিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসেন। এই বংশেরই নির্মলচন্দ্র ঘোষের জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। একবার এক অমাবস্যার রাতে পুরোহিত উন্মাদ হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতন আচরণ করে বলে উঠে, ‘দে আমার কথার উত্তর দে, না হলে আজ তোর নিস্তার নেই। তোকে ছাড়ব না। দে জবাব দে…।’ তারপরেই প্রথমে মায়ের হাত ধরে টানাটানি শুরু করে পরক্ষণে বলি দেওয়ার খরগ নিয়ে মায়ের দুই হাতে মারল কোপ। সঙ্গেসঙ্গে হাত দুটি ছিন্ন হয়ে খসে পড়ল।
উন্মাদ পুরোহিতকে মায়া মমতায় মুক্ত করে নির্মলচন্দ্র পুজো করার নির্দেশ দিলেন। রাত্তিরে ঘটল এক গা ছমছমে ঘটনা। তাঁর স্ত্রী হঠাৎ মূর্ছিতা হয়ে পুরুষ কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন যে, আমরা ছয় জন দলপতি ও তেত্রিশ জন অনুচর মৃত্যুর পর দূর দূর দেশ থেকে এসে রাজবাড়ির বাগানে বেলগাছে বাস করছি। মা নিস্তারিনীর সেবক আমরা। আমি দলপতি শম্ভুনাথ। মায়ের কাটা হাতে যন্ত্রণা হচ্ছে। তোমরা তার কোন ব্যবস্থা করলে না? কাল সকালেই মায়ের ক্ষতস্থানে রক্তচন্দনের প্রলেপ দেওয়ার আয়োজন করো।
পরের দিন সকালেই নির্মলচন্দ্র মায়ের ক্ষতস্থানে রক্তচন্দনের প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেন তীব্র যন্ত্রণায় মায়ের মুখমন্ডল কেমন যেন ব্যথাতুর। খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসে বললেন, এমন প্রতিমা রাখতে নেই। নির্মলচন্দ্র পড়লেন মহাবিপদে। বিপদতারণ করলেন তান্ত্রিক সাধক শ্যামলাল। বললেন, আপনার মায়ের যদি এমন অবস্থা হয়, তাঁকে বিসর্জন নতুন মা আনবেন? এও ঠিক সেই রকম ব্যাপার।
যে ভাস্কর প্রতিমা নির্মাণ করেছিলেন তারই এক বংশধর না ডাকতেই এসে গেল। মায়ের হাত এমনভাবে জুড়ে দিল যে বোঝাই গেল না জোড়া হয়েছে। ধন্য মহিমা মা নিস্তারিণীর।
শেওড়াফুলি হাট
সমগ্র পূর্বভারতে যে ক’টি হাট বর্তমান আছে তার মধ্যে বৈদ্যবাটীর পুরসভার ‘শেওড়াফুলি হাট’ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশালত্বে ও বাণিজ্যিক লেনদেনের হিসাবে আজও বিখ্যাত। বৈদ্যবাটীর হাট এক সময়ে খুব বিখ্যাত ছিল। পর্তুগীজরা এই স্থানকে দীর্ঘাঙ্গ বা দিগঙ্গ বলত। এই হাট থেকে বহু অর্থ উপার্জন হয় দেখে ১২২৭ সনে মুন্সি গোলাম হোসেন নামে জনৈক ব্যক্তি বৈদ্যবাটীর উত্তরে নতুন একটি হাট স্থাপন করেন। রাজচন্দ্র রায়ের পুত্র হরিশচন্দ্র পুরনো হাটটি বজায় রাখার জন্য বহু চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। শেষে সম্পূর্ণ হাট-টিকেই তুলে নিয়ে চলে আসেন শেওড়াফুলিতে। ১৮২৭ সালে শেওড়াফুলিতে স্থাপন করেন নতুন হাট। সপ্তাহে দু দিন। শনি ও মঙ্গলবার। জনপ্লাবনে পূর্ণ হয়ে যেত। দূর দূরান্ত থেকে আগে নৌকা ও গরুর গাড়ি করে মালপত্তর আসত। ১৮৮৫ সালে শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত রেল চালু হওয়ার পর এই হাটের চেহারা একেবারে বদলে যায়। হান্টার সাহেব তাঁর “ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ্ ইন্ডিয়া” গ্রন্থে বলেছেন, “A market said to be the largest in Bengal, is held here twice week, at which large transaction take place in various kinds of produce, and specially in jute which is brought from all parts of the adjacent country.”
দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ‘সুরধনী’ কাব্যে এই হাট সম্পর্কে লিখেছেনঃ
বাজারে বেগুন আলু পালমের ঝাড় সুপক্ক কদলী কত সংখ্যা নাহি তার
গাদায় গাদায় করা হারায়ে পাহাড় ; মাসাবধি খাদ্য চলে রামের সেনার।
কথিত আছে, শেওড়াফুলি হাটের কুমড়ো ছিল প্রসিদ্ধ। এক একটির ওজন ছিল আধ মন। ইংলন্ডে ভোজ সভায় আদরের সঙ্গে স্থান করে নিয়েছিল। ‘বৈদ্যবাটীর কুমড়ো’-র নাম শুনলেই খুশী হয়ে উঠতেন।
১২৩৯ সনে ফাল্গুন মাসে (১৭৬৮ সালে মার্চ মাসে) হরিশচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে মেজো রাণী হরসুন্দরী দেবী ‘সাত আনি’ বংশের সন্তান যোগেশচন্দ্রকে এবং ছোটরাণী রাজধন দেবী তাঁর পরিচিত এক বংশ থেকে পূর্ণচন্দ্রকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এই সময়ে বাংলা তথা কলকাতার ‘প্রথম বাবু’ সাতুবাবু ওরফে আশুতোষ দেব শেওড়াফুলিতে দেবগঞ্জ নামে একটি হাট স্থাপন করেন। আজও ওই জায়গা ছাতুগঞ্জের বাজার বলে বর্তমান। সেই সময় বাংলায় জনসাধারণের মধ্যে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ধনী লোকেরা কিভাবে সাধারণ মানুষকে উৎপীড়ন করতেন তা ইতিহাস বুকে করে বহন করে চলেছে। আর এর সমর্থন পাওয়া যায় ১২৪৫ সনে ৭ই জ্যৈষ্ঠের ‘সমাচার দর্পণ’-এঃ
“জিলা হুগলীর সেওড়াফুলির জমিদার ঁপ্রাপ্ত হরিশচন্দ্র রাজা বৈদ্যবাটীর পুরাতন হাটের স্থান সঙ্কীর্ণ প্রযুক্ত অথবা ঐ হাটে দুই তিন জমিদারের সম্পর্ক থাকাতে বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্তই হউক অনেক ব্যয় ব্যসনপূর্বক দরবার করত আপনার জমিদারি সেওড়াফুলিতে ঐ পুরান হাট ভাঙ্গিয়া বসান। বিশেষত রাজা অনেক টাকা ব্যয় পূর্বক বহু সংখ্যক ঘর প্রস্তুত করিয়া ঐ সোনার হাট বসাইয়া মাত্র, স্বর্গীয় হাট করিতে গেলেন। এইক্ষণে মোদের বিষয় যে, এই হাটের উত্তরাধিকারিণী দুই রাজ মহিষী দুই পোষ্য পুত্র করিয়াছেন ঐ বালকেরা এইক্ষণে নাবালক এবং রাণীরাও অবলা জমিদারীও হস্তান্তর। ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসী অতি ধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় ঐ হাটের নিকটস্থ দেবগঞ্জ নামক এক গঞ্জ বসাইয়াছিলেন, কিন্তু অনেক টাকা ব্যয়ভূষণ করিয়াও তাহাতেও প্রায় তাদৃশ্য কৃতকার্য না হওয়াতে এইক্ষণে ঐ নাবালক ও ঐ অবলাদের হাটের উপর বলপ্রকাশ করত ঐ হাট ভাঙ্গিয়া আপনাদের ভগ্ন দেবগঞ্জ পূরণ করিতেছেন এবং শুনা গিয়াছে কলিকাতাস্থ ব্যাপারী লোকদিগকে অনেক টাকা দিয়া ঐ দেবগঞ্জের নীচে ভূরি নৌকা শনি মঙ্গলবারে বন্ধন করিয়া রাখেন যদ্যাপি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক রাজার হাটে না যায়, সুতরাং রাইয়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেববাবুর হাটে আসিতে হইবেক। ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরষ নাই উক্ত রাজা বর্তমান থাকিলে প্রশংসা হইত।”
শেওড়াফুলি হাট রাজা হরিশচন্দ্র রায় অনেকটা রেষারেষির জন্য এই হাট স্থাপন করেছিলেন।
বাকি কথা
বর্তমানে শেওড়াফুলি রাজবংশের অবস্থা তথৈবচ। তাল পুকুরে ঘটি ডোবে না। হাটের অর্ধেক অংশ অনেকদিন আগেই দিঘাপতিয়া (অধুনা বাংলাদেশ) রাজপরিবারে চলে যায়। চার আনা উত্তরপাড়ার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে এবং বাকি চার আনা মাত্র শেওড়াফুলি রাজ পরিবারের দুই শরিকের মধ্যে বিদ্যমান। দুই রাণী দত্তক পুত্র গ্রহণ করার পরই দুই শরিকের জন্ম হয়। যোগেশচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। পূর্নচন্দ্র সম্পর্কে সেরকম কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যোগেশচন্দ্রের আমলে পাটুলির রাজবাড়ি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। যোগেশচন্দ্রও ছিলেন দেবী নিস্তারিণীর পরম ভক্ত ও সুগায়ক। জগতমাতার নাম কীর্তনেই তিনি জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করে যান। ১২৬২ সনে তিনি চিরশান্তির দেশে যাত্রা করলে পুত্র গিরীন্দ্রচন্দ্র জমিদারি লাভ করেন। পূর্বপুরুষের মতন গিরীন্দ্রচন্দ্রও দেবী নিস্তারিণী নিবেদিত প্রাণ। তাঁর সময়ে মায়ের পুজো হতো প্রগাঢ় আড়ম্বরে। তিনিই প্রথম বৈদ্যবাটী পৌরসভার চেয়ারম্যান হন। এই পৌরসভা স্থাপিত হয় ১৮৬৯ সালে। গিরীন্দ্রচন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা মনোরমার বিবাহ দিয়েছিলেন বিহার ভাগলপুরের চম্পা নগরের জমিদার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। গিরীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর মনোরমার একমাত্র পুত্র নির্মলচন্দ্র শেওড়াফুলি রাজবংশের উত্তরাধিকারী হন। শেওড়াফুলি ও বৈদ্যবাটী একই পৌরসভার অন্তর্গত। কেবল মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ডানকুনি খাল দু’স্থানকে পৃথক করে দিয়েছে। আইনজীবি নির্মলচন্দ্র ঘোষও বহু জনহিতকর সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার পাশাপাশি বৈদ্যবাটী পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন বহুদিন। ছিলেন কায়স্থ সভার সভাপতি। নিজ ব্যয়ে শেওড়াফুলিতে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিলেন। ১৩৩৫ সনে ১৯ শ্রাবণ তিনি মারা যান। পুত্র সুনীলচন্দ্র ঘোষের হাতে দিয়ে যান যাবতীয় দায়িত্ব।